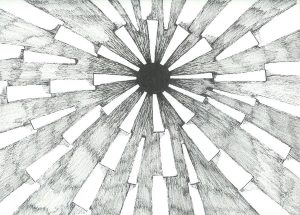 কামাল রাহমান
কামাল রাহমান
১
দিনবদলের দুর্লভ এক মুহূর্তে গাইডবুকের চকচকে মলাটের উপর দারুণ সুন্দর এক যুদ্ধবাজ কালো ঘোড়ার মতো মাথা উঁচিয়ে থাকা মানচিত্রের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বুকের ভেতর রঙিন স্বপ্নের একটা বীজ বোনা হয়ে যায়। পৃথিবীর এই আশ্চর্য দ্বীপদেশের কঠিন মাটির অনেক গভীরে পাতালছোঁয়া শেকড় ছড়িয়ে দেবে ঐ বীজ থেকে জন্মানো, এখনো অস্পষ্ট ও অনেকটা অজানা এক স্বপ্ন, কল্পনা ও রহস্যের মিশেলে বেড়ে ওঠা ঐ গাছ। তাহলে এই আমার দ্বিতীয় দেশ, একটা ঘোড়ার মাথা! আর ক’ঘণ্টা পর পা রাখতে যাচ্ছি ওখানে, ত্রিশ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে ঘণ্টায় সাড়ে পাঁচশ’ মাইল বেগে বিমান এগিয়ে চলেছে এখন ঐ দেশটার দিকে। অজানা এই উত্তেজনার সঙ্গে বুকের অনেক ভেতরে মিশে থাকা একটা দীর্ঘশ্বাসও আটকে থাকে ফেলে আসা গাঙ্গেয় ঐ বদ্বীপটার জন্য। ছোট্ট এ জীবনের যাপিত, প্রাণস্পর্শী ছোট্ট অংশটার জন্য, বিচিত্র প্রকৃতি ও আশ্চর্য মানুষজনের জন্য। জীবনের এই রহস্য অন্য খাতে বয়ে নিয়ে যায় যে-সব দিন, সেগুলোর একটা এখন মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে উঁচু আকাশে, এবং অবচেতনের কোনো এক ইচ্ছের অদৃশ্য সুতো ধরে বিলেতে আমার প্রথম পা রাখার এই তারিখটা পারিবারিক এক ইতিহাসও সৃষ্টি করে। দেড়শ’ বছর পর আমার নাতির ঘরের পুতি, পুতির ঘরের লাই, যার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আমার নাকি নাই, পরিবারের ইতিহাস খুঁড়ে শেকড় খোঁজার জন্য যাবে বাংলাদেশে, যখন দেশের অনেকটাই নেই!
পায়ের নিচে সমুদ্র দেখার বিস্ময়-ঘোর কেটেছে একটু আগে, নীল রঙে আঁকা একটা ছবির মতো আঁকাবাঁকা রেখায় লেপ্টে আছে সবুজের পাশে, ঢেউয়ের অবিরাম দাপাদাপি নেই ওখানে, অশান্ত উত্তাল গর্জন নেই, অনেকটা সাদামাটা ও বিশাল এক মানচিত্রের মতো নিশ্চুপ। এই তবে শুরু আমাদের সাগর পাড়ি দেয়া! আরব হুন ইংরেজ দিনেমার এরা এই নীলের সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছে এতোকাল। এবার উল্টোরথ, অন্য জীবন।
তারিখটা সতেরোশ’ সাতান্নোয়, আমাদের ভূখণ্ড হতে ইংরেজদের ভারতবর্ষে উপনিবেশীকরণের শুরু থেকে আঠারোশ’ সাতান্নোয় উপনিবেশরোধী বাহাদুর শাহ্ শেষ প্রচেষ্টা ভারতবাসী কর্তৃক নস্যাৎ করে দেয়া, উনিশশ’ সাতচল্লিশে লুটের রাজ্য নিজেদের কর্তৃত্বে রাখার জন্য ভারতবর্ষ বিভাজন, এবং ঐ বিভাজনে আমাদের স্বার্থ রক্ষায় নেতাদের ক্ষমাহীন অযোগ্যতা, অদূরদর্শীতা ও চরম ব্যর্থতা। কাকতালীয়ভাবে প্রতিটা সংখ্যার পেছনে রয়েছে সাত সংখ্যাটি, আর একাত্তরের শুরুটাই তো সাত দিয়ে, আমারও এখানে আসা উনিশশ’ সাতষট্টিতে, তারিখটাও আবার সাতই জুন, সিরাজের পতনদিন! বিমানে বসে মনে হয়েছে সিরাজের যে জুতোজোড়া ওকে ধরিয়ে দিয়েছিল, ওটার একটা রেপ্লিকা সঙ্গে নিয়ে এলে, মজা হতো। হাস্যকরভাবে অবশ্য, প্রায় ওরকম একটা কাজই করেছিল পরে আফ্রিকার স্বৈররাজা ইদি আমিন, অতিকায় জুতো পরে বিলেতে বিচরণ করে!
জানালায় চোখ থাকায় এমন একটা দৃশ্য চোখে পড়ে যা অতীতে দেখা হয় নি কখনো, এবং ভবিষ্যতেও হবে না আর। যারা অনেক বেশি বিমান ভ্রমণ করে তাদেরও দেখা হয় না এটা। আরেকটা বিমান অতিক্রম করে যায় আমাদের বিমানটাকে, এত অল্প সময়ের জন্য যে সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়েও ওটার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। সাধারণত একই উচ্চতায় দুটো বিমান অতিক্রম করে না, ফলে এমন দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না। মনের ভেতর আরো একটা বিষয় স্থায়ী হয়ে যায় ঐ মুহূর্তে। পৃথিবীর উপরিভাগের কোনো এক বিন্দুতে অতিক্রম করে যায় পরস্পর বিপরীতমুখী দুটো ভিন্ন সংস্কৃতি, এখানেও কাকতালীয়ভাবে দুটো মিশ্র সংস্কৃতি। ইংরেজরা যেমন হাজার হাজার বছর ধরে দ্বীপের বাইরের মানুষ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, শাসিত হয়েছে, এবং গড়ে ওঠেছে, গাঙ্গেয় বদ্বীপের মানুষেরাও তাই। কিছুটা দূর পূর্বপুরুষ আমার, বারো ভূঁইয়ার এক ভঁূইয়া ঈশা খাঁর রক্তবীজ, জিন বয়ে চলেছি শরীরে, ইতিহাসের ভাবনাটা তাই সবকিছুতেই জড়িয়ে যেতে চায়।
মুহূর্ত আগে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া বিমানটা ভীষণ নিঃসঙ্গ করে দেয়, যে দুটো সংস্কৃতি ক্রস করেছে ঐ মুহূর্তে, ধরে নেই, পেছনে চলে যাওয়া বিমানটি আমার ছোট্ট সংস্কৃতি, ওটার বাইরে থেকেও আজীবনের জন্য থেকে যাবো ওটার ভেতর। আর এই বিমানের ভেতরে থেকেও এটার সংস্কৃতি আমার নয়, এটার খাবার-দাবার, কথা বলা, ভাষা, ভঙ্গি, পোশাক-আশাক, কোনোটাই মেলে না পেছনে ফেলে আসা আমার সংস্কৃতির সঙ্গে। অথচ এটাই ধরে রাখতে হবে অবশিষ্ট জীবন।
ডানদিকে, আমার জানালার বাইরে শুধুই আকাশ, নরোম মেঘ ছুঁয়ে যায় বিমানের ধাতব শরীর, প্রাণীর অনুভূতি পেলে আরো নিচে নেমে আসতো বিমানটা, যেখান থেকে পৃথিবীর রূপ কিছুটা হলেও দেখা যায়। হাত রাখি কাচের উপর, পেতে চাই মেঘের শীতল অনুভব, ত্বক ও পালকের দূরত্ব যত কমই হোক, আছে একটু হলেও। ভেতরের আঁটসাঁট পরিবেশ ও বাইরের একই রকম আকাশে ক্লান্ত হয়ে পড়ে চোখ। জানালার আকৃতি এইমাত্র আকর্ষণ করে অখণ্ড মনোযোগ। চৌকো নয়, কোন চারটে গোলাকার, গোল নয়, সরল বাহু রয়েছে চারটে, ডিম্বাকারও না, জ্যামিতি কি বলে, আয়তও না এমন একটা সমতলের ক্ষেত্রফল কীভাবে বের করা যায়? সবচেয়ে খারাপ উপপাদ্য, মাথার ভেতর অকারণে এতো চঞ্চল হয়ে ওঠে অন্যের সাহায্য নেয়ার কথা মনে হয়। বিমানবালাকে ডেকে জিজ্ঞেস করা যায় জানালাগুলোর ক্ষেত্রফল সম্পর্কে ওর ধারণা আছে কিনা! বোতাম টেপার আগে বোঝা যায় নি ভুলটা, দূর থেকে ওর আকর্ষণীয় হাঁটা, শরীরের ছন্দ, মুখের লাবণ্য চোখে পড়ে। কাছে এলে অসাধারণ এক হাসি, চোখ মুখ ছাড়িয়ে ওর দাঁতের সৌন্দর্য! ওখানে চোখ রেখে নির্দ্বিধায় বলা যায়, এক গ্লাস জল পেতে পারি, প্লীজ? নিশ্চয়! দাঁতের উপরের পাটিতে লেগে থাকা লিপস্টিকের ছোট্ট একটা দাগ তখনো আকাশে এক ঝলক বিদু্যতের মতো আমার চোখ ঝলসে রেখেছে, জল নিয়ে ফিরে আসে যখন পপি ফুলের রং ঠোঁট দুটিতে মিশে আছে একই হাসি, দাঁতের প্রান্ত ঘেষে লিপস্টিকের মোহন ঐ দাগটুকু নেই শুধু! জোর দিয়ে বলা যায়, খেয়ে ফেলে নি, ওটা মুছে এসেছে। এতো নির্ভুলভাবে পুরুষের বিভিন্ন দৃষ্টি ধরতে পারে মেয়েরা, যা প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা একটা, নিঃসন্দেহে! ঐ মুহূর্তে পানের জন্য জল চাওয়ার বাইরে আর কিছু ছিল না মাথায়, এখন কত শত পানীয় প্রতিদিন! ছেলেবেলার কথা মনে করতে পারি, পানি ছাড়া অন্য তরল যা পান করা যেতো, তার তালিকা অনেক ছোট! প্রতিদিন পান করতে হতো দুধ, গ্রীষ্মে কেবল কোনো উপলক্ষে চিনিগোলা লেবু সরবত, কখনো বেলের, আরো বেশি পাওয়া যেতো আখের গুড়ে তেঁতুলগোলা ঠাণ্ডা পানি, শীতে খেজুরের রস, নানার বাড়ি ফরিদপুরের পাংশায় কখনো তালফুলের রস। তালিকা আর বাড়াতে কষ্ট হয়। অতিথি এলে, অথবা রোজার মাসে আরেকটা বিদঘুটে পানীয়, ওহ্, মনে হলে এখনো ওগলে ওঠে, গাঢ় গোলাপি রঙের রুহ আফজা, ওয়া ওয়া!
গতিময় পৃথিবীতে মানুষও চিরপরিবর্তনশীল, এক সময় যাদের শত্রু ভেবে আক্রমণ করে তাড়িয়ে দিতে চায়, অন্য সময় তাদের আশ্রয়ে যেয়ে ওঠে স্বেচ্ছায়। মাত্র দু’যুগ আগে আমার পূর্বপ্রজন্ম এই ইংরেজ জাতটাকে দেশ থেকে বের করে দেয়ার জন্য সংগ্রাম করেছে, এখন ইংরেজদের ঘরে আশ্রয় পাওয়ার জন্য দেশান্তরী হতে হয় আমাদের। মনের ভেতর একটা ভুল স্বপ্নের বীজ শোষক ও শোষিতের শেকলটা ভেঙ্গে দেয়। ভারতবর্ষ থেকে আসা মানুষের প্রায় শতভাগই দেশান্তরী হয়ে এখানে এসেছে কায়িক শ্রম বিক্রি করার জন্য, এই শ্রম বিক্রিটাই আসল। বিলেতের ভালো একটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে আমাকেও বিক্রি করতে হবে শ্রম। হাত দুটোর মতো মস্তিষ্কটাও দেহের অংশ, তুলনামূলক ভালো অংশ, ইংরেজরা এটার ব্যবহার শিখেছে অনেক আগে, ঠেকে ও ঠকে! ওরা ভারতবর্ষে গিয়েছিল শ্রম বিক্রি করতে। উপনিবেশ, রাজ্য জয়, দেশ শাসন এসব কেতাবী কথা। যে-সকল অংশ থেকে ওদের করে খাওয়ার রসদ পেয়েছে, তা গায়ের জোরে হলেও দখল করেছে, যেখানে ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা নেই সেখানে যায় নি। আফগান, নেপাল, এসব জায়গা থেকে পাওয়ার আশা কিছু ছিল না, নেয় নি। শাসনদণ্ড হাতে থাকলে করে খাওয়ার সুবিধে, তাই ওটা নিয়েছে।
অক্সফোর্ডে যাওয়ার আগে একটা হপ্তা কাটাতে হয় লন্ডনে, বিদেশী ছাত্রদের জন্য বিলেতি কেতা শেখার একটা কোর্স করতে হয় ব্রিটিশ কাউন্সিলে। শব্দের অশেষ শক্তি বুঝতে পারি আরো ভালোভাবে, খুব বড় একটা অন্যায়ের পর ‘দুঃখিত’ বলে এটাকে হালকা করে ফেলা যায়, এমনকি ক্ষমাও পেয়ে যাওয়া যায় কখনো কখনো। মনে পড়ে না, দেশে কোনো ভুল করার পর বলেছি দুঃখিত, অথচ এরা একটা মানুষ মেরে ফেলার সময়ও বলে দুঃখিত, আমি কেবল কর্তব্য পালন করছি! মুসলমানদের নারায়ে তকবির হুঙ্কার, সমাজসমূহের তলানীতে পড়ে থাকা সম্প্রদায়টিকে অন্তত একটা মানসিক শক্তি এনে দেয়, একশ’টা কোরামিনের চেয়েও বেশি কাজ করে এটা রক্তের ভেতর!
এক বিকেলে, ছড়ায় শোনা ফলিং ডাউন লন্ডন ব্রিজটা দেখে আসি, দিব্যি দাঁড়িয়ে তখনো! ঘোলাজলের নদী টেমস দেখে আমাদের কাকচক্ষুজল নদীগুলো মনে পড়ে, তখনো রঙিন পালের নৌকো ভাসতো অসংখ্য নদীতে। গুনটানা মাঝিদের তির্যক হাঁটার ভঙ্গি জয়নুলের ক্যানভাসে বিবর্ণ হতে হতে এখনো বেঁচে আছে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে অবহেলার ধূসর গ্যালারিতে! কালো, বাষ্পীয় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, নোংরা, দুর্গন্ধ, এরকম অনেক বদ-বিশেষণের কালি লেগে আছে টেমসের ইতিহাসে। এমনকি রোমানদের সময়েও বিভিন্ন ভবনের বর্জ্য ভূমিতলের কাঠের পাইপ গড়িয়ে টেমসের জলে এসে মিশেছে। লন্ডন ব্রিজের একটা পয়ঃনিষ্কাশন পাইপ সরাসরি নেমে এসেছে টেমসে। শত শত বছর ধরে টেমস বর্জ্যবাহী নদী হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে, এবং এখনও! অবিশ্বাস্য যে বিষাক্ত জলের ছোট্ট, মাত্র পনেরো মাইল দীর্ঘ এই নদীটা বিশ্বের ইতিহাসে বিখ্যাত সব নদী, আমাদের গঙ্গা যমুনা, মিশরের নীল নদ, মধ্যপ্রাচ্যের টাইগ্রীস ইউফ্রেটিস, আমেরিকার আমাজন মিসিসিপি প্রভৃতির মতই অতিবিখ্যাত!
বইয়ে পড়া ঐ টেমস নদীর সুরঙ্গে প্রবেশ করার জন্য পাতালরেলে চড়ে মনে হয় না নদীর তলা অথবা সুরঙ্গের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা! গ্রামের কুপি-জ্বালা মানুষের চোখে দেখা ছোট্টো রেল-জংশন লাকসামকেই মনে হয়, ওরে বাবা, কত লাকসাম কত বাত্তি! বড় একটা গ্রামের মতো শহর ঢাকার পর রাতের লন্ডনকেও মনে হয় আলোয় সাজানো মহানগর, লন্ডনের সাতটা দিন খুব দ্রুত শেষ হয়ে যায়, অনেক সাতশ’ দিনের স্মৃতির ভেতরও থাকে না অনেক কিছু, অথচ ঐ সাত দিনের স্মৃতিতে গেঁথে আছে কত শত কিছু!
বিলেতবাসের তৃতীয় দিন, নয় জুন, রাতের খাবার খেতে বসি আটটায়, সূর্য ডোবে সে-সময় দশটার পর, জেটল্যাগ কাটে নি তখনো। বাংলাদেশে এখন গভীর রাত। এতো ঝকঝকে প্রকৃতি বাইরে, ঘরে ফিরতে চায় না মানুষ। বিশেষ করে শনিবার আজ, এদের স্যাটারডে নাইটস ফিভারটা দেখার ইচ্ছেয় আমার হাউসমেট কেনিয়ার টাঙ্গাকে নিয়ে বেরোই, দু’পাইন্ট বিয়ার টেনেছে সে, হালকা আমেজে আছে, প্রকৃতিগতভাবে মনে হয় কালোরা বেশ ফুর্তিবাজ! এলকোহোলে অভ্যস্ত হই নি তখনো, পানি খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলি। যাবার সময় টাঙ্গা যখন বলে গুডনাইট, একটু অবাক হই, প্রত্যুত্তরে যদিও বলি ‘গুডনাইট, বাই’, দিনের আলোয় সংশয়ে পড়ি খানিকটে। কিছুদিন পরে বুঝি, রাত বারোটার পরই এদের সকাল, আলো ফুটুক বা না ফুটুক। আর বিকেল ছ’টার পর রাত, আলো ও অন্ধকারের সঙ্গে এদের দিন ও রাতের সম্পর্ক নেই। সংস্কৃতির পার্থক্যটা বুঝতে শুরু করি এখান থেকেই।
বিলেতের প্রথম দিনগুলো, মাত্রই তো ক’টা দিন, জীবনের এক দীর্ঘ অধ্যায়, প্রতিটা মুহূর্ত হৃদয়ে গেঁথে আছে, শেকড় ওপড়ানো একটা গাছ, যা জন্মেছে পাললিক নরোম শীলায়, বেড়ে উঠেছে আদরের মৌসুমি জলহাওয়ায়, কঠিন পাথুরে মাটিতে তার শেকড় খুঁজে পায় না জল, শীতল বাতাসে পাতা পায় না আলো হাওয়া! বর্ণনা-অযোগ্য এক অবস্থার ভেতর কাটতে থাকে সন্ধিকালের তরল সময়, ওগুলোকে দুঃখের দিন বলবো না কখনো, ভালো লাগতো, যদি বলা যেত কিছুটা আনন্দের, অথচ অনেক বেশি মনে হয় একটা বড় রকম পরিবর্তনের, জীবনের সঙ্গে একটা খণ্ডযুদ্ধের অথবা সংগ্রামের!
ঘরে ফেরার পথে আমার হাউসমেট তিনজনের কথা ভাবি, চমৎকার মানবমিশ্রণ! বাঙালি, পাকি, ভারতীয় ও আফ্রিকান! দু’দিনে অনেক বেশি কাছাকাছি এসেছে আফ্রিকার টাঙ্গা, ভারতীয় অভিন্দা যেন জানেই না যে পড়াশোনা ছাড়াও জীবনে আরো অনেক কিছু করার আছে। দেশ থেকে ইংরেজি শেখার দু’একটা বই এনেছে, আরো কি কি! সব সময় দেখি ওগুলোর ভেতরই ডুবে আছে, পাকিটাকে মনে হয় না পড়াশোনা করতে এসেছে, প্রথমদিনেই অনেক পাকি ইয়ার জুটিয়েছে, ওদের সঙ্গে নিয়ে সাদা চামড়া মেয়েমানুষের উপর হামলে পড়েছে কুকুরের মতো। আসছে বুধবার লন্ডন ছেড়ে যেতে হবে, অক্সফোর্ডে হয়তো আর দেখাও হবে না এভাবে, আমি এসেছি বিজ্ঞান পড়তে, পাকি ও টাঙ্গা এসেছে আইন পড়তে, আর অভিন্দা সাহিত্য!
বিকেলের ঐ চমৎকার আবেশ জড়ানো বিষয়টা পাল্টে যায় হঠাৎ, ঘরে ফেরার পর মেজাজ বিগড়ে যায়। গভীর রাত পর্যন্ত পাবে কাটাবে টাঙ্গা। পাশের রুমে থাকে বাইরে ধোপদুরস্ত অন্তরে সেফটিট্যাঙ্ক এক পাঞ্জাবি কুকুরের ছাও, তখনো ডাইনিং টেবিলে বসে কদুর তেলে ভেরেণ্ডা ভাজছে। চোখ মুখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করে–
কিঁউ ভাই, ইতনি রাত?
বলি, বাংলা ক হউরের পুত, জানোস যদি।
ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে, ও ভেবেছে আমার অন্য বাঙালি ভাইদের মতো গদগদ হয়ে ওর সঙ্গে উর্দুতে কথা বলবো। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনোযোগ আকর্ষণ করে সে, ওর ভেতরটাও দেখতে পাই কিছুটা পরিষ্কারভাবে। মানুষের দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকা সৌজন্য নয়, অথচ ডুবে রয়েছি এক ধরনের বিস্মৃতির ভেতর। ও হয়তো ভাবছে, বন্ধুতা চাইছি ওর। বিষয়টা যে মোটেও তা না, কোনোদিনও বুঝবে না সে। পৃথিবীর সেরা একটা বিদ্যাপীঠে পড়াশোনার জন্য পাঠিয়েছে ওর পরিবার, অথচ সে ধারণ করে আছে ঐ কৃষ্টি, যা মানুষকে মর্যাদা দেয়া শেখায় না। ওর আর্থসামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থান ভাবতে শেখায় যে মানুষের মধ্যে সব চেয়ে সেরা ওরা, এই অহংবোধ কাজ করে অন্যদের ছোট করে দেখতে। ওর সম্প্রদায়টিকে সামগ্রিকভাবে দোষ দেয়া যায় না, কারণ ওদেরকে বিশ্ব-দেখা শেখানো হয় একটা চোঙের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সে তো নিশ্চয় কিছুটা মেধা নিয়ে জন্মেছে, অক্সফোর্ডে যে পড়াশোনা করতে এসেছে, ওর ভিতটাকে এতো হালকা ভাবতে ইচ্ছে হয় না। ওর সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে ক্ষুব্ধ করে, পাকি হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে দেখতে ইচ্ছে করেছি ওকে, কিন্তু নিজেই পাকি করে তুলেছে নিজেকে। অনেক কিছুই লোক দেখানো ওদের, অন্তরের ব্যবহার কম জানে ওরা। এমন কি, যে ধর্মীয় সংস্কৃতি ওদের, তাও কত বেশি লোক দেখানো! মহানবীর দৌহিত্রের মৃত্যুদিনে ওদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে যেয়ে রাস্তায় মিছিল করে, ছুরি দিয়ে বুক পিঠে আঘাত করে নিজেদের রক্তাক্ত করে। প্রভুকে স্মরণ করতে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে এক সময় অজ্ঞান হয়ে যায়, জিকির করতে করতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে অচেতন হয়ে পড়ে। চোখ মুদে প্রভুকে স্মরণ করতে পারে না ওরা, অন্তর নেই ওদের। ইচ্ছে হয় ওকে একটা শিক্ষা দেই, সিদ্ধান্ত নেই, এমন একটা আচরণ করি ওর সঙ্গে, যা আমার স্বভাবের বাইরে, ওটাই হয়তো পছন্দ করবে সে!
সকালে নাস্তা খাওয়ার জন্য সাবওয়ে থেকে এক প্যাকেট চিপস ও ফ্রায়েড চিকেন এনেছি। জিজ্ঞেস করে ওগুলো কি, বলি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানেরা কি হারাম খায়? সঙ্গে সঙ্গে রক্ত চড়ে যায় মাথায়, চাঁদির চুল ব্র্হ্মতালুর উপর দাঁড়িয়ে যায় হাজার কাঁটার মতো। ওর সঙ্গে ঝগড়ায় নামার কোনো ইচ্ছে নেই, নাক ঝাড়ার মতো ঝেড়ে ফেলি ওর কথাগুলো। টেবিলের এক কোনায় প্যাকেটটা রেখে উপরে ওঠার জন্য পা বাড়াই, পেছন থেকে যখন আবার বলে, ইয়ে তো হালাল নেহি, আর থাকতে পারি না, বলি, মি. চুতমারানি, ডু ইউ নো ইংলিশ? এবার বোধ হয় টনক নড়ে। ছ’ফুটের উপর আরো আধা ইঞ্চি লম্বা শরীর আমার, গয়ালের মতো কাঁধ নিয়ে যখন ঘুরে দাঁড়াই, বোধ হয় ভয় পায় মনে মনে, গলার স্বর নামিয়ে বলে–
আই সেইড, ইট ইজ নট হালাল, উই অল আর মুসলিম, এনি ওয়ে, মাই নেইম ইজ জিন্না, নট হোয়াট ইউ সেইড।
এবার পথে এসেছো হালার পো! আমিও আসল রূপে ফিরে যাই।
সরি, মি. জাউরা, টু মি হিউমিনিটি ইজ এবাভ এভরিথিং!
মাই নেইম ইজ জিন্না, জীন্না।
সরি ফর মাই এক্সেন্ট, টু মি ইটস সেইম, মি. জ্বেনা।
ইফ ইউ ওয়ান্ট আই মে গিভ ইউ সাম হালাল ফুড।
আবার ঐ হালাল! তুমি কি আমার শালার পুত, না শ্বশুরের পুত, বুঝতে পারছি না। ব্যক্তিগত বিষয়গুলো এড়িয়ে চলি সব সময়, তবু ওকে না বলে পারি না–
লাস্ট নাইট ইউ স্লেপ্ট উইথ এ ব্লন্ড হেয়ার গার্ল, হোয়াট কাইন্ডা হালাল দ্যাট ওয়াজ, মি. জ্বেনা?
কাঁচা আনারসের রস মেশানো এক বালতি চুনের পানি যেনো ওর মুখে ছুঁড়ে দিল কেউ। মনে আছে, ছোটো থাকতে আমার মা গুঁড়ো ক্রিমির প্রতিষেধক হিসেবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিস্বাদ, সর্বপ্রকারে অসহ্য ঐ পানীয়টা নাক টিপে আমার গলায় ঢেলে দিতো। আমার চেহারার অবস্থা যা হতো তার প্রতিক্রিয়ায় অসাধারণ সুন্দর মায়ের মুখটাও ঠোঁট উল্টে কেমন বিকৃত হয়ে উঠতো। ঐ হারামজাদার চেহারাটা তার থেকেও ভয়ানক করুণ হয়ে ওঠে। আর কিছু না বলে দোতলায় উঠে যাই। যাওয়ার সময় বলি, মনে হয় স্বপ্নেও সে আশা করতে পারে নি, এক বাঙালি, যাদেরকে সব সময় কাঁচুমাচু হয়ে কথা বলতে দেখেছে ওদের সামনে, সে এমন প্রতাপের সঙ্গে কথা বলতে পারে–
আই এম সরি টু সে মি. জ্বেনা, ইফ ইউ ইন্টারফেয়ার এনি মোর টু মাই পার্সোনাল মেটার্স, দ্যান আই স্যাল কিক অন ইয়োর আস নেক্সট টাইম, এন্ড থ্রো ইউ আউট ফ্রম দ্য হাউস।
বীরত্ব দেখানোর জন্য কথা ক’টা বলি নি, বলেছি ঘৃণায়, দু’বছর আগে করাচি যেয়ে বাঙালিদের প্রতি ওদের যে তাচ্ছিল্যের প্রকাশ দেখে এসেছি, তা ভুলতে পারবো না আজীবন। জানি না বাংলাদেশী কুলাঙ্গারগুলো এখনো পাকি বলতে কীভাবে পোঁদের কাপড় তুলে দেয়! এমন কি আমার ছোট কাকাও খুব প্রভাবিত করেছে আমাকে ওদের প্রতি বিতৃষ্ণ হতে। পয়ষট্টির যুদ্ধে কাকার বাঙালি ব্যাটেলিয়ান জীবন বাজী রেখে যুদ্ধ করে ওদের দেশটাকে রক্ষা করেছে, অথচ যে-সব পাঞ্জাবি শেয়ালেরা দু’পায়ের ফাঁকে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছিল ভারতীয়দের প্যাঁদানী খেয়ে, যুদ্ধ শেষে ওরা সব তকমাইপাকি, সিতারাইহেলাল, বালস্ববাল প্রভৃতি খেতাবগুলো পেয়ে যায়, অথচ বাঙালিরা সামান্য একটা প্রমোশনও পায় নি। চাকরির মেয়াদ আঠারো বছর হওয়ায় ক্যাপ্টেন হিসাবে অবসর গ্রহণ করে পরের বছর দেশে ফিরে আসে কাকা। অনেক সময় দুঃখ করে বলতো, জানিস দাউদ, পাকিদের ঐ বদখত কুর্তাজামা, যা এখন অনেক পাকিবাঙ্গিরাও পরে বেড়ায়, পৃথিবীর সব চেয়ে নোংরা ও বিচ্ছিরি ঐ পোশাকটা পরে সেনাবাহিনীর অফিসার্স মেসে যাওয়া যেতো, অথচ এত সুন্দর পাজামাপাঞ্জাবী এলাউড ছিল না, মাংস দেয়া হতো প্রতিবেলা, কিন্তু মাছ কখনোই না, এসব অনাচারের আরো কত গল্প! বয়সের খুব পার্থক্য না থাকায় খুব মেশামেশি ছিল কাকার সাথে, জীবনের কত অম্লমধুর গল্প কাকার কণ্ঠে শোনা! পরে, উনিশশ’ একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে পঙ্গু হয়ে যায় কাকা, এখনো বয়ে বেড়াচ্ছে দুঃসহ ঐ জীবনের বোঝা!
কাপড় না পাল্টেই কিছুক্ষণের জন্য বিছানায় ছুঁড়ে দেই ক্লান্ত, অবসন্ন ও বিধ্বস্ত শরীরটা। বিলেতে আসার পর এই প্রথম মেজাজ খারাপ হল। একটা কুইক শাওয়ার নিয়ে ঘুমোতে যাই ফ্রেস হয়ে, ঘুম আসে না, মাথা থেকে রাগের চাপটা নামাতে পারিনে কোনোভাবে! শালা আমাকে হালাল চেনায়! ঝট করে উঠে পোশাক পরে বেরিয়ে যাই। সময়টা যদি আজকালের হতো তাহলে মোবাইলে ধরে ফেলতাম টাঙ্গাকে, অগত্যা অফ-লাইসেন্স সপ থেকে একটা কার্লসবার্গ নিয়ে ঘরে ফিরি। ঐ শালা তখনো টেবিলে বসে, ইচ্ছে করেই লিভিং রুমের সেটিতে বসি, বিয়ারের ক্যান খুলি ফস করে, গলায় ঢালি এক ঢোক, বিস্বাদ তেতো ঐ পানীয়ের স্বাদ আগে কখনো নেই নি, এটা যে এত পঁচা-স্বাদের, জানা ছিল না, চেহারায় কিছুই প্রকাশ করি না, যেন দীর্ঘদিন থেকে এটায় অভ্যস্ত আমি। সেটিতে শরীর কিছুটা এলিয়ে দেই, ক্লান্তির ভাব দেখাই। ভেজা বেড়ালের মতো চুপচাপ উঠে যায় ধাড়ি কুকুরছানা, একটু পরে আমিও উঠে পড়ি, বাকি বিয়ারটুকু বেসিনে ঢেলে দেই, মনের খেদ অনেকটা কমেছে, ঘুমোতে যাই, ঘুমিয়ে পড়ি।
রোববার সবাই দেরিতে ওঠে ঘুম থেকে, আমার হয় না কোনোদিনই। দুলে দুলে নিচে নামে টাঙ্গা, ব্রেকফাস্ট শেষ করে তখনো বসে আছি টেবিলে, কফি শেষ হওয়ার আগেই বিলেতের প্রভাতপত্রিকা পড়া শেষ হয়ে যায়, হয়তো এসব কোনো খবরই আকর্ষণীয় নয় আমার কাছে। ইংরেজদের পত্রিকা পড়া দেখে প্রথমে খুব অবাক হয়েছি, সকালটা সবাই পত্রিকার ভাঁজে নাক ডুবিয়ে কাটায়। অবাক হয়ে ভেবেছি, ভীষণ কিছু ঘটে গেছে নাকি কোথাও, এতো মন দিয়ে পড়ছে সবাই! পরে বুঝেছি, নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকার ইংরেজি কায়দা একটা, এতো বেশি আড়ালে রাখে নিজেদের, কোনো কিছুই শেয়ার করতে চায় না ওরা। বিপরীতে, বাঙালির আড্ডা-দেয়া স্বভাব আমার, কয়লার ময়লার মতো লেগে আছে সবখানে। কালোদেরকে ফুর্তিবাজ মনে হলেও আড্ডাবাজ মনে হয় নি। আসলে পুকুরঘাট, নুনদেয়া চিনেবাদাম, আর শহর আধা-শহরের রক তো বাংলার বাইরে অন্য কোথাও নেই, নেই শ্রাবণ আষাঢ় মাস দুটোও, বেচারারা!
কালোদের মধ্যে যেমন বদকালো আছে, তেমনি আছে অনেকভালোকালো, টাঙ্গা দ্বিতীয় গোত্রের। দাঁতগুলো কুন্টাকিন্তির দাঁতের মতো ঝকঝকে সাদা, হাসিও সাদা অন্তরের, কোনো কথা গোপন রাখতে পারে না, নাইরোবিতে অনেক পুরোনো বনেদী পরিবার ওদের, বিত্তবান। পরিবারের ইচ্ছে, ছেলে অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করে দেশে ফিরে রাজনীতি করবে, কিন্তু ওর দেখি রাজনীতি থেকে নারীদেহনীতিতে অনেক বেশি আগ্রহ। কালোরা দুটো জিনিস দিয়ে ইউরোপীয়দের মুগ্ধ করে রেখেছে, প্রথমটা হচ্ছে সংগীত, যতটা না গলার, তার চেয়ে অনেক বেশি যন্ত্রের ও শরীরের। দ্বিতীয়টা পুরোপুরি শরীরের সংগীত, সাদা মেয়েরা কালোদের বেতের মতো শরীরের পেশল পেষণ যে দারুণ উপভোগ করে, মেয়ে না হয়েও তা বুঝতে পারি। টাঙ্গা যে একটা অসাধারণ কৃষ্ণ-জীবন যাপন করবে, শুরুতেই বুঝতে পারি। এদিক দিয়ে বিধাতা কেন যে বামাস্বভাব দিয়ে বাজারে ছেড়েছে আমাকে, বুঝি না। ভালোভাবে এপ্রোচটাই করতে পারি না, মাঝে মাঝে বরং মনে হয়, কোন কুলের আমি!
লন্ডনে থাকার জায়গা পেয়েছি টেমস নদীর ওপারে, কুখ্যাত লন্ডন হোয়ার্ফ এর কয়েক ব্লক পেছনে, দ্বিতল এক টেরাসের পূর্বাংশে। লন্ডন হোয়ার্ফে রাখা হতো আফ্রিকা থেকে আনা ক্রীতদাসদের, এখনো এখানের বাতাসে কান পেতে শোনা যায় মানুষের নির্মমতার ইতিহাস। লন্ডন আই তখনো লন্ডনের আকাশরেখায় চোখ মেলে নি, লন্ডনের বিশেষ আইকন বোমা বিল্ডিং, আদর করে ওরা বলে ‘দ্য ঘেরকিন’ আকাশে মাথা উঁচু করে নি, ক্যানারি হোয়ার্ফের ওয়ান কানাডা স্কোয়ার নেই। বাইশ বছর কেটেছে দ্বিতীয় যুদ্ধের পর, লন্ডনের ক্ষত শুকোয় নি, পুনর্নির্মাণের যজ্ঞ শেষ হয় নি তখনো। একটু বয়স্কদের স্মৃতিতে সবকিছু দগদগে, আমাদের টেরাসেরই একটা অংশে থাকে বাড়িওয়ালি, ক্লেয়ার সিম্পসন। বিল্ডিংএর অর্ধেকটাই নাকি বোমার আঘাতে ভেঙ্গে পড়েছিল, পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে আবার, দেয়ালের পাথর থেকে বোঝা যায় না কোন অংশটা নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে। নতুন ঘরবাড়ি এখন আর কাঠ পাথরে বানানো হয় না, কঙ্ক্রিট ব্লক ও মেটাল ফ্রেমে বিশাল এক বিল্ডিং বানিয়ে ফেলে তিন মাসে, আমাদের দেশে ওরকম একটা বিল্ডিং বানাতে লাগে তিন বছর। যুদ্ধের কথা বলতে পুরোনো ব্রিটিশদের খুব ভালো লাগে, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধটা জিতেছিল কিনা! জার্মানদের মার খাওয়া থেকে কালোরা, রাশানরা যে কীভাবে শেষ রক্ষা করেছিল, তা কখনো বলে না। সুযোগ পেলেই যুদ্ধের আলাপ জুড়ে দেয় ক্লেয়ার। ইংরেজদের বীরত্বের অসাধারণ কাহিনীটা মিথ্যে নয়, মেনে নিতে অসুবিধে নেই ইংরেজদের বাহাদুরী। অনেকাংশে সত্যিও ওটা, কিন্তু সঙ্গে তো আরো কিছু আছে, ওগুলোকে সামনে আনে না, এ জন্য বিশ্বের সেরা অকৃতজ্ঞ জাতি মনে হয় ওদের। অবশ্য, আমরাও বা কি! স্বাধীনতাযুদ্ধে রাশানদের অবদানের কথাটা কেউ কি বলি! ভারত যা করেছে, ভারতের স্বার্থে, ওটা অন্য হিসাব। কিন্তু ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা যা করেছে, অন্তরের টানে, জাতভাই হিসেবে, ওটাই কি স্বীকার করি!
সদা ব্যস্ত শহর লন্ডনও রোববারে অলস হয়ে যায়, কালো ট্যাক্সিক্যাবগুলো বেড়ালের মতো ছোটাছুটি করে না যখন তখন, দু’একটা হুসহাস দৌড়ে যায় এদিক সেদিক, জাপানি ট্যাক্সি ইংল্যান্ডের বাজার দখল করতে পারে নি তখনো, কালো লেইল্যান্ড ও মরিস মাইনরের রাজত্ব রাস্তা জুড়ে। ঝকঝকে রোদের দিনে হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি কোথা থেকে আসে বোঝা যায় না, রাস্তাঘাট ও গাছপালা আরো চকচকে দেখায়। দীর্ঘ পথ হেঁটে, লন্ডন ব্রিজ পেরিয়ে, টাওয়ার হিলের পাশ দিয়ে বাকিংহ্যাম প্যালেসে রানিমাকে নমস্কার জানিয়ে এসে বসি হাইড পার্কে। তখন ঘাস ও গাছ, সবই শুকিয়ে ঝরঝরে আবার। কারুকাজ করা লোহার কালো রঙের চকচকে বেঞ্চগুলো বৃটিশ ঐতিহ্য, সবখানেই এদের দেখা মেলে, এমন কি রাস্তার ধারেও। সবুজ রঙেরও কিছু রয়েছে কোথাও কোথাও, খুব কম এদের সংখ্যা, মনে হয় ভিনদেশী। একটা বেঞ্চে শুয়ে মেঘমুক্ত খোলা আকাশ দেখি, কোনো পার্থক্য নেই পাংশার তীব্র নীল উজ্জ্বল আকাশের সঙ্গে, যা কিছু পার্থক্য সব, আমাদের এই ধরাধামে!
লন্ডন শহরের যে ছবি মনের মধ্যে আঁকা ছিল, এখন ওটার বাস্তবতার ভেতর ঢুকে তা ধূসর হয়ে যেতে থাকে। এতো স্বপ্নীল মনে হয় না সব কিছু। অনেক কিছুই অবাক হওয়ার মতো, কিন্তু কোনো অসাধ্য সাধন করে এসব করা হয়েছে মনে হয় না। কোনো কোনো ভবন যদিও পর্বতের মতো গম্ভীর, ওগুলোর বিশাল চওড়া দেয়ালে গাঁথা পাথরের অসাধারণ সব মর্মরমূর্তি দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছে করে অনেক সময় নিয়ে। কিছুটা আক্ষেপ হয় নিজেদেরই প্রতি, বাইরের বিশ্ব থেকে নেয়া অর্থে এসব গড়েছে এরা, যার কিছুটা আমাদের ওখান থেকেও এসেছে। অথচ আমাদের অর্থ, সম্পদ আমরা ব্যবহার করতে পারি না, জাতি হিসেবে এটা আমাদের ব্যর্থতা। এখন পাকিরা লুটে নিচ্ছে আমাদের সম্পদ, যতটা না ওদের দোষ, তার চেয়ে অনেক বেশি সহায়তা দিচ্ছে আমাদের পোষা জানোয়ারেরা। অবশ্য মহামানবদেরই যেখানে লুটতরাজে আপত্তি নেই, সেখানে সাধারণ মানুষ পিছিয়ে থাকবে কেন? অন্য সম্প্রদায়ের সম্পদ ও নারী লুট করায় কোনো সমস্যা নেই সধর্মীদের!
নামের সামনে আমার কোচোয়ানের মতো বসে আছে শেখ, তখনো আরবের সব শেখ মহান শেখ হয়ে ওঠে নি, কিন্তু কিছু শেখ তো অবশ্যই ছিল, যারা দেশের স্বার্থ বিকিয়ে, ধর্মের বাণিজ্য করে, আরব সাগরের তুঁতনীল জলে ভাসমান বজরায় পাল তুলে হারেমের বিলাসিতা করতে পারতো পুরোদস্তুর! এই কোচোয়ান অংশটাই অনেক সময় তির্যকভাবে বেশ সমীহ আদায় করে দিতো আমাকে। মিথ্যাও মিথ্যার মতো লাগতো না বলতে যে দেশের অনেক বড় ধনী আমার পরিবার, যদিও বিলেতে এসেছি দাঁত-উঁচু, কালো, ছোট্ট, এক রত্তি এক চাচাতো বোনের কাছে ভবিষ্যৎ দাম্পত্য বন্ধক রেখে। বাবা আমার নিতান্তই গরীব মানুষ। এমনকি, ময়মনসিং জেলা স্কুলের হোস্টেলে রেখে পড়াশোনা করানোর খরচ চালানোর ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। ব্রহ্মপুত্রে তখন ব্রিজ ছিল না, খেয়া পার হয়ে ওপারের স্কুলে যাওয়ার ঝক্কি থেকে বাঁচাতে চেয়ে লজিং মাস্টার হিসেবে এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের আশ্রয়ে উঠিয়ে দেয় আমাকে। সেখানেও তখন ল্যাঠা, ভবিষ্যতে বিয়ে দেয়া যেতে পারে এমন লজিং মাস্টারদেরই ছিল প্রথম চাহিদা। লজিং-দেয়া ঐ পরিবারের কন্যাটির হাত থেকে উদ্ধার করে চাচা আমার, নিজ কন্যার সঙ্গে সম্পর্কটা পাকাপাকি করার ব্যবস্থা করে ফেলে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে, কড়াই থেকে সরাসরি উনুন! ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমাকে বিকিয়ে দেয়া ছাড়া বাবার কিই বা করার ছিল আর, এ জন্য মনে কোনো খেদ ছিল না তাঁর। আমার দিক থেকে যদি বলি, আগের কন্যাটি এখনো মনে ধরে আছে, ও ছিল সত্যিই সুন্দরী, অসাধারণ মেধাবী, কোনো অংক দু’বার বুঝিয়ে দিতে হয় নি আমাকে, এবং মনে হয় না আমার প্রতি কোনো আসক্তি ছিল ওর। আর কিছু দিন ওখানে থাকলে ওর প্রেমে পড়ার সম্ভাবনা ছিল খুব জোরালো। এখনো বুঝতে পারি না, হয়তো প্রেমেই পড়েছিলাম ওর, কিন্তু বিষয়টা পরিকল্পিত হওয়ায় তীব্র আকর্ষণ জাগায় নি হয় তো!
ভবিষ্যৎ আমার কতোটা উজ্জ্বল হবে জানি না, তবে পরিবারের প্রথম সদস্য হিসেবে বিলেতে অন্তত পৌঁছাতে পেরেছি, ধারণা করি, এতেই বাবার হাতে চাঁদ এসেছে!
নামের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ, দুটোই দু’হাজার বছর আগে স্বর্গের মসৃণ পথে হাঁটা দু’জন নবীর! ভাবতে অবাক লাগে, বাবাকে এ নামটা জুগিয়েছিলেন যিনি, কী আশা করেছিলেন আমার জীবনে! মাঝখানের নামটাই চালু ছিল দেশে, এখানে এসে ঐ দাউদ এখন হয়ে গেছে ডেয়ুড, কোথাও লিখতে বলার সময় ওটা দরকার পড়ে, মিডল নেইম কেউ ব্যবহার করে না এ দেশে। দাউদকে ওরা বলে ডেভিড, ডাকে ডেইভ বলে! কেন যে নবীদের যুগ শেষ হয়ে গেল, মানুষকে ভালো পথে চলার উপদেশ দেয়ার জন্য এখনই তাঁদের প্রয়োজন আরো বেশি। যত সব ঝামেলা গ্যালিলিও, আইনস্টাইনরা বাঁধিয়ে রেখে গেছে, ওদের ছাইপাঁশ পড়াশোনার জন্য এত কষ্ট করতে হয়! অযথা সব লেখালেখি লাইব্রেরিতে ডাঁই করে রেখেছে! ওগুলো জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য মহাত্মাদের আগমন আর ঘটছে না কেন! সত্যি বলছি, পড়াশোনা করতে আমারও ভালো লাগে না, অন্তত যেগুলো পড়ে পাশ-টাশ করে ডিগ্রি পেতে হয়, সেগুলো তো অবশ্যই না, অথচ যেতে হবে অক্সফোর্ডে!
পাণ্ডববর্জিত হবে ঐ জায়গাটা, ধারণা করি। ওখানে যাওয়ার আগে লন্ডনের দিন ক’টা উপভোগ করে নেই। হাঁটতে হাঁটতে এক দিন গৌল্ডার্স গ্রীনে পৌঁছে যাই, ওখানের বেশির ভাগ মানুষজন দেখে কিছুটা অবাক হই। বাংলাদেশে তখনো গেরুয়া বসন একতারা বাজানো প্রকৃত বাউল ছিল, ইয়া লম্বা দাড়ি এক বাউলের জন্য এতো কাল পরেও মন অস্থির হয়, ওর গাওয়া নাক ডেঙা ডেং নাক ডেঙা ডেং গানটা এখনো স্মৃতিকাতর করে। এ ছাড়া ছিল লম্বা দাড়ি তাবলিগের দল। প্রথমে মনে হয়েছে এটা বোধ হয় বিলেতের কোনো মুসলমান প্রধান এলাকা, আকর্ষণ বোধ করি। হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো জোব্বা পড়া পুরুষদের অনেকেরই লম্বা দাড়ির সঙ্গে কানের দু’পাশে ঝুলে থাকা লম্বা দু’গাছি চুল, মাথার বাকি চুল ছোট করে ছাঁটা, চাঁদির উপরে ছোট্ট একটা টুপি, পড়ে জেনেছি ওটা স্কালক্যাপ আর ওরা ইহুদি! ওদের তো বেঁচে থাকার কথা না, অথবা অন্যদের! ওদের ধর্মগ্রন্থে আদেশ দেয়া হয়েছে অন্যদের ধ্বংস করে ফেলার জন্য। পরবর্তী গ্রন্থগুলোও তাই করেছে। অসহনশীলতার সূত্রপাত এখান থেকেই, যদিও এখন অনেকে বাহ্যিকভাবে হলেও কিছুটা সহনশীলতার চর্চা করে।
লন্ডন শহরের প্রায় সব জায়গায় ইহুদিদের জুয়েলরির দোকান আছে। তৈরি পোশাক শিল্প বিস্তার লাভ করে নি তখনো, অসংখ্য টেইলরিং সপ রয়েছে ওদের। আমেরিকা পাড়ি দিচ্ছে তখন ওসবের মালিকেরা, সিলেটিরা সেসব দোকান কিনে রাখে ভালো দামে।
ক্লান্ত পায়ে হাঁটার সময় একটা খাবারের দোকানের কাচে স্ন্যাঙ্ লেখা দেখে অবাক হই, ইংরেজরা অথবা ইহুদিরা সাপও খায় নাকি! বানানটা তখনো মাথায় কাজ করে নি, কিছুক্ষণ পর আরেকটা দোকানেও একই লেখা দেখে ভুলটা নিজেই ধরতে পারি, ওটা স্ন্যাইঙ্ না। কিছু একটা খাওয়ার জন্য ঢুকে পড়ি, ভাজা মাংসের মজার গন্ধে রসনা জাগিয়ে দেয়। ভাগ্য ভালো তখন বেশি কাস্টমার ছিল না। খাবারগুলো সম্পর্কে টুকটাক জিজ্ঞেস করি কাউন্টারে দাঁড়িয়ে, সরলভাবে বলে ফেলি, আমি নতুন এসেছি, এসব খাবার-দাবার সম্পর্কে ধারণা নেই। কানের পাশের লম্বা চুল দুলিয়ে বলে তা আর বলতে হবে না, বুঝেছি, কিন্তু তুমি কি মুসলমান? হঁ্যা বলাতে একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করি, আমাদের মাংস তো তুমি খেতে পারবে না, কেইক বা অন্য কিছু খাও, কফি খাও। বিষয়টা বুঝতে পারি, বলি, না গরুর মাংস দিয়ে ঐ বার্গার একটা বানিয়ে দাও, আমার দায়িত্ব আমারই, তুমি কিছু ভেবো না। মুখ কিছুটা কালো করে বার্গারের মাংসটা বৈদ্যুতিক তাওয়ায় দেয়। ট্রে নিয়ে এক কোনায় যেয়ে খেতে বসি। কী দারুণ স্বাদ! এত মজার বার্গার এর পরেও আর খাই নি কখনো। ইহুদি একটা খাবার দোকান এখনো আছে মাদাম তুসোর পাশে, কাউকে মাদাম তুসো দেখাতে নিয়ে গেলে ওটার বার্গার খাইয়ে আনি, অবশ্যই। আর যে খেতে চায় না, ওর জন্য মাদাম তুসোর টিকিট আমি কাটি না কখনো!
তখনো, পৃথিবীর এক ব্যস্ততম শহর লন্ডন, দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা কাটায় নির্ঘুম। তবুও হেঁটে রাস্তা পেরোনো যেতো ক্রসিঙের সিগন্যাল পর্যন্ত না যেয়ে। টিউবরেইল ধরে একদিন চলে আসি দক্ষিণ লন্ডনে, বন্দরের কাছাকাছি, কিছুটা শহুরে গ্রামের ছবি, আস্তাবল আছে, ভেড়ার পাল চড়ে বেড়ানোর মতো ছোট্ট চারণভূমি আছে এমন একটা খামারের পাশ দিয়ে হাঁটার সময় পুরোনো খড়ের গন্ধ মেশানো বাতাসে তীব্র আর একটা গন্ধ পাই, অনেকটা পঁচাইয়ের, কাছে যেয়ে বুঝি, একটা পারিবারিক ব্রুয়ারি। নিজেদের বিয়ার অনেক খামার মালিকই তৈরি করে নিতো তখন। খামারের এক কোনায় ছোট্ট একটা সেলিং কর্ণার আছে। সবজি, ডিম, পাউরুটি, এসব কেনার ফাঁকে বসে পান করা যেতো দু’এক পাইন্ট বিয়ার। সঙ্গ পাওয়া যেতো খামার মালিকের খনখনে স্ত্রীর ও সোনালি চুলের দু-বেণী ঝোলানো এক কিশোরী বালিকার। ইচ্ছে হয় বসি একটু, যদিও আমার কেনার কিছু নেই। এক পাইন্ট বিয়ার চাইলে বলে উনিশ পেন্স, তার মানে আগে পয়সা, বাংলাদেশের মোড়ের চায়ের দোকানের মতো উঠে যাওয়ার সময় পয়সা দেয়া নয়। কুড়ি পেন্সের একটা মুদ্রা রাখি কাউন্টারে, কাঠের জ্বালায় লাগানো ট্যাপকল ঘুরিয়ে ফেনায়িত একটা গ্লাস রাখে কাউন্টারের উপর, সঙ্গে এক পেনির চকচকে একটা মুদ্রা, ও সেলসগার্ল হাসি। ধন্যবাদ বলে বাইরের বেঞ্চে যেয়ে বসি আয়েস করে। এইলের রঙটা একটু গাঢ়, স্বাদও বেশি তেতো, কিন্তু কয়েক ঢোক পানের পর একটা প্রশান্তি ভাব আসে, হাঁটার ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।
এমন এক শহর লন্ডন, যা মানুষকে ক্লান্ত হতে দেয় না, স্যামুয়েল জনসন বলেছিলেন, কেউ যদি লন্ডনে ক্লান্ত হয়ে ওঠে, তাহলে বুঝতে হবে, সে জীবনের উপরই ক্লান্ত! পুরো একটা জীবন কাটানোর জন্য সব কিছুই রয়েছে লন্ডনে। পৃথিবীর সব সংস্কৃতির দেখা পাওয়া যায় লন্ডনের রাস্তা ঘাটে, কত বিচিত্র সেসব। কিন্তু খোদ ইংরেজরা মনে হয় অনেক বিষয়ে একই রকম, ছোট বাচ্চাদেরও দেখি খুব রিজার্ভ, কৌতূহল আছে, আড়চোখে তাকায়, কিন্তু কথা বলে না। বয়স্ক কেউ হয়তো আবহাওয়া নিয়ে স্বগতোক্তির মতো বলে, খুব গরম পড়েছে আজ, অপেক্ষা করে শ্রোতা কোনো প্রতিক্রিয়া জানায় কিনা। হ্যাঁ তাই, বললে হয়তো এক আধটা কথাও বলে। অনেকটা সময় ঘুরে বেড়ানোর পর বাসায় ফেরার পথে ক্লান্তি লাগায় একদিন বাসে উঠি, একেবারে ফাঁকা বাস। এক ইংরেজ ভদ্রলোকের পাশে বসি, আমার বাঙালি কৌতূহল, যেমনটা করেছি দেশে, জিজ্ঞেস করি, কি নাম ভাই আপনার? ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়, বলি, আমার নাম দাউদ। ও আচ্ছা জাতীয় একটা শব্দ মুখ থেকে বের করে ভাঁজ করা পেপারটা খুলে চোখের সামনে ধরে। ভাবি, দেখি ব্যাটা কতক্ষণ কথা না বলে থাকে, আবার বলি, আমি যাচ্ছি ওয়াটারলু স্টেশনে, বাংলাদেশ থেকে এসেছি, অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করতে। আবার ও আচ্ছা বলে ওর নাম বলে এবার, কীথ। ভালোই হলো তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে, লন্ডনে কাউকে চিনি না, তোমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়, নামটা লিখে রাখি। ভয় পেলো, না কি উৎপাত এড়াতে, সীট থেকে উঠে পড়ে। বলে, নেক্সট স্টপে নেমে যাবো আমি, বাই। মনে হয় পরের বাস ধরবে, বাস স্টপ ছেড়ে যেতে দেখি না ওকে। ঐ স্টপ থেকে কয়েকজন যাত্রী ওঠে, ইচ্ছে হয় না আর কারো সঙ্গে কথা বলি। ঠোঁট চুলকানো অভ্যেসটা ঝেড়ে ফেলতে আরো কয়েক মাস লাগে আমার!
কলেজ জীবন ঢাকার নটরডামে কাটানোয় কিছু কিছু বিলেতি কেতা সম্পর্কে ধারণা হয়েছিল। খাবার কখনো কাঁটাচামচে খেতে হয় নি বলে একটা ঝামেলা মনে হয় এখন, মনের দিক থেকেও কিছুটা ব্যবধান বোধ করি। নেহেরুর ঐ কৌতুকটা মনে পড়ে, ‘কাঁটাচামচে খাওয়া আর রোধক পরে ওটা করায় তৃপ্তির পার্থক্য কাছাকাছি!’
উত্তর মেরুর বিস্তৃত হিমরাজ্যের একটা গ্রিজলি ভালুকের মতো খাবার সংগ্রহ, আশ্রয় নির্মাণ, বরফে শরীর ডুবিয়ে দিনের পর রাত, রাতের পর দিনের নিদ্রা, বছরের একটা সময় ভালুকিকে সঙ্গ দিতে ক’টা দিন বা কিছু সময় ওদের সঙ্গে থাকা, এমন একাকিত্বও যাপনযোগ্য! ইংরেজরা, অথবা ইউরোপীয়রা, এরকম একাকী, স্বতন্ত্র জীবনে বড় আনন্দ পায়, এ সমাজে এসে অন্যদেরও প্রভাবিত হতে হয়, এর ভালো দিকগুলো ভালো লাগতে শুরু করে।
রুমে ফিরে ক্লান্তি বোধ করি, একটা বাথ নেয়ার ইচ্ছে হয়, এন্ড-টেরাসের নিচের একটা রুমে বাথ, ওয়াশিং, এক পাশে ক্লেয়ারের একটা লিভিং রুম, যা দেখায় অনেকটা অফিসের মতো। বাথ নিতে নিচে নামি, দেখি দরোজা বন্ধ, ভাবি ভেতরে কেউ আছে, অনেকক্ষণ পরও কেউ বেরিয়ে না আসায় দরোজায় নক করবো কিনা ভাবছি। এমন সময় ক্লেয়ার নেমে আসে উপর থেকে।
তুমি কি আমার জন্য অপেক্ষা করছো শেখ?
না, বাথরুমে যাবো, ওটা বন্ধ দেখছি।
হ্যাঁ, ওটা তালা দেয়া, তুমি কি ব্যবহার করতে চাও?
হ্যাঁ।
ছয় শিলিং।
জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকাই। বুঝতে পেরে বলে–
এখানে থাকার লিফলেটটা সম্ভবত পড়ো নি তুমি, আমারই পড়ে দেয়া উচিত ছিল, মাপ করো। ওখানে লেখা আছে দেখো, সপ্তাহে এক দিন ফ্রী বাথ ইউজ করতে পারবে, এর বেশি চাইলে প্রতিবারে ছয় শিলিং করে দিতে হয়।
ও আচ্ছা।
ইচ্ছে করলে যাওয়ার সময় একবারে বিল দিতে পারো।
ঠিক আছে।
খুলে দেবো?
দাও, বলি আস্তে করে।
ইচ্ছে হয় না বাথটাবের উষ্ণ জল ছেড়ে আসি, প্রায় ঘুম এসে যায়। পরদিন আর একটু হেঁটে স্নান করতে যাই একটা বাথহাউসে, ঘণ্টায় চার শিলিং, বাবলবাথ নেই, খুব আরাম!
আজ এতো বছর পর লন্ডনের ঐ দিনগুলোকে মনে হয় স্বপ্নের ঘোরে কেটে যাওয়া ক’টা মুহূর্ত, নতুন বিশ্ব পাওয়ার আনন্দ, ফেলে আসা দেশের দুঃখ, আত্মীয় পরিজনের জন্য বিচ্ছেদকাতরতা, বিপরীতে নতুন সব ভালো ও মন্দ মানুষের সাক্ষাৎ ও সঙ্গ লাভ, এসবের মিশ্রণ পরের দিনগুলোর জন্য অসাধারণ একটা ভিত গড়ে দেয়। মানবিক বিশেষ অসম্পূর্ণতাগুলোর অনেক কিছুই অতিক্রম করে উঠতে পারি, এবং এখন মনে হয়, দেশে থেকে অর্ধমানব হয়ে জীবন কাটানো থেকে এটা শ্রেয়তর।
দেরি করে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস বা বদভ্যাস রপ্ত করতে আরো কয়েক মাস লেগে যায়। রোববার সকালে তো লন্ডন শহরেরই ঘুম ভাঙে না, এর অধিবাসীদের ঘুম থেকে জেগে ওঠার প্রশ্নই আসে না। অনেক দিনের অভ্যেস আমার, বলা যায় পিতৃ-আদেশ পালন করতে যেয়ে ঘুমোতে হতো রাত দশটার আগে, এবং উঠতে হতো ভোর পাঁচটায়। প্রাতঃভ্রমণের পর সাঁতরে গোছল করা ছিল নিত্য অভ্যাস। ঘুম ভাঙতেই ইচ্ছে হয় আজ গোছল করে নেব সকালেই, ছয় শিলিং দিয়ে হলেও।
নিচে নেমে একটু অবাক হই, ইংরেজদের ব্যক্তিগত আবেগের প্রকাশ করতে দেখি নি এ ক’দিনে। জানালার ধারে বসে একা একা কাঁদছে ক্লেয়ার, ফিরে যাবো কিনা ভাবছি, চোখ মুছে ঘাড় ফেরায়–
আসো, আসো শেখ, কোনো দরকার আছে?
না হয় পরে আসি, তোমার বোধ হয় মন ভালো নেই।
অসুবিধে নেই, বলো কেন এসেছো?
বাথ নেবো। একটু অবাক হয়।
কাল রাতেই না নিলে! ঠিক আছে, আসো।
সিঁড়ির ধাপ কয়টা নেমে আসি।
একটু বসবো তোমার সঙ্গে?
নিশ্চয়, কোনো অসুবিধা নেই, ভালো ঘুম হয়েছে তো? বড্ড গরম পড়েছে, তাই না?
হ্যাঁ, গরম, তবে তোমাদের কাছে, আমাদের পুরোপুরি শীত।
যা বলেছো!
কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ও, হয়তো ভাবছে চেপে রাখা দুঃখের ভার কিছুটা হালকা করা যায় কিনা আমার কাছে। এখনো সুন্দরী ক্লেয়ার, স্লীভলেস সাদা একটা শার্ট পরনে, হাত ও বুকের কাছে ফ্রিল করা, মোকা রঙের মাঝারি ঝুলের গাউন ঝুলছে মেদহীন কটি থেকে, টিপিক্যাল ইংলিশ ভদ্রমহিলার সাজ, নির্দোষচিত্ত মানুষের প্রোটোটাইপ। পোশাক পরিচ্ছদে অত্যন্ত পরিপাটি ইংরেজরা, এই এক হপ্তায়ই বুঝে গেছি এটা ভালোভাবে। ওরা বলে, ড্রেস টু ইমপ্রেস, কথাটা সত্যি মনে হয় ওদের দেখে।
একটু মন খারাপ হয়েছিল শেখ, কিছু মনে করো না।
কোনো অসুবিধা নেই, ইচ্ছে হলে শেয়ার করতে পারো।
তাই? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে–
আমার মেয়ে আসবে ন’টায়, গির্জায় যাবো দশটায়। আমার স্বামীর মৃত্যুদিবস আজ। ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুকে ক্রস আঁকে।
দুঃখিত ক্লেয়ার।
ঠিক আছে শেখ, একটু থেমে, অতীত থেকে উঠে এসে বলে, জানো, বিশ্বযুদ্ধের পুরো সময়টা রণাঙ্গনে কাটিয়েছে সে, ফিরে আসে বীরের বেশে, পুরো শরীরটা নিয়ে, অনেকগুলো মেডেল বুকে ঝুলিয়ে। ওকে পেয়ে মনে হয়েছে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছি। এই যে বোর্ডিং হাউসটা দেখছো, এর অর্ধেকটাই বোমার আঘাতে ধ্বসে গিয়েছিল। অনেক সস্তায় এটা কিনে নেয় ও, তারপর দু’বছর লাগিয়ে নিজে নিজেই মেরামত করে। আর্মিতে ইঞ্জিনিয়ারিং কোরে কাজ করতো। বাড়িটার কাজ সব শেষ করে যখন একটু গুছিয়ে বসেছি, বলা নেই, কওয়া নেই, টুক করে হার্টফেল করলো মানুষটা! ডোরার বয়স তখন মাত্র তিন, যুদ্ধের সময় জন্ম মেয়েটার, আর ইচ্ছে হয় নি বিয়ে করি। ওর কথা একদিন বলবো না হয় তোমাকে। সাউদাম্পটন থেকে জাহাজে চড়েছি মায়ের সঙ্গে জার্মানি যাবো বলে, আমার ঠাকুর্মা ছিলেন জার্মানির কোলোন শহরের, ঐ যে ইউ ডি কোলোন বানায়! জাহাজের ডেকে দেখা ওর সঙ্গে, এর দু’মাসের মাথায় পরিণয়, কেমন ছিল সেই সব দিন! এই দেখো আবার চোখে জল আসতে চায়, তুমি বাথে যাও শেখ, আরেক দিন কথা হবে।
জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ক্লেয়ার, বাইরে দুরন্ত সবুজ নিসর্গ, কত রঙের ফুল যে ফুটেছে, গাছে ও ঘাসে! রাস্তার ওপাশে বিশাল চত্বর, হোলি ট্রীর ঝোপোলো বেড়া দেয়া, গাঢ় সবুজ কণ্টকময় নিচু গাছগুলোয় লাল বলের মত ছোট ছোট ফল ধরে, খুব সুন্দর দেখায় তখন, ক্রুশবিদ্ধ করার আগে যিশুকে কাঁটার মুকুট পড়ানো হয় এই গাছের লতাজাতীয় শাখায়, বড়দিনে এরা ঘর সাজায় এর শাখা-লতায়।
মনে মনে অবাক হই, আমাদের ওখানে বাবা মা অথবা অন্য কোনো আপনজনের মৃতু্যদিনে মিলাদ পড়ানো, কাঙালিভোজ, যেয়াফত, কত কিছুই না করে, যাদের সামর্থ আছে, অথচ এরা? মেয়ে আসলে গির্জায় যেয়ে প্রার্থনা করবে কিছু সময়ের জন্য, ব্যস, এটুকুই। আপনজন অনেকে মিলে একত্রে বসে একটু স্মরণ-টরন করা, বয়স্কদের দোয়া-দরূদ পড়া, এসব কিছু নেই। অবশ্য আমাদের ওখানেও দরিদ্রদের মধ্যে এসব আনুষ্ঠানিকতার বালাই নেই, বাবামায়ের মৃত্যুদিনটাই হয় তো হিসেবে থাকে না ওদের। সামাজিক ও ধর্মীয় আচার পালন করে শুধু নিম্ন ও মধ্যবিত্তের মানুষেরা। ঈদের নামাজের সময় দেখা যায় সমর্থজনেরা ঈদগাহে যায় নামাজ পড়তে, আর দরিদ্ররা সারি বেঁধে প্রবেশ পথে বসে থাকে ভিক্ষের জন্য, অথচ ধর্মটা নাকি সাম্যের! এখানে ধনী দরিদ্র সবাই প্রায় একই রকম পোশাকে গির্জায় যায়, দামী কাপড়ে সেজে, চোখে সুরমা এঁকে, একটা পার্থক্য সৃষ্টি করে না।
বিভিন্ন সমাজের মধ্যে মিশে থাকা বিভেদগুলো বিলেতে আসার পর ভালোভাবে বুঝতে শুরু করি। এগুলোর কারণ খুঁজতে থাকি, গোড়ায় যেয়ে এদের উৎপত্তিস্থল খুঁজে দেখে বিস্মিত হই। সেমেটিক এসব ধর্ম পৃথিবীর একটা অংশেই জন্ম নিয়েছিল। ভিন্ন হয়ে গেছে সমাজগুলোর ভিন্নতার কারণে। অপেক্ষাকৃত বেশি মানবিক বৈশিষ্টসম্পন্ন মানুষেরা এগুলোকেও অনেকটা মানবিক করে নিয়েছে, নিষ্ঠুরতাগুলো অনেকটা ঝেড়ে ফেলেছে। অথচ আমাদের এখানে এখনো ফতোয়ার নামে বর্বরতা, মুতা বিয়ের নামে নারীদের প্রতি চরম নির্মমতা ঘটে চলেছে অহরহ, এসব কোনো অপরাধই নয় সমাজের চোখে। এমন কি রাষ্ট্রশক্তিও কিছু করতে পারে না এদের বিপক্ষে, বরং অনেক ক্ষেত্রে সহায়তা দিয়ে যায় নিজেদের কায়েমী স্বার্থ অব্যাহত রাখার সুবিধার্থে!
উঠে যেয়ে বাথের দরোজা খুলে দেয় ক্লেয়ার। বাথরুমে রাখা ক্যামেলিয়া সুগন্ধির হালকা আবেশ ফুরফুরে করে দেয় মনের গুমোট। গরম পানিতে একমুঠো বাথ সল্ট মেশালে হালকা পান্না নীল হয়ে ওঠে টাবের পানি, নেমে পড়ি ওখানে, কী আরাম! ইচ্ছে হয় সাঁতার কাটি। বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখি পোশাক পাল্টে গির্জায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছে ক্লেয়ার। জিজ্ঞেস করি
তোমাদের সঙ্গে গির্জায় যেতে পারি, ক্লেয়ার?
নিশ্চয় পারো, কিন্তু তোমাদের ধর্মে কি এটা অনুমোদন করে?
ওটা নিয়ে ভাবি না, তুমি চাইলে তোমাদের সঙ্গে যেয়ে বসতে পারি, যদি কোনো অসুবিধে না থাকে।
তুমি চাইলে যেতে পারো, আমার কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু আমি তো ক্যাথোলিক। তোমার জানা আছে কিনা জানি না, ক্যাথোলিক গির্জাগুলোয় বসার আসনের সামনে অনেকটা জায়গা খালি থাকে নিলডাউনের জন্য, প্রার্থনার সময় আমরা কয়েকবার নিলডাউন হই, সে-সময় বেঞ্চে বসে থাকা হয়তো স্বস্তি দেবে না তোমাকে।
তা অবশ্য ঠিক বলেছো, ক্লেয়ার।
খুব যদি যেতে চাও আমার সঙ্গে, গির্জা পর্যন্ত যেতে পারো। গির্জার উল্টোদিকে একটা সপিং সেন্টার আছে, ওখানে বসে কফি খেতে পারো, রোদের সঙ্গে।
একটু হালকা করতে বলি, ওরা কি রোদের জন্যও পয়সা নেয়?
ছোট্ট একটা বাচ্চা মেয়ের মতো খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে ক্লেয়ার, আমাদের কাছ থেকে তো নেয় না, কি জানি, তোমার কাছ থেকে হয়তো নিতেও পারে।
সঙ্গে সঙ্গে ভালো হয়ে ওঠে মনটা আমারও, বলি, কেন, আমি কালো বলে?
না না, তুমি অনেক সুদর্শন, তোমার কাছ থেকে হয়তো নেবে রোদের অপচয় হবে বলে। তোমার তো ওটার প্রয়োজন নেই।
যা বলেছো, ঠিক আছে, যাবো তোমার সঙ্গে।
আমার মেয়ে আসবে ঠিক ন’টায়, ন’টা পঞ্চাশে বেরোবো।
ঠিক আছে, বলে ঢুকে পড়ি আমার আপাত প্রিয়, স্বপ্নের ঘোরে!
২
অক্সফোর্ডের দিনগুলো আমার চৈনিক ড্রাগন উৎসবের মতো বর্ণাঢ্য ও বিপুল, আনন্দ-উচ্ছল, কলরবময়, বিহ্বলপুলকিত ও উপভোগ্য! যেনো এক ড্রাগনের ভেতর প্রবেশ করে আমার আত্মা, ওখানে দগ্ধ হয়, জারিত হয়, এবং বেরিয়ে আসে এক ড্রাগনশিশু হয়ে, জিহ্বা যার এখনো আগুনের। আরো পরে বুঝতে পারি, ঐ আগুন নবলব্ধ জ্ঞানের গরিমায় উজ্জ্বল, বাইরে আসার জন্য যা উৎসাহ দেয় প্রতি মুহূর্তে, এবং ওটা প্রশমিত হয় প্রকৃত জ্ঞানের দ্বারপ্রান্তে এসে নিজের তুচ্ছতা আবিষ্কার করতে পেরে, যখন ঐ উপলব্ধিটা হয় যে ‘জ্ঞানসমুদ্রের তীরে এক বালুকণা মাত্র’ আমি!
পনেরো জুন, কীভাবে মিলে যায় ইতিহাসের ঐসব তারিখের সঙ্গে যে-কিনা এখন কোনো-কেউ-না পৃথিবীর এই জটিল ইতিহাসের! কি ঘটেছিল সেদিন পলাশীর আমবাগানে? আমার ক্ষেত্রজীবী পূর্বপুরুষেরা লাঙল চালানো ক্ষণিকের জন্য থামিয়ে বিস্ময় চোখে শুধু দেখেই শান্ত ছিল দীর্ঘকাল!
হতদরিদ্র আজকের বাংলাদেশ তখন ছিল সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সব চেয়ে বেশি সম্পদশালী। যে ভারতবর্ষ অন্বেষণে সারা পৃথিবী হন্যে হয়ে ঢুঁড়েছিল ইউরোপীয় নাবিকেরা, ওটার সেরা অংশটা কী করে ছোবড়ায় পরিণত হয়েছিল, তা গবেষণার বিষয়। ইংরেজদের আর্কাইভের তথ্য বলে, পলাশীর পরাজয়ের পর কম করে হলেও বছরে পাঁচ কোটি টাকা বাংলা থেকে পাচার হতো, আড়াইশ’ বছর পর এটার অর্থমূল্য এখন কত হতে পারে হিসেব করলে মাথা ঘুরে পড়ে যেতে হবে। দশ বছরে যে অর্থ বাংলা থেকে বিলেতে এসেছে হাজার বছরেও বাঙালি তা বিলেত থেকে বাংলায় পাঠাতে পারবে না। কেন ঘটেছিল এটা? বাণিজ্য, সবই বাণিজ্য রে ভাই। ধর্ম, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, ঘৃণা, এ সবই পরের বিষয়। দেশপ্রেম? ওটা যে কী বস্তু ঐ কৃষক ভাইয়েরা তখন বুঝতেই পারে নি। কি এমন বাণিজ্য ছিল বাংলার যে পৃথিবীর একটা সমৃৃদ্ধতম অঞ্চল হয়ে উঠেছিল? মিহিবস্ত্র, রেশম, মসলা, আফিম, এসব রপ্তানি করে যে পরিমাণ অর্থ আসতো বাংলায় তা দিয়ে মূল্যবান পাথর, হিরে-জহরত, সোনাদানার পাহাড় বানানো সম্ভব হয়েছিল। তখনকার জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, ওয়াজিদদের সম্পদ হিসাব করলে মূর্ছা যেতে হবে, থাক ওসব।
নবাবী আমলে বাংলা স্বাধীন ছিল। দিল্লির তোয়াক্কা করতো না বাংলার স্বাধীন নবাবেরা। ব্যবসায়ীরা স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে পারতো, উৎপাদকেরা পণ্যের মূল্য নিজেরা নির্ধারণ করতে পারতো, প্রচুর উদ্বৃত্ত জমতো ওদের ভাণ্ডারে। কিন্তু ইংরেজ শাসনে উৎপাদনের স্বাধীনতা পুরোপুরি খর্ব হয়ে পড়ে। ওদের ইচ্ছানুসারে পণ্য উৎপাদন করতে হতো, এমনকি মূল্যও নির্ধারণ করে দিতো ওরা। ফলে বিলুপ্ত হয়ে যায় বাংলার ঐতিহ্যবাহী সব শিল্প। চিরকালীন উদ্বৃত্ত শস্যের দেশ এই বাংলায় জবরদস্তি করে নীল চাষ করিয়ে কৃষক সমপ্রদায়ের মেরুদণ্ড পুরোপুরি ভেঙ্গে দেয়া হয়, যা এখনো সেরে ওঠে নি, হয়তো উঠবেও না কোনোদিন।
উনিশশ’ সাতচল্লিশের পনেরো জুনের সূর্য ওঠার আগেই ভূমিষ্ট হওয়ায় বলা যেতে পারে এক প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারে জন্ম আমার, ফলে আলোর প্রতি এতো তৃষ্ণা, সব রকম, সর্বার্থে। অক্সফোর্ডে নেমেই এক আশ্চর্য পরিবর্তন অনুভব করি, দেহে ও মনে। একটা ভূমিকম্পের মতো দুলে ওঠে শরীর, অতিকাঙ্খিত অবস্থানে পৌঁছে সাফল্যের আনন্দে যেনো শিথিল, অবশ অনুভূতি, মঞ্জিলে-মকসুদে পৌঁছার লক্ষ্য অর্জনে চিত্ত নির্ভার, বিহ্বল। এখানে আসার জন্যই কি প্রথম জীবনের বাইশটি বছর অক্লান্ত সাধনা করেছি!
লন্ডনের চমকলাগা দিনগুলোর মতো উচ্ছ্বাস নেই শান্ত ও নিরিবিলি অক্সফোর্ড শহরে, ঘর থেকে বের হয়ে গ্রীষ্মের প্রকৃতি দেখারও ইচ্ছে হয় না, পরপর তিনদিন ঘুম ও আলস্যের কাছে পুরোপুরি সমর্পণ করি নিজেকে, এক ঘুমের পর দুই ঘুম, এমনকি দুই ঘুমের পর তিন ঘুমও সেরে নেই কোনো স্বপ্ন না দেখেই।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ শুরু হওয়ার এক হপ্তার মধ্যেই আমার শিবনেত্র ফুটতে থাকে। অর্থ ও ঈশ্বরের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য যে সম্পর্ক তার বিপরীতে আবিষ্কার করি শ্রম ও জ্ঞানের সম্পর্ক। যত বেশি ঈশ্বর তত কম অর্থ, দরিদ্র বিশ্বে ঈশ্বর অনেক বেশি প্রতিষ্ঠিত, বিত্তবানের কাছে ঈশ্বর তেমন কোনো মূল্য বহন করে না। একটা আরেকটার বিনিময়ও বটে, পরস্পর বিপরীতমুখী সম্পর্কিত দুটো সত্তা, যে কারণে ধর্মান্তরিতকরণের ঘটনাগুলো ঘটেছে, নতুন নতুন ঈশ্বর এসেছে। পুরাতন ঈশ্বর পরিত্যাগ করেছে মানুষ, আস্থা হারিয়ে নয়, অধিকতর অর্থ প্রাপ্তির প্রত্যাশায়, অর্থ এখানে ব্যাপকার্থ প্রকাশ করে। যেমন ফ্রয়েড লিবিডো শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন মানুষের অদস ও অহংএর কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে। সার্বিক প্রত্যাশাপূরণের বহুমুখী এ অর্থ বিভিন্ন সময়ে মানুষকে নতুন নতুন ধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু শ্রম ও জ্ঞান সরাসরি সম্পর্কিত, একটা বাড়লে অন্যটা কমে না, জ্ঞানার্জনের জন্য শ্রমের বিকল্প নেই, যত শ্রম দেয়া যায় তত জ্ঞানার্জন করা যায়। বলবো না শ্রমবিমুখ ছিলাম কখনো, কিন্তু এখন, পরিস্থিতি সামলাতে যেয়ে এটার মাত্রা এতোটাই বাড়িয়ে দিতে হয় যে অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, অথচ এই জ্ঞানটুকু, জানি না এর প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার কতটা, অর্জনের জন্য আমার স্কুলশিক্ষক পিতা নিজের জীবন তুচ্ছ করেছেন, জাগতিক সব প্রাপ্তি নির্দ্বিধায় বিসর্জন দিয়েছেন।
অক্সফোর্ডের শিক্ষা জীবনের শুরুতে প্রাজ্ঞ এক টিউটর পেয়ে যাই, ভারতীয় আশ্রমগুরুদের বিষয়ে পড়েছি, কবিগুরুর শান্তিনিকেতনের পাঠদান পদ্ধতি বিষয়ে জেনেছি, এখানে এসে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ একটা বিদ্যাপীঠের পাঠদান পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে শুধু শিহরিতই হই নি, অনেক বিষয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গি আমূল বদলেও গেছে, নিজেদের সংকীর্ণতা ও অসামর্থ বিষয়ে প্রচণ্ড বিষাদাক্রান্ত হই, নালন্দা নামে সুপ্রাচীন একটা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদেরও ছিল, যার নামই এখন আমাদের প্রায় কেউই জানে না!
প্রথমে আমার পাঠক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেয় আমার টিউটর পল ব্রাইডাল, এবং প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই আস্বস্ত করে, ভেবো না, সবকিছুতে অভ্যস্ত হয়ে যাবো আমরা। যখন বলি এভাবে এটা করতে চাই, ওটা ওভাবে লিখতে চাই, জবাবে বলে, হ্যাঁ ওটা করবো আমি, ওটা লিখবো আমি! একটু খটকায় পড়ি, আমার ওসবকিছু টিউটর কেন করে দেবে? পরে বুঝতে পারি, ঠিক আছে, তুমি করবে ওটা, বলে না ওরা! সংস্কৃতির পার্থক্য ভাষার ভেতরও যে কত জটিল ও ভিন্ন, একটু একটু করে বুঝতে শুরু করি।
কয়েক সপ্তাহের মধ্যে উপমহাদেশের ক’জন শিক্ষার্থীর সঙ্গে বন্ধুত্ব জমে ওঠে, একটা বিষয় বুঝতে পারি, দেশের ভেতর যত রেষারেষি ও সংকীর্ণতা থাকুক না কেন, অক্সফোর্ডের পরিবেশ ওগুলো ধুয়ে-মুছে দেয়। দু’জন ভারতীয় ও একজন দক্ষিণ আফ্রিকান সঙ্গে নিয়ে একটা ভাড়া বাসায় উঠে যাই দু’মাস পর। কিছু স্বস্তি পাই মনে, দাঁত দেখিয়ে জোরে হাসা যায়, পেঁয়াজ কাচামরিচ দিয়ে ঝাল-মুড়ি খাওয়া যায়। যদিও ঘরের পাশের বাঙালি রেস্টুরেন্টে প্রতিদিনের কাস্টমার আমি, মাঝে মাঝে রান্নার চেষ্টাও করি। শুক্র ও শনিবার সন্ধ্যায়, বিশেষ করে, রেস্টুরেন্ট এড়িয়ে চলি ভিড়ের জন্য। অন্য সন্ধ্যাগুলো বেশ আড্ডা জমে উপমহাদেশের বাঙালিদের। কয়েকমাসের মধ্যে আড্ডাকুলশিরোমণি খেতাব জুটে যায়। আড্ডাগুরু মুজতবা আলীর জার্মানির দিনগুলো স্মরণ করি। এর মধ্যে আবার মোড়লগিরি মনোভাব জেগে ওঠায় দেশীয় একটা সংগঠন গড়ে তুলি, এটার সভাপতির পদ গ্রহণ করতে হওয়ায় বেশ কিছু চমৎকার সুযোগ সুবিধা পেয়ে যাই। আমাদের গ্রাজুয়েশান কোর্সের ফর্মাল ইনডাকশান উৎসবে অতিথি হয়ে আসেন মহামান্য রানি ভিক্টোরিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক ডাইনিং হলে রানির সঙ্গে ডিনারের একটা আমন্ত্রণ পেয়ে যাই এসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে। পোশাক অবশ্যই ফর্মাল, বলার অপেক্ষা রাখে না। সাধারণ স্যুটই নেই, সেখানে ফর্মাল ডাইনিং স্যুট পাবো কোথায়। পাঞ্জাবি এক বন্ধু, নেসার আমেদ, বুদ্ধি দেয় ভাড়া নিতে। এতোগুলো টাকা এক সন্ধ্যার জন্য, মন খচখচ করে। সে প্রস্তাব দেয় এসোসিয়েশন খরচ দেবে, নয়তো আমরা কয়েকজনে চাঁদা তুলে দেবো। পোশাক ভাড়া করে নিয়ে আসি, কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। ফর্মাল স্যুটের বিকল্প ছিল, জাতীয় পোশাক, কিন্তু ঐ জ্বেনা টুপি তো মাথায় চড়াবো না, শেষ পর্যন্ত পাজামা-পাঞ্জাবীর উপর প্রিন্স-কোট চাপিয়ে কারুকাজ করা নেপালি-মরোক্কান মিশেল এক ধরনের গোল টুপি মাথায় চাপিয়ে ডিনার হলে ঢুকি। সব ফর্মাল পোশাকের মধ্যে ঐ রাতে এক গোঁয়ার-গোবিন্দ বাঙালিই ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম। ভালো কি মন্দ বুঝি নি, আড়-চোখে এক ঝলক দেখে নিলেন রানি-মা, তখনকার মতো মনে হলো, ধন্য হলাম মা গো! খাবার কি খেয়েছিলাম মনে নেই, রেড ওয়াইনটা কোন বাগানের আঙুর থেকে বানিয়েছে জানি না। তবে, এ দুনিয়া ফানা হইবের পর স্বর্গের সুরা ওখান থেকেই যাইবে।
বিলেতে এসে অনেকে নামের ঝামেলায় পড়ে, প্রথম নাম, মধ্য নাম, শেষ নাম, এরকম ভাগাভাগিতে অভ্যস্ত নই, নাম বলতে এক ভালো নাম। ডাক নাম সীমিত থাকে পরিবার ও বন্ধুদের মধ্যে, এখানের শেষ নামটা পারিবারিক নাম, বলার সময় সামনে একটা মিস্টার লাগায়। আমাদের অনেকের প্রথম নামটা হয়ে যায় নামগুলো, আকম, আসম, আঃ ম এরকম আদ্যক্ষর সবগুলোকে ভাঙ্গাতে হয়, ফলে ঝামেলাটা বোঝে, যার আছে ওসব। আমার নামের আগে একটা শেখ কিভাবে জুড়ে বসেছিল জানি না, ওটাই কিছুটা গোপন আনন্দ দেয়। শেখ বলতে ওরা বোঝে আরবের শেখে জ্ঞাতিকুল, কুটুম্ব। ধরে নেয় আমিও এক বিশাল ধনীর দুলাল, সখ করে পড়তে এসেছি বিলেতে। সুবিধে হয় যেটা, দেশে যে নিজেকে বিক্রি করে এসেছি তা ভুলে একের পর এক কিছু বান্ধবী পেয়ে যাই, ভালোই যায় আমার দিনকাল।
অঙ্ফোর্ডের পাঁচটা বছর যে কীভাবে কাটিয়েছি! এখন মনে হয় স্বপ্নের ঘোরে কেটে গেছে সেসব দিন, মানুষের সেরা দিনগুলো কেটে যায় ঘোরের ভেতর, তখন বুঝতেই পারে না যে জীবনের মধুরতম দিনগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে, জীবনের এতো মধু কখনোই আর আহরিত হবে না। ছোট্ট আইসিস নদীতে বান্ধবী নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্যানু চালানো, নদীতীরে চোখজুড়ানো প্রাচীন গাছের সারি, গ্রীষ্মের বাতাসে সবুজ ঘাসের গালিচায় শুয়ে ধূমপান, বীয়ারের শীতল প্রশান্তি, নদীতে ভেসে থাকা রাজহাঁস, অসংখ্য ফুলের চেনা অচেনা সৌরভ, সবই আছে তেমনি এখনো, শুধু আমার সেসময়টা নেই, কেটে গেছে!
মাঝে মাঝে ছোটোখাটো উত্তেজনাও তৈরি হয়েছে, অক্সফোর্ডের দ্বিতীয় বছরে বাসা বদলে আরেকটা ভালো জায়গায় উঠে যাই, বাসা ছেড়ে দেয়ার কথা ছিল দুপুর দু’টায়। বন্ধু আবীরকে নিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে ধীরে সুস্থে সাড়ে তিনটায় ঘরে পৌঁছে দেখি মালপত্র সব রাস্তায়! কাছে যেতেই দরোজা খুলে আগুনচোখে ঘড়ি দেখায় বাড়িওয়ালি। একটু থতমত খেয়ে যাই, এ রকম তো ভাবি নি। গজগজ করে ওঠে আবীর, জিজ্ঞেস কর, একটু দেরি হওয়ায় মালামাল রাস্তায় ফেলে দেবে নাকি! না-হয় আরেক দিনের ভাড়া নিতো। থামাই ওকে। মুখ কাঁচুমাচু করে বলি–
দুঃখিত, একটু ঝামেলায় পড়ে দেরি হয়ে গেছে।
ঠিক আছে, দেখো তোমার জিনিসপত্র ঠিক আছে কিনা।
ওসবের দিকে না তাকিয়ে বলি–
সব ঠিক আছে, কিছু ভেবো না তুমি। একটু থেমে বলি–
কিছু মনে করো না, তোমার নতুন ভাড়াটে কি এসে গেছে?
না, কাল আসবে।
যদি অনুমতি দাও তাহলে হুভার করে ঘরটা ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করে দেই।
কিছুটা শিথিল হয় ওর মুখের পেশি।
ঠিক আছে, ধন্যবাদ তোমাকে। ওটা আমি করে নেবো।
ওকে, ভালো থেকো, তোমার এতোদিনের আতিথেয়তার জন্য অনেক ধন্যবাদ, বাই।
বাই।
দরোজা বন্ধ করার পর বলি আবীরকে–
ওদের সঙ্গে পারবি? শুধু শুধু ঝামেলায় জড়ানো, কথার বরখেলাপ তো আমিই করেছি, দোষটা তো ওর না।
রাগ তখনো থামে নি আবীরের, জিজ্ঞেস করি–
এখন এগুলো নিবি কীভাবে?
কীভাবে আবার, মাথায় করে।
চল স্যুটকেইস দু’টা আগে রেখে আসি, তারপর টুকটাক।
কয়েক খেপ লেগে যাবে যে?
যাবে, অসুবিধা কি?
খেপ মারামারি ভাল্লাগে না আমার, ট্যাক্সি ডাকি কয় শিলিং আর নেবে।
ডাকো, তোমার আছে যখন।
মালামাল সব তোলার পর ট্যাক্সিতে দু’জনের বসার জায়গা থাকে না। চাবিটা ওর হাতে দিয়ে হাঁটা দেই। ভালোই হলো, হাঁটতে ভালো লাগছে বরং। ‘ব্রিটিশ টাইম’ বিষয়টা ভুলি নি এখনো, এটার কোনো খারাপ দিক নেই, সবই ভালো!
রুমে ঢুকে দেখি মালপত্র সব দোতলায় ওঠাতে যেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আবীর, বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে।
একা একা সব উপরে তুলতে গেলি কেন? জবাব দেয় না।
আবার বলি, বইগুলো যা ভারি।
ভারি বিদ্যের বই তো ভারি হবেই।
যা বলেছিস, ওঠ, বালিশ দিয়ে দেই, আরাম করে শো।
থাক, চল বেরোই, একটু ঘুরে আসি।
চল তাহলে।
বুঝতে পারি মন খারাপ হয়েছে ওর। এটা না করলেও পারতো ভদ্রমহিলা। সংস্কৃতির পার্থক্য প্রতি পদক্ষেপে বুঝে যাই। হাজার হলেও আমরা তো বিদেশি, আমাদের ওখানে বিদেশি কেন, কারো প্রতিই কি এটা করি আমরা? ম্যানার এটিকেটে নাকি ওরা পৃথিবী-সেরা, কথায় কথায় দুঃখিত আর ধন্যবাদ!
মনের গুমোট কাটাতে শহর ছাড়িয়ে কাউন্টির সীমানায় এসে পড়ি দোতলা এক বাসে চড়ে। নেমেই হালকা হয়ে যায় মন, প্রকৃতির বুনো গন্ধ, বহুবর্ণিল সাজ, আকাশে অবাধ আলো, সবই যেনো অফুরান! ঝোপালো গোলাপের ঝাড় কম করে হলেও বিশ ফুট উঁচু হয়ে লতিয়ে ওঠেছে একটা পাহাড়ের গা বেয়ে, বিভিন্ন রঙের গোলাপে ছেয়ে আছে পুরো পাহাড়, নিরিবিলি রাস্তা ধরে এগোলে দূরে দেখা যায় অপূর্ব এক গ্রাম, মনে হয় না ওখানে কেউ বাস করে। ছবি তোলার জন্য গড়া হয়েছে। একটা খামারের পাশ দিয়ে হেঁটে যাই। এতো সুন্দর একটা ঘোড়া ওখানে ঘাস খায় না! মহিনের ঘোড়াটা কি এতো সুন্দর ছিল? জীবনের একটা বড় সখ ছিল, বাড়ি না, গাড়ি না, ঘোড়ায় চড়া, ভগবান মহাশয় সাফ জানিয়ে দিয়েছেন: হবে না।
সামনের রাস্তা ডানে বাঁক নিয়ে কোন দিকে গেছে বোঝা যায় না, কিছুটা চড়াই, একটু ইতস্তত করে এগিয়ে যাই, যেতে যেতে মনে হয় বেশ বড় বাঁক, শেষ প্রান্ত নেমে গেছে অনেক নিচে, তারপর আবার উঠে গেছে অনেক উঁচু পাহাড়ে, বিশাল এক সাদা ঘোড়ার ছবি ওখানে, হর্স ট্রেইল। মোটর গাড়ি মানুষকে গতি দেয়ার আগে ঝড়োগতি ঘোড়ার গাড়ি চলতো ঐ পথ ধরে, পায়ে হেঁটে এখন ওখানে পৌঁছানো যাবে না। যে খামারটা ছিল হাতের বাঁদিকে ওটা এখন ডানে। খামারবাড়ির পেছনে ডাঁই করে রাখা টুকরো কাঠের বিশাল এক স্তূপ, এখনো ভিজে, মাসখানেকের মধ্যে শুকিয়ে এলে গোলা-ঘরে উঠে যাবে, তারপর গ্রামের বাড়িঘরের চিমনি দিয়ে বেরিয়ে যাবে ধোঁয়া হয়ে। ছোট্ট একটা স্প্যানিয়েল বিশালদেহী এক শেফার্ডের সঙ্গে বাপ-বেটার মতো খেলছে, কোনো একটা কাঠের টুকরো স্প্যানিয়েলটা কামড়ে ধরলে ছিনিয়ে নেয় শেফার্ডটা, দৌড়ে রেখে আসে কিছুটা দূরে, আবার ছুটে যায় স্প্যানিয়ালটা, আবার ছুটে যেয়ে অন্যত্র সরিয়ে রাখে শেফার্ডটা, কাঠগুলো ছড়িয়ে যেতে থাকে, কোথা থেকে মনিবের হাঁক শুনে ওসব ফেলে দৌড়ে যায় দু’জনেই। খামারের পেছনে ছোট্ট একটা ঝরনা, পাহাড়ের চূড়ায় কোটি কোটি বছর আগের ছোট্ট একটা পাললিক বুদবুদ ফেটে গিয়ে গড়ে দিয়েছিল ছোট্ট এই জলাধার, খামারের এই জায়গাটা। কয়েকটা গাছ বেড়ে ওঠার পর কিছুটা সরে আসে ঝরনাটা, বাঁকা হয়েও বেঁচে আছে একটা গাছ। ওটার এক পাশের শেকড় জলে ডোবানা। দু’জনেরই ইচ্ছে হয় ঝরনাটা কোন দিকে নেমে গেছে তা দেখতে। পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নেমে যাই, দূরে যেতে হয় না, দুটো পাহাড়ি ভাঁজের ভেতর দিয়ে শীর্ণ একটা নদীর মতো ডান দিকে বয়ে চলেছে। যাওয়ার পথে কোনো শিলাখণ্ড, ধারালো ম্যালাকাইট, অথবা অন্য কোনো আগ্নেয় শিলা পেলে ধুয়ে ঝকঝকে করে রেখেছে।
এটা মিশেছে আইসিসে।
কীভাবে বুঝলি?
অঙ্ফোর্ডের এদিকটায় আর নদী নেই।
কেন, চেরওয়েল ঘুরে এদিকে আসতে পারে না?
তোর মতো সবাই ও সবকিছু খামাকা ঘুরে না।
ঝরনারা ঘুরে কম, নদী ঘুরে বেশি।
হ্যাঁ, সমুদ্র একেবারেই ঘুরে না।
একটা সাইডার হলে হতো।
হতো, কিন্তু হচ্ছে না।
যে গাছটার অর্ধেক শেকড় ছিন্ন হয়ে বাঁকা অবস্থায় আবার দাঁড়িয়েছে মাথা উঁচু করে সেটাকে মনে হয় উদ্বাস্তু মানুষের প্রতীক। গাছের নিচ থেকে কয়েকটা ফল কুড়িয়ে নেই, চেস্টনাট। বাংলাদেশে এ গাছটা ছিল, এখনো আছে বলা যায় না, হাই-ঈল্ড ভ্যারাইটি হয়তো বিলোপ করে দিয়েছে। ভেষজ অনেক গুণ এই চেস্টনাটের, এর কাঠে আসবাব বানানো হয়, চেস্টনাটের খোসায় অসংখ্য নরম কাঁটা, তিনটা চেস্টনাট হাতে নিয়ে লোফালুফি করে আবীর, বেশ ভালো জাগলারই সে, একটাও মাটিতে পড়ে না, একবারের জন্য হলেও! গাছের গুচ্ছটা যেখানে শেষ হয়েছে তার আশেপাশে বুনো ফুলের ঝাড়, অনেক ল্যাভেন্ডার ফুটেছে, ট্যালকম পাউডার ও মেয়েদের শরীরের গন্ধ মিশে যা হয় তা থেকে ভিন্ন ও তীক্ষ্ন এই ল্যাভেন্ডারের সৌরভ। ফুলের একটা মঞ্জরি তুলতে যেয়ে দেখি ঝোপের ভেতর একটা হ্যাজহগের কঙ্কাল, অনেক বছরের পুরোনো। বুনো ফুলের বাগানে কোমল এক প্রাণের অবসান! একটা কবিতাবোধ কাজ করে। প্রাণীটা মরে গেছে ওসব না জেনে, না বুঝে!
এটা বলতে পারো না, ওর বোঝার ও প্রকাশ করার মাধ্যম হয়তো ভিন্ন। তা ছাড়া, বিশ ডেসিবেলের নিচের কোনো শব্দতরঙ্গ বোঝার ক্ষমতা তোমার কানের নেই। আর এখানে কবিতা আসে কীভাবে? আমার ভেতর দুঃখবোধ কাজ করে।
ওখানেই তো কবিতা আরো বেশি ক্রিয়াশীল, তীব্র পুত্রশোকের মাঝে প্রাণভরে হাস্নাহেনার সৌরভ নেন কবি নজরুল, রচনা করেন অপূর্ব সংগীত, আঘাতে আঘাতে জীর্ণ রবিঠাকুরের অন্তর থেকে বেরিয়ে আসে রক্তরং গোলাপের মতো অসাধারণ সব কবিতা।
এখন কাব্য না হলেও চলবে।
ঠিক আছে, কবিতা, বয় আকার বাদ।
আকাশে রা দেব আগুনের গোলাটা মাথা থেকে কাঁধে নামিয়েছে, ওটার আঁচ কমে এসেছে, ওজনেও হয়েছে হালকা, খুব দ্রুত এখন পশ্চিমে নেমে যেতে পারবে দেবজী, অথচ এ সময়টাই দীর্ঘ চাই আমাদের! ঝোপের পাশে শুয়ে পড়ি দু’জনে। ডান দিকের পাহাড় পেঁচিয়ে যে রাস্তাটা নিচে নেমে গেছে অনন্তের পথে, ওটার সামান্যই দেখা যায় এখন। চুপচাপ শুয়ে দাঁতে ঘাস কাটে আবীর, হালকা হতে দেই ওকে, অল্পেই আপ্লুত হয়ে পড়ে সে।
একটা কালো মাইনর গুবরে পোকার মতো ধীরে ধীরে বেয়ে ওঠে পাহাড়টা, থাকে কোথায় ওটা? প্রায় চূড়ায় উঠে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়, যাক যেদিকে খুশি। কিছুক্ষণ পড়ে ওটার গোঙানি শুনি আবার, আস্তে আস্তে কাছে আসে, আবীরও কান পেতে রাখে, স্পষ্ট শুনতে পাই ওটার ইঞ্জিনের ঘড়র-ঘর শব্দ, একটু দূরে মিলিয়ে যেয়ে আবার একেবারে কানের কাছে এসে থেমে যায়, দু’জনেই ঘুরে যাই, ঝোপের বিপরীত দিকে থেমে গেছে ওটা, ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়। কীরে বাবা, এখানে রাস্তা এলো কোথা থেকে? তার মানে ঝোপের ওপাশ দিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে কোথাও।
আরোহীদের কথা শুনতে পাই, দু’জনের হাসি ও জোরে জোরে কথা বলা নীরব প্রকৃতিতে আলোড়ন তোলে। চলে যাবো কিনা ভাবছি, ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে আবীর ইঙ্গিতে বলে চুপচাপ শুয়ে থাক। ওদের খুনসুটি শুনি, একটু পড়ে বুঝতে পারি মিলিত হয়েছে ওরা, মৃদু তালির ছন্দ আমার ভেতরেও প্রচণ্ড ভাব জাগিয়ে তোলে, কান পেতে ঘাসের গুঞ্জন শুনি অগত্যা। কিছুক্ষণ পড়ে দেখি পুরোপুরি নগ্ন হয়ে ঝরনার ভেতর লাফিয়ে পড়ে ওরা, ওখানে একটা জলাধারও আছে নিশ্চয়, এখান থেকে বোঝা যায় না। সাধারণত বাইরে স্নান করে না এরা, তবে এটা বোধ হয় অনেক পরিচিত এদের। ঘাড় ঘুরিয়ে উপরে তাকালে আমাদের দেখতে পাবে কিনা বুঝতে পারি না, নাও পেতে পারে, কারণ ঝোপটার সঙ্গে মিশে আছি দু’জনেই, পেলেও বা কি, আমরা তো আর লুকিয়ে দেখতে আসি নি ওদের, আগে থেকেই এখানে আছি, অবশ্য কেউ দেখতে পেলো কিনা এর পরোয়াও করে না এরা। গ্রীষ্ম হলেও ঝরনার জল ঠাণ্ডা থাকে, একটু পরে উঠে যায়। ফিরে যেতে থাকে ওরা, যে পথে এসেছিল ও পথেই আবার গুবরে হয়ে যেতে দেখি গাড়িটাকে।
ঝরনায় স্নান করবি?
করতাম, সঙ্গে বান্ধবী থাকলে, তুই না থেকে।
বান্ধবী নিয়ে আসার মতো জায়গাই বটে।
চিনে রাখলাম।
আসবি নাকি?
আসতেও পারি।
জানাস।
কেন, লুকিয়ে দেখার জন্য?
আমার তো ইংলিশ বান্ধবী নেই, দেখাই সব।
বাধা কোথায়?
বুঝতি, যদি বাবার সংসারে থাকতি, আর সিলেটি হতি।
আমিও রক্ষণশীল পরিবার থেকেই এসেছি।
পার্থক্য আছে।
থাক, চল উঠি।
গত তিন মাসে একটা চিঠিও লেখা হয় নি আমার দেশের সাদা মেঘেদের কাছে, বুকের ভেতর মেঘ গুরগুর করে, ব্যাঙের করতলের মতো ফুলে ওঠেছে হাতের তালু দুটো, হালকা করার কোনো সুযোগই হয়ে ওঠে নি।
অক্সফোর্ডের সিটি সেন্টারের একটা বেঞ্চে বসে দেখি বিভিন্ন দেশ থেকে আসা মানুষজনের বিচিত্র চালচলন। সিটি সেন্টারটা তুলনামূলকভাবে খুব ছোটো। কারফ্যাঙ্ টাওয়ার ঘিরে বড় একটা চত্বর, কর্ণমার্কেট স্ট্রীট ও কুইন স্ট্রীটের একটা জাংশানের মধ্যে সীমিত। সিগারেট শেষ করে ব্ল্যাকওয়েলস বুকসপে ঢুকি, কোনো একটা কক্ষের ভেতর ইউরোপের সব চেয়ে বড় বইয়ের দোকান এটা, দশ হাজার বর্গফুট আয়তন। বইয়ের গন্ধে মন ভরে যায়। অনেক সময় দ্বিধায় পড়ে নিজেকে শুধাই, কোন গন্ধটা বেশি প্রিয় আমার, বই, না ফুলের? বই কিনি না, ঘুরে ঘুরে দেখি, পছন্দ করে রাখি, লাইব্রেরি থেকে নিয়ে পড়া যাবে সময় মতো।
দারুণ সবুজ এই অঙ্ফোর্ড শহরটা, অনেকগুলো পার্ক আছে এ শহরে। সিটি সেন্টার থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সাউথ পার্কে এসে বসি, এতো সুন্দর একটা পার্ক, অথচ হাতে-গোনা ক’জন মানুষ! ঢাকা শহরে নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য একটু খোলা জায়গা পাওয়া যায় না, অথচ এদের প্রতিটা পাড়ায় একটা পার্ক আছে। বড় একটা সবুজ চত্বর দেখে ফুলের মেলায় বসে পড়ি কোমল মখমলের মতো ঘাসের উপর। কথা বলার কেউ নেই, বাদাম চিবুতে পারি না, খুব কষ্ট পাই মনে মনে!
এ হপ্তাহান্তটা পুরোপুরি ভবঘুরে হয়ে কাটাবো ভাবছি। বইয়ের পাতা ওল্টাবো না, কারো সঙ্গে আড্ডা না, নো রান্নাবান্না, নো টাইডি-আপ। পার্কে বসে থেকে ঝিমুনি আসে। ঘুমিয়ে পড়ার মতো জায়গাই বটে। কোনো এক কালে বাংলাদেশের অনেক গ্রামে বটের ছায়ায় দড়ির খাটিয়া পেতে গ্রীষ্মের দুপুরে অলস সময় কাটাতে পারতো সাধারণ মানুষজন। এখন কারো কারো স্মৃতিতে হয়তো রয়ে গেছে সেসব। বট গাছের ইংরেজি নাম কেন বেনিয়ান ট্রী হয়েছিল বুঝতে পারি না, এখানে বেনিয়ান নামে কোনো গাছ নেই। এই বেনিয়ান শব্দটার অর্থই বা কি? আসলে বাংলার বটবৃক্ষতুল্য কোনো গাছই এদেশে নেই।
পতিতা ও পুলিশের আনাগোনা নেই এসব দেশের পার্কে, বুড়োবুড়িরা সময় কাটায় এখানে, তরুণতরুণীরা খুব একটা আসে না। ঘাস থেকে উঠে একটা বেঞ্চে শুয়ে পড়ি। ঢাকার রমনা পার্কের একটা স্মৃতি মনে পড়ে। ক্লাশ নাইনে পড়ার সময় অভিমান করে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলাম একবার, সঙ্গে ছিল আরেক বন্ধু। পালিয়ে তো এলাম ঢাকায়, কিন্তু কি করবো, কোথায় থাকবো কিছুই জানি না। কোনো পরিকল্পনা তো ছিল না। সারাদিন রমনা পার্কে কাটাই আর ভাবি। বাদাম আর ঝালমুড়ি কিনে খাই। মসজিদটা বানিয়ে পার্কের কান কাটে নি তখনো, নাহলে হয়তো মসজিদে যেয়ে ঘুমাতে পারতাম। নিরিবিলি একটা ঘুুপচি দেখে ঘুমিয়ে পড়ি পার্কের ভেতর। ঘুম যে কত গভীর হতে পারে এখন মনে পড়ে হাসি পায়। আজকালের মতো এতো কায়দা-কানুন আমাদের জানা ছিল না তখন। টাকা পয়সা লুকিয়ে রাখার গোপন জায়গার মধ্যে নিরাপদ ছিল প্যান্টের ফ্লাই। পকেটমারের জন্য তখনই বিখ্যাত ঢাকা শহর, খুচরো-টুচরো সব বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলাম। ভোরে ঘুম থেকে উঠে দু’বন্ধুর কেউই বুঝতে পারি না কোথায় আছি। পায়ের স্যান্ডেল তো নিয়ে গেছেই, গায়ের শার্ট কীভাবে খুলেছে ভেবেই পাই না। প্যান্টের ফ্লাইয়ের ভেতর থেকে রোল করা পাঁচ টাকার নোটটা বের করে নিয়ে গেছে একটুও টের পাই নি। দু’জনেরই প্রায় একই দশা। তখন ওরা বেশ রসিকও ছিল, পকেটে রুমাল রাখার প্রচলন ছিল সেসব দিনে, দু’জনের জন্য আট আনা পয়সা আমার রুমালে গিঁট দিয়ে বেঁধে রেখে গেছিল। ঐ অবস্থায় কীভাবে বাড়ি ফিরে আসি, মনে হলে এখনো আতঙ্কিত হই!
পার্কের একাকিত্ব্ব ছেড়ে আবার সিটি সেন্টারের জনসমাগমে আসি। একটা নাচের দল হুট করে আসে কোত্থেকে, চৌরাস্তার ক্রসিঙে ওদের দলনেতা দাঁড়িয়ে উঁচুগলায় দলের সদস্যদের পরিচয় দেয়, দশ মিনিটের একটা নাচ দেখাবে ওরা। অক্সফোর্ডশায়ারের বিখ্যাত লোকনৃত্য, ওটার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও দলের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করে। ওর কথা বলার ফাঁকে গোল করে ঘিরে দাঁড়িয়েছে দর্শক-শ্রোতা, আমিও মিশে যাই ওদের সঙ্গে। ড্রাম বাজতে শুরু করে, দর্শকেরাও পা দিয়ে তাল ঠোকে নাচের ছন্দে। আমাদের লাঠি খেলার মতো অনেকটা, তবে মেয়ে-নাচিয়েও আছে এদের দলে। সবার মুখ থেকে গলা পর্যন্ত সাদা ও কালো রঙে রং করা, পোশাকও সাদা ও কালো, লাল রঙের ক্রসবেল্ট পড়নে সবার। অসাধারণ একটা নাচ দেখালো, হাততালি দিয়ে ওদের অভিবাদন জানায় সবাই। অনেকে ছবি ওঠায় ওদের সঙ্গে। গ্রীষ্মের এ সময়টায় প্রতি হপ্তাহান্তেই নাচের অনুষ্ঠান করে ওরা। অঙ্ফোর্ডশায়ার কাউন্সিল থেকে অর্থায়ন করা হয় ওদের। ঐতিহ্য ধরে রাখার চমৎকার উদাহরণ।
পৃথিবীর অনেক দেশের খাবারের স্বাদ নেয়া যায় অক্সফোর্ডে বসে। ইটালিয়ান একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকি দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য, ‘লা ডোলচে ভিটা’, এ রেস্টুরেন্টের শাখা বিলেতের প্রায় সব বড় শহরে আছে।
চেরওয়েল ও আইসিস নদী দুটো অক্সফোর্ডের দুই ধমনি, অক্সফোর্ডশায়ারের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া টেমসের অংশটাকে ওরা আইসিস নামে ডাকে। শস্য ও প্রকৃতির দেবী আইসিস। অঙ্ফোর্ডশায়ারের প্রকৃতি সত্যিই অনন্য সুন্দর, এতো সবুজ, এতো শ্যামল, চোখ জুড়িয়ে যায়। টেমসের এই আইসিস অংশটার সঙ্গে লন্ডনের টেমসকে কোনোভাবে মিলানো যায় না। ঐতিহাসিকভাবে অঙ্ফোর্ড শহর বিখ্যাত টেমসের এ অংশের নদী বন্দরের জন্য। শহরের দুই প্রান্তে আইফলি ও ওসনি লক নির্মাণ করে নদীর নাব্যতা রক্ষা করা হয়েছে। অক্সফোর্ড ক্যানাল তৈরি করে বিলেতের মধ্যাঞ্চলের সঙ্গে এর সংযোগ দেয়া হয়েছে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এই সব নদী ও ক্যানালে চলাচলকারী অনেক প্রমোদতরী রয়েছে। তিন ঘণ্টার একটা রিভার ক্রুইজিংএ উঠি বিলেতের বিখ্যাত ‘সল্টার্স স্টীমার্স’এর একটা সুন্দর জাহাজে। অপূর্ব এই নৌ-ভ্রমণ মনে থাকবে আজীবন।
প্রকৃতির দেবী আইসিস অক্সফোর্ডশায়ারকে দিয়েছে অঢেল প্রাচুর্য। গমের ফলন হয় এখানে খুব ভালো, অনেকগুলো ব্রুয়ারি গড়ে ওঠেছে। বিখ্যাত মোরেলস ব্রুয়ারি দেখতে আসি রোববার সকালে। পারিবারিক এ ব্যবসাটা হাতবদল হয়ে শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয় পরের শতকে এসে।
অনেকটা পথ হেঁটে দশ ডিগ্রির কম কৌণিক ঢালের একটা পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে অনেক বড় একটা প্রায় সমতল পেয়ে যাই, উত্তল লেন্সের পিঠের মতো অনেকটা। এক বেচারা চাষা, এ শব্দটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হতদরিদ্র নিরক্ষর ভাঙ্গাচোরা মানুষের মুখ মনে পড়ে। এর বিপরীতে ট্রাক্টরের ড্রাইভিং সীটে বসা লালমুখ বিশাল এই মানুষটা মনের ভেতর ছোট্ট একটা আঁচড় কাটে। শিল্পী সুলতান ইউরোপে থাকার সময় পাহাড়ি জমিতে এমন কোনো চাষার হাল দেয়ার দৃশ্য দেখেছিলেন হয়তো, কল্পনায় আমাদের চাষীদেরও ওরকমভাবে এঁকেছেন। গগার নিসর্গের ছবির মধ্যে কৌণিক স্ট্রোকের একটা বিশেষত্ব যেমন নিশ্চিতভাবে বলে দেয় এগুলো গগার ছবি, তেমনি সুলতানের সার্কুলার স্ট্রোকের বিশেষত্ব বিশেষভাবে চিনিয়ে দেয় এগুলো সুলতানের। একজন শিল্পীর মেধার পাশাপাশি তার পৃষ্ঠপোষকতাও জরুরী। না ব্যক্তি, না সমাজ, না রাষ্ট্র, বাংলাদেশের কোনো শিল্পীর পৃষ্ঠপোষকতা করে। অথচ এসব ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের তুলনা নেই, এজন্যই এগিয়ে গেছে ওরা, আর আমরা ঐ তিমিরেই, এখনো মধ্যযুগীয় কীর্তন গাইছি। ছবি আঁকা পাপ বলে এক সময় প্রচার করেছে যারা, তারাই এখন নিজেদের মেহেদিরাঙানো কুৎসিত ছবি ফেরি করে দরিদ্র ও নিরক্ষর মানুষের কাছে।
রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে জমিটার শুরু সেখান থেকে, এক টুকরো ঘাসের আচ্ছাদন দেখে বসে পড়ি, বুঝতে পারি হেঁটে কেউ আসে না এখানে। এত বিশাল একটা জমি, কয়শ’ একর হবে কে জানে, একা একা চাষ করছে লোকটা। ফসল বুনবে একা, কাটবে একা, গোলা ঘরে তুলবে একা, শুধু একটা যন্ত্র সহায়, যন্ত্র তো নয় দানব, আমাদের কয়েকশ’ চাষীর প্রয়োজন এমন একটা প্রান্তর আবাদ করতে। অবশ্য এতো বড় শস্যক্ষেত আমাদের দেশে তো নেইই।
চাষীভাইয়ের বোধ হয় ব্রেকটাইম, ট্রাক্টরটা নিয়ে এদিকে আসে। ঘাসের এদিকটায় আরেকটু সরে বসি, আরো কিছু সময় কাটাতে ইচ্ছে হয়। রাস্তার মাথায় এসে থেমে যায়, কিছুটা অবাক হয় আমাকে দেখে।
হাই আ?
অ’রাই মী।
আ’ ইউ ওয়চিং মি? আমুদে চোখে তাকায় লোকটা।
ইয়া ইয়া, আ’এম ওয়াচিং ইউ। ইউ আ’ ডুয়িং ভেরি ফাইন।
দেন ইউ হ্যাভ টু অফার মি আ সিগারেট। বলে পকেট থেকে একটা সিগারেট নিজেই বের করে দেয়। বুঝতে পারি ভাগ্য আজ ভালো, মজার এক মানুষের সঙ্গ পেয়ে গেছি। ইংরেজরা সাধারণত মিশুক না, যদি কেউ মিশে, তাহলে আবার খোলাখুলি।
আমি ব্রেকে যাচ্ছি, ততক্ষণ ট্রাক্টরটা চালাবে নাকি?
হেসে উঠি আমি।
সাইকেলই চালাতে জানি না।
বলে কি! তোমাকে ইংল্যান্ডে ঢুকতে দিয়েছে কে?
দেয় নি কেউ, নিজেই ঢুকেছি।
বাহ্, তাহলে তো তুমি এক হিরো। এখানে একা বসে কি করবে। নিচে যাবে নাকি, বিয়ার টানতে পারবে এক পাইন্ট।
কেন, ভয়ে হচ্ছে, তোমার ট্রাক্টর নিয়ে পালাবো?
এই তো ধরে ফেলেছো, বেশ বুদ্ধিমানও বটে, কোন দেশের লোক হে তুমি?
চলো, নিচেই যাই, তোমাকে দুঃশ্চিন্তায় রেখে লাভ নেই, আর দেশ-টেশ ঘেঁটেও বিশেষ কিছু হবে না।
সাড়ে ছ’ফুট তো হবেই বেটা, বুকের ছাতি কম করে হলেও বাষট্টি, লম্বা বেশি হওয়ার কারণে এতো যে মোটা বোঝা যায় না তেমন, মধ্যযুগীয় কোনো নাইটের বংশধরের পোলাটোলা হবে হয়তো। রোদে পুড়ে চামড়া টকটকে লাল, গায়ের আসল রং বোঝা যায় চামড়ার ভাঁজে, মুখের বলিরেখায়। রোদে কাজ করে যারা, প্রায় সারাক্ষণ চোখ কুঁচকে থাকতে হয় বলে চোখের কোনায় গভীর ভাঁজ পড়ে। ভাঁজের ভেতর রোদ ঢুকতে না পারায় ধবধবে সাদা থাকে ওখানটা। সাধারণ আলোয় আসে যখন, মনে হয় চোখের দু’পাশে সাদা রঙের দাগ টানা। চোখের বলিরেখা বোঝা যায় স্পষ্ট।
নিচে নেমে দু’মিনিট হাঁটার পরই দেখি যেদিক থেকে এসেছি তার উল্টোদিকে সুন্দর একটা গ্রাম, রাস্তার ওদিক থেকে বোঝাই যায় নি, কোথায় লুকিয়ে ছিল এটা! ওর সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারি নদীর ওপারের কাউলিতে কাজ করে এখানের অনেকে। নদীর অপর তীরে গড়ে উঠেছে বিখ্যাত শিল্প এলাকা কাউলি। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত মোটরগাড়ি নির্মাতা কোম্পানি মোরিসের অবস্থান এখানে, অসংখ্য ভারি শিল্প কারখানা, প্রিন্টিং ও প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রি প্রভৃতি গড়ে ওঠে এখানে। স্পষ্ট দু’ভাগে ভাগ করা যায় অক্সফোর্ড শহরটাকে, চেরওয়েল নদীর উপর বানানো ম্যাগডালেন ব্রীজের পশ্চিমে বিশ্ববিদ্যালয় শহর, ও পুবে শিল্প শহর কাউলি। এখানের অধিবাসীরা কৌতুক করে বলে, কাউলির বাম তীর হচ্ছে অক্সফোর্ড। বাংলাদেশের রাস্তার রাজা ছিল এক সময় লেইল্যান্ড ট্রাক, বিখ্যাত এই লেইল্যান্ড কোম্পানির গাড়ি বানানো হয় এখানে, এক দিন ঘুরে ঘুরে দেখে এসেছিলাম কোম্পানিটা। লেইল্যান্ডের সঙ্গে বাংলাদেশে ছিল বেডফোর্ড ট্রাক, এখন ঐসব বিখ্যাত কোম্পানির জায়গা দখল করেছে ভারতের লক্কড়-ঝক্কড় সব কোম্পানি, পাঁচ ছয় বছর পর যেগুলোকে স্ক্র্যাপ করতে হয়, অথচ ঐসব লেইল্যান্ড অথবা বেডফোর্ড বিশ ত্রিশ বছর বেশ ভালোভাবে চালানো যেতো। জাপানি গাড়ির জোয়ারে লেইল্যান্ড কোম্পানিও একসময় বন্ধ হয়ে যায়। কাউলি শহরটাই প্রায় পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে।
এক পাইন্ট বিয়ারের সঙ্গে এক প্লেইট ফ্রাই ও মীট-বল-অন-সস নিয়ে বসি। ইংলিশ খাবার কোথায় যে স্বাদ আর কোথায় বিস্বাদ বুঝে উঠতে পারি নি এখনো। মীটবলগুলো এতো সুস্বাদু যে আবার খেতে ইচ্ছে করে।
খাবার দোকান থেকে বেরোনোর সময় ও বলে–
যাবে নাকি ট্রাক্টর চালাতে? আমার নাম নিকোল।
আমি ডেয়ুড। সত্যি বলছো?
চোখ কুঁচকে তাকায়। গোঁফ-জোড়া ওর দেখার মতো, দাঁতগুলো বিশ্রি, হলদে। অবশ্য এটাই এদের আসল রং।
নাহ্, জৌক করলাম, আজকের কাজ শেষ আমার। বাসায় যেয়ে শাওয়ার নেবো, তারপর বিশ্রাম।
ঠিক আছে, ভালো থেকো।
একটা সিগ্রেট এগিয়ে দেই, একগাল হেসে ধন্যবাদ জানায়।
সি ইউ, বাই।
বাআই।
ভালোভাবেই জানি জীবনে হয়তো আর কোনোদিনই দেখা হবে না ওর সঙ্গে। আজকের দিনটা কোনো এক রোববারের স্মৃতি হয়ে থেকে যাবে আমার সঙ্গে। নিকোলের হয়তো মনেই থাকবে না ডেয়ুড নামের কোনো মানুষের সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল। জীবন এমনই!
রাতে বাসায় ফিরে চুপচাপ শুয়ে থাকি বিছানায়, আর ভাবি এখানের সাধারণ মানুষগুলো তো আমাদের সাধারণ মানুষজনের চেয়ে বেশি চালাক-চতুর না, এদের ভেতর থেকে কীভাবে এতো ভালো নেতৃত্ব গড়ে ওঠে যে পুরো জাতিকে টেনে এতোদূর নিয়ে যেতে পারে! কীভাবে এতো ভালো থাকে এরা আর আমরা এতো অধোপাতে! ভাবনাটা ঝেড়ে ফেলি মাথা থেকে, আমি তো আর রাজনীতি করতে যাচ্ছি না।
অক্সফোর্ড শহরই নয় শুধু, পুরো অক্সফোর্ডশায়ার কাউন্টিটাই আমার হৃদয়ে গেঁথে রয়েছে। এর গ্রামগুলো অসাধারণ সুন্দর, ইংল্যান্ডের সৌন্দর্য বোঝাতে এর গ্রামগুলোই বোঝায়, এতো সুন্দর সাজানো-গোছানো গ্রাম পৃথিবীর খুব কম দেশেই আছে। গ্রামগুলো বলতে বিচ্ছিন্নভাবে থাকা গ্রামের সমষ্টি বোঝায়। প্রতিটা গ্রাম পৃথক, কোনোটার গায়ে কোনোটা লেগে নেই। উঁচু জায়গা থেকে, অথবা কিছুটা দূরে থেকে পুরো একটা গ্রাম বিচ্ছিন্নভাবে চোখে পড়ে। বাংলাদেশের কোনো গ্রাম অন্য গ্রাম থেকে পৃথক করা যায় না, হাজার হাজার গ্রাম মিশে রয়েছে এক সঙ্গে, বড় একটা গ্রামের মতো। অসংখ্য নদী ও খাল বিল যদি না থাকতো, তাহলে পুরো বাংলাদেশটাকেই বড় একটা গ্রাম বা বস্তি বলা যেতো। বাংলাদেশে কোনো একটা গ্রামের ছবি কখনোই দৃষ্টির ভেতর ধরা যায় না, গ্রামের ভেতরে থেকে না, বাইরে থেকেও না। বড় কোনো বিল বা হাওরের মাঝখান থেকেও গ্রামগুলোকে চেনা যায় না। চারদিকে দেখা যায় সবুজ গাছপালার বিস্তার, কোথাও বিচ্ছিন্নতা নেই। ঐসব গাছপালার ফাঁকে ঘরবাড়িও চোখে পড়ে না। আগে কিছুকিছু মঠ ও মন্দিরের চূড়া দেখা যেতো দূরে থেকে, ওসব দেখে বোঝা যেতো কোনো লোকালয়ের অবস্থান, এখন সেগুলোও সব ভেঙ্গে ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেলা হয়েছে।
সৌন্দর্যপিপাসু মানুষেরা দেশে দেশে আর্টগ্যালারি, মিউজিয়াম, থিয়েটার হল এসব ঘুরে বেড়ায়। মহাজনদের অনুসরণ করে আমিও যাই, কিন্তু সব চেয়ে বেশি ভালো লাগে আমার নদী। আইসিস ও চেরওয়ালের তীরে ঘণ্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেই। নদী দুটোর নৈসর্গিক দৃশ্য চোখ জুড়িয়ে দেয়, পুরোপুরি মন ভরিয়ে দেয়, খুব ইচ্ছে নদীতে নেমে সাঁতার কাটি, কিন্তু এখানে এটা হবার নয়। বাংলাদেশের নদীগুলোর কাকচক্ষু জলে সাঁতার কাটায় কী যে আনন্দ, স্রোতের ভেতর গা ভাসিয়ে ভাটিতে নেমে যাওয়া, আবার স্রোতের বিপরীতে উজানে সাঁতরে আসা, মনে হলে শিহরণ জাগে। সব চেয়ে মজা হতো, শীতকালে পানিতে নামার আগের মানসিক প্রস্তুতি ও আয়োজন, পানিতে নামার পর এতো ঠাণ্ডা লাগতো না, পানির উপরের স্তরের এক দু’হাত নিচেই ছিল গরম পানি। স্পষ্ট বোঝা যেতো দু’স্তরের তাপমাত্রার পার্থক্য, অনেকক্ষণ ডুব দিয়ে থাকলে অন্যরকম এক আনন্দ পাওয়া যেতো। সকালের দিকে নদীর উপর থেকে সাদা ধোঁয়ার মত বাষ্প উঠতো, নদীর তীরে খুঁটিতে বাঁধা রশিতে এক থোকা ডালপালার ভেতর ঘাপটি মেরে থাকা চিংড়ি মাছ ধরার এটাই ছিল ভালো সময়। মাছ ধরার উত্তেজনায় ঠাণ্ডা যেনো লাগতোই না, সাবধানে পানিতে নেমে ঝটিতি টানে পুরো ডালপালার ঝাড়টাকে ডাঙ্গায় উঠানোর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যেতো চিংড়িদের লাফানো, দু’একটা সাপও নেমে যেতো দৌড়ে। বড় চিংড়িগুলো রেখে ছোটোগুলো আবার পানি ছিটিয়ে নদীতে ছেড়ে দেয়া, চমৎকার একটা স্পোর্টসের আনন্দ পাওয়া যেতো।
মাঝে মাঝে দেখা যায় নৌকো থেকে আইসিস অথবা চেরওয়েলে বড়শি ফেলে বসে কেউ কেউ আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মাছ ওঠাতে ওদের দেখতে পাওয়া ভাগ্যের ব্যপার। হাউসবোটে বাস করে অনেকে, দু’চারটা ধনী পরিবার সখ করে কাটায় কিছুদিন, অনেকে আবার ভবঘুরে, কাউন্সিল ট্যাঙ্ নেই, ঘরভাড়া দিতে হয় না, নৌকোর ও নিজেদের পেটের জ্বালানি কোনোভাবে সংগ্রহ করতে পারলেই হয়। মনের ভেতর একটা আশা রয়েছে বাংলাদেশে একটা হাউসবোট বানিয়ে নদীগুলোয় ভেসে বেড়াবো কয়েক বছর। নিরাপত্তার কথা ভেবে পিছিয়ে যেতে হয়।
সেদিনের ট্রাক্টর চালানো দেখার পর নিকোলের সঙ্গে দেখা হয়েছে আরো অনেকবার, আশাই করতে পারি নি! এক ধরনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে ওর সাথে। নিয়মভঙ্গ করে, ইংরেজরা সাধারণত যা করে না, ট্রাক্টর চালানো শিখিয়েছে আমাকে। রক্তে আমার চাষারু জিন, আমার ভালো লাগে চাষবাস, অথচ পড়তে হচ্ছে রেডিওলোজি নিয়ে পিএইচডি! খুব ইচ্ছে, ইংল্যান্ডে একটা খামার কিনে চাষা হই। নিকোলরা দু’ভাই, গ্রীষ্মকালটা চাষাবাদ করে নিকোল, ফসল উঠিয়ে গোলা ভরে ছোটো ভাইয়ের হাতে চাবিটা দিয়ে পাড়ি দেয় অস্ট্রেলিয়া। প্রায় পুরো শীতকাল কাটায় ওখানে, অস্ট্রেলিয়ায় তখন গ্রীষ্ম। সেকেন্ড হোম ধারণাটা ওর কাছ থেকে ধার করি। অস্ট্রেলিয়া নাকি ওর সেকেন্ড হোম, স্ত্রী ও দু’কন্যা থাকে ওখানে। অস্ট্রেলিয়ার শীতের ছুটিতে ইংল্যান্ডের গ্রীষ্ম কাটায় ওরা, ভৌগোলিক এ সুবিধেটা কীভাবে উপভোগ করে ভেবে চমৎকৃত হই। মনের ভেতর সেকেন্ড হোম ধারণাটা জেঁকে বসায় এমন একটা খামারের স্বপ্ন দেখি। পিএইচডি শেষ করার পর হয়তো কোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করতে ও ছাত্র পড়াতে হবে, বইয়ের পাতায় চোখ রেখে জীবন কাটানো, ভাবতে ভালো লাগে না, মাঝে মাঝে মনে হয়, ভুল একটা জীবনের দিকে এগিয়ে চলেছি নাকি?
গ্রামের কৃষকদের ছবি যখন স্মৃতিতে ভেসে ওঠে, শিহরিত হই প্রচণ্ড শীতের রাতে শেষ প্রহরে উঠে হুক্কা টানতে টানতে দিনের প্রস্তুতি নেয়। খালি পায়ে, শরীরে একটা পাতলা কাঁথা জড়িয়ে হাল নিয়ে বেরিয়ে যায়। জমিতে লাঙল চালাতে যেয়ে শীতের মধ্যেও ঘেমে ভিজে ঐ কাঁথাটাও জমির আলে রেখে দেয়। বাইরে থেকে যেমনই লাগুক, ভিতর থেকে দেখলে বোঝা যায় কত কষ্টের ঐ জীবন। এখানেও হয়তো প্রকৃত চাষাবাদের কাজ শুরু করার পর বোঝা যাবে বিষয়টা আসলে কেমন। কল্পনায় তো অনেক কিছুই করা যায়, রক ক্লাইম্বিং বা তুষারাবৃত পর্বতারোহণ, স্কাই ডাইভিং, অথবা স্টান্টম্যানের দুঃসাহসী কোনো কাজের ফুটেজ টিভি পর্দায় দেখে শিহরণ পাওয়া যায়, নিজে কখনো ওটার ভেতর প্রবেশ করলে বোঝা যায় শিহরণটা কোথায়, আর কাজটা কত পরিশ্রমসাপেক্ষ।
চাষবাসের জন্য না হলেও সেকেন্ড হোম হিসেবে আমার মনের গভীরে প্রবেশ করে ইংল্যান্ড।
অচিরেই বুঝে যাই যে নিকোলের খামারটার মতো একটা খামার কোনো দিনই হবে না আমার, এমন একটা স্বপ্ন মনের ভেতর ধরে রাখাও অর্থহীন। এটার প্রভাব কাটাতে যেয়ে নিকোলের সঙ্গে বন্ধুত্বটাই বরং গাঢ় হয়ে ওঠে। যে-কোনো অবসরের দিন ওর সঙ্গে কাটাতে পারি বলে জানায় সে। খুব বেশি বন্ধুবান্ধব নেই নিকোলের, ফলে প্রায় প্রতি হপ্তাহান্তে সঙ্গ পাওয়া যায় ওর। এখানের চাষাবাদ ও ফসল সম্পর্কে অনেক কিছু জানায় সে। অনেক গাছপালা, বুনো ফুল ও ফলের নাম জেনে নেই। নিকোল বলে, প্রকৃতিকে ভালোবাসতে হবে তোমাকে, নাহলে কখনোই চাষী হতে পারবে না। অনেক কিছু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসে এখন প্রায় এদেশেরই হয়ে গেছে। ওদের প্রধান খাবার যে আলু, ওটাই এসেছে আমেরিকা থেকে। একদিন জিজ্ঞেস করি ওকে, তাহলে নিজের কি ছিল তোমাদের? হেসে বলে, তোমাদেরই বা কি ছিল? পৃথিবীর সবকিছু ভাগাভাগি করে নিয়েছি আমরা, তোমাদের ওখানেও অনেক গাছপালা, প্রাণী, এসবের অনেক কিছু বাইরে থেকে গেছে। চা না-হলে যে এক বেলাও চলে না তোমার, ঐ গাছটা কোথা থেকে গেছে বল তো? ইংল্যান্ডকে এক সময় বলা হতো কান্ট্রি অব মিল্ক এন্ড হানি। আমাদের পশুপালন ছিল খুব উন্নত, অনেক মাছ ছিল উত্তর সাগরে, আটলান্টিক উপকূলে, উন্নত জাতের সরিষার ফলন হতো প্রচুর, যেখানে মৌমাছির আবাস ছিল, অঢেল মধু উৎপাদিত হতো। আপেল, প্লাম, স্ট্রবেরি থেকে শুরু করে অনেক ফলমূল প্রচুর পরিমাণে জন্মাতো। রোমানরা তো এমনিতেই বারবার আক্রমণ চালায়নি এ-দেশটায়। সারা পৃথিবী থেকে এখনো হাজার হাজার মানুষ এখানে আসছে, কেন বল তো?
ওর কথায় যুক্তি আছে নিশ্চয়।
নিকোলের সঙ্গে সময় কাটিয়ে একজন প্রকৃত ইংরেজ কৃষকের সঙ্গে কথা বলার আনন্দ পেয়েছি। ওর বিশাল দেহ, থুতনি পর্যন্ত নামানো গোঁফ, আর একটু নামলে খসে পড়ে যাবে এমন এক ভাব, কিছুটা বেরিয়ে থাকা নীল চোখ, ও প্রাণখোলা হাসি আমাকে আকৃষ্ট করেছে ওর প্রতি। ওর বাড়িতে নিয়ে গেছে আমাকে অনেক দিন। গ্রামের এসব বাড়িঘর দেখে বোঝা যায় ওদের পূর্বপুরুষদের মেধা ও পরিশ্রমের সমন্বয় কীভাবে ঘটেছিল। ওরা যে বলে ‘ঈগেলেটেরিয়ান সমাজ’, সেটা কীভাবে বিকশিত হয়েছিল বুঝতে পারি কিছুটা। একই গ্রামে বিশাল এক সাতমহলা জমিদারবাড়ি ঘিরে শত শত দরিদ্রবস্তি গড়ে ওঠে নি। গ্রামের প্রায় সব ঘরবাড়ি একই রকম। কাঠ ও পাথরে তৈরি, এসবের নির্মাণও অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করতে হয়েছিল, কোনো কোনো বাড়ি গ্রামের সমান বয়সের, পাঁচ ছয়শ’ বছর আগে এসব জনপদ গড়ে ওঠে। পাথর গেঁথে, কাঠের কড়িবর্গা বসিয়ে বেশ বড় আকারের দ্বিতল এসব বাড়িগুলোর ভেতর অদ্ভুত এক প্রাচীনত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটা বাড়িতে ঘোড়ার জন্য আস্তাবল, গোলাঘর, খোঁয়াড় প্রভৃতি রয়েছে। অনেক গ্রামে এখনো কয়েকশ’ বছর আগে বানানো হাওয়াকল রেখে দিয়েছে স্মৃতি হিসেবে। বাড়ির সামনে ও পেছনে ফুলের বাগান, খোলা জায়গা, আপেল ও অন্যান্য ফলমূলের গাছ, সবুজ চত্বর, সবই রয়েছে। কোনো কোনো বাড়িতে কৃত্রিম ঝরনা ও নালা আছে, সেখানে ছোটো ছোটো কয়েক প্রজাতির মাছ ও ব্যাঙ রয়েছে। বেশির ভাগ বাড়ির ছাদে টালি-বসানো, দু’একটা বাড়ির ছাদ দেখা যায় এক ধরনের শনে ছাওয়া, এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ আজকাল খুব ব্যয়সাপেক্ষ, রক্ষণশীল ও বিত্তশালী কোনো পরিবার ঐতিহ্য হিসেবে এখনো রেখে দিয়েছে ওরকম দু’একটা ছাদ। খুব ধনবান মানুষদের বাড়ি থাকে গ্রামের বাইরে, মধ্য-যুগের নাইটদের এবি, অথবা ছোটোখাটো সামন্তদের একটা বাড়ি ও আশেপাশের জায়গা মিলিয়ে বাংলাদেশের কয়েকটা বড় গ্রামের সমান। ওগুলোর বেশির ভাগই এখন ন্যাশনাল হ্যারিট্যাজ। যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, এবং দর্শনীর বিনিময়ে ওসব দেখা যায়। পুরোনো দিনের এসব নাইটরা বাংলাদেশের জমিদারদের মতো অত্যাচারী ছিল না। বরং গ্রামগুলোর রক্ষাকর্তা হিসেবে কাজ করতো এবং সবার সুখদুঃখের ভাগী হতো। নিজেদের বাহিনীর জন্য সৈন্য সংগ্রহ করতো এসব গ্রাম থেকে। এরাই রাজার বাহিনী হয়ে যুদ্ধে যেতো। ওদের মধ্যে ব্যতিক্রম যে ছিল না, তাও না, বাংলাদেশের এক-দু’জন প্রজাদরদী জমিদারের মতো বিপরীত স্রোতে ছিল ওদের অবস্থান। সে-সবের বিরুদ্ধেও রবিনহুডের মতো দল গড়ে উঠতো।
ইংল্যান্ডের গ্রামীণ এই জনপদের ভেতর, নিকোলের মতো মানুষের মাঝে এদেশের প্রকৃত সংস্কৃতির সন্ধান পাই। অথচ নটরড্যাম কলেজে পড়াকালীন সময়ে যে ইংরেজদের সঙ্গে সামান্য মেশার সুযোগ হয়েছিল ওদের অতি-ফর্মাল আচরণ যে কত বেশি কৃত্রিম ছিল, এখন বুঝতে পারি। ওসব মেকি আচরণের স্মৃতি ধরে কল্পনায় বিভ্রান্ত হয়েছি ওদের নিয়ে। এখন বুঝি আমাদের কবির ঐ বাণী, ‘নানা রঙের গাভীরে ভাই একই রঙের দুধ, সারা জগৎ ভ্রমিয়া দেখি সব একই মায়ের পুত!’
৩
অসংখ্য রাত কাটিয়েছি এমন এক প্রত্যুষের স্বপ্ন নিয়ে যা হয়তো মানুষের জীবনে কখনো আসেই না! ঘুম ভাঙতেই বুঝতে পারি একটা ভুল স্বপ্নের জগতে ছিলাম, এমনকি ঘুমিয়েও ছিলাম ভুল জায়গায়। বিছানা, বালিশ, পরিবেশ সবই অন্য, তাড়াতাড়ি উঠে বসতে যেয়ে দেখি পুরো শরীর উদোম, এভাবে তো কখনো ঘুমাই না আমি! সারা শরীরে ব্যথা, মাথা তুলে রাখতে পারি না, প্রচণ্ড হ্যাঙওভার হয়েছে, আবার শুয়ে পড়ি, একটু একটু করে গত সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে। কাত হয়ে শুই, দেখি পাশের টেবিলে ভাঁজ করে রাখা আমার কাপড়-চোপড়, একটা দুবে দু’ভাঁজ করে মেঝেতে বিছিয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে এলিনা, গায়ের দুবেটা কোমর পর্যন্ত নামানো, পাতলা একটা শেমিজ গায়ে, ভেতরে কোনো অন্তর্বাস নেই, মহাবিপজ্জনক এক দৃশ্য! এভাবে এখানে আমাকে টেনে আনার অর্থ কি! ফাঁদে পড়া একটা ইঁদুরের মতো মনে হয় নিজেকে, নিঃশব্দে উঠে পোশাক পরে নেই, টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন খুব, মনে হয় ওটা এড়িয়ে যাওয়া ভালো, ওর ঘুম ভাঙার আগেই বেরিয়ে যেতে চাই, আস্তে আস্তে দরোজা খুলে বেরিয়ে আসি, মুক্ত বাতাসে এসে বুঝতে চেষ্টা করি, কি ঘটেছে!
লাইব্রেরি-ওয়ার্কস করছিলাম বিকেলে, এলিনা এসে হাজির–
একটু সাহায্য করতে পারবে দাউদ? ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে বোঝাতে চাই এটা লাইব্রেরি। এবার ফিসফিসিয়ে বলে–
প্লীজ দাউদ, একটু সাহায্য করো, আমার এসাইনমেন্ট শেষ করতে পারছি না।
আমারটাই শেষ হয় নি এখনো।
তোমারটা শেষ করেই না হয়, প্লীজ দাউদ, ইউ আর এ জেন্টলম্যান।
কি করবো বুঝতে পারি না। ওভারকোট খুলে চেয়ারের গায়ে পরিয়ে দেয়। বসে পড়ে সামনের চেয়ারে। কাজে মন দেয়ার চেষ্টা করি। একটু পরে হ্যান্ডব্যাগ খুলে আয়না বের করে ঠোঁটের লিপস্টিক ঠিক করে, এভাবে ঠোঁট চাপে ও বাঁকায়, স্নায়ু বিকল করে দেয়ার অবস্থা, পড়াশোনায় মন দেই কি করে, শার্টের বোতাম দুটো খোলা রাখায় সূর্য উঁকি দেয়। বুঝতে পারি এসাইনমেন্ট এখন অসম্ভব। ওকে আগে বিদায় দেয়ার কথা ভাবি, বলি–
ঠিক আছে, তোমার এসাইনমেন্ট বের করো, বলো কি সমস্যা।
তোমারটা শেষ?
না।
তোমারটা শেষ করো আগে। অসুবিধা নেই, আমি বসতে পারবো।
এখানে বসে থাকলে আমার কনসেন্ট্রেশান অন্য দিকে ঘুরে যায়।
কোন দিকে?
তুমি কিন্তু প্ররোচিত করছো আমাকে এলিনা!
কী যে বলো, এতো শীতল রক্ত তোমার।
হজম করে যাই খোঁচাটা, জড়াতে চাই না ওর সঙ্গে, কোনোভাবে।
রোমান দেবীর মতো অসাধারণ সুন্দরী এলিনা, ভাবতেই পারি না কেন আমার দিকে ঝুঁকেছে সে! রেডিওলোজি নিয়ে এক সঙ্গে পড়াশোনা করি, বেশ কিছু ক্লাশ রয়েছে কমন, গ্রুপ-ওয়ার্কসও করতে হয় প্রায়ই, ক্লাশমেইটের চেয়ে বেশি আকর্ষণ কখনো অনুভব করি নি, হয়তো এক ধরনের ভীতিও কাজ করে, কেন জানি না পাকিদেরকে ভয়ও করে, ঘৃণা থেকে কিনা বুঝতে পারি না। দূরত্ব বজায় রেখে চলতে চেষ্টা করেছি, অথচ ঘনিষ্ট হওয়ার জন্য উদ্বাহু এগিয়ে এসেছে সে। হয়তো কখনো যাচ্ছি ক্লাশের দিকে, পিছন থেকে পিঠে বুক ঠেকিয়ে কাঁধে হাত রেখে হেঁটে এসেছে এক সঙ্গে কথা বলতে বলতে। প্রায়ই এক সঙ্গে খেতে আসে কেন্টিনে, কোনো কোনো দিন বাইরে খাওয়ার আহ্বান জানায়, যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলি ভদ্রতা বজায় রেখে, অনেক সময় না যেয়ে পারি না, যে-কারণে, আমাকেও ফেরত-আমন্ত্রণ জানাতে হয় মাঝে মাঝে। বুঝতে পারি, প্রবলভাবে চাইছে সে আমাকে, কিন্তু এগোতে পারি না কোনোভাবে। নিজেই অবাক হই কখনো কখনো, এমন অসাধারণ এক রূপসীর আমন্ত্রণ এড়িয়ে চলেছি কীভাবে? ওর সঙ্গে পরিচয় ইউনিভার্সিটির ইন্ডাকশানের দিন, একই দেশের দু’অংশের নাগরিক হিসাবে সাধারণ সৌজন্য বিনিময় হয়েছে। ওদের জাতীয় রক্ষণশীলতার জন্যই হয়তো খুব বেশি ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে মেলামেশা ছিল না ওর, করিডোরে বা অন্য কোথাও দেখলে এগিয়ে আসতো। ক্লাশের ফাঁকে কখনো কেন্টিনে গেলে সামনাসামনি এসে বসতো, এড়িয়ে যাওয়ার কোনো কারণ ছিল না আমার, ক্লাশমেইট হিসাবে কথাবার্তা চালিয়ে যেতাম। ধীরে ধীরে যেনো এক ধরনের নির্ভরতা খুঁজে পায় আমার ভেতর। ভাবে, ওর অনেক কিছু শেয়ার করা যায় আমার সঙ্গে, অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার অনেকটা, ক্লাশের অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গেও ওর তেমন ভাব ছিল না, অমিশুকই বলা যায় ওকে।
ওদের গ্রাম ও পরিবারের কথা এতোভাবে বলেছে যে ওসবের একটা চিত্র এরি মধ্যে আমার মনে তৈরি হয়ে গেছে। ইসলামাবাদের খুব কাছে এক পাহাড়ের চূড়ায় ওদের গ্রাম চাকলান। ওটাকে নাকি মনে হয় পৃথিবীর শেষ গ্রাম, যেখানে শেষ হয়েছে ওটা, সেখান থেকে খাড়া ঢাল এতো নেমে গেছে যে নিচে কিছুই দেখা যায় না, অনেক দূর দিগন্ত ছাড়িয়ে শুধু পাহাড়ের পর পাহাড়, সবুজের চিহ্ন মাত্র নেই, অথচ ওদের গ্রামটা চিরসবুজ, হাজার হাজার বছর আগে কোনো ভূকম্পনের ফলে হয়তো ওদিকটা দেবে নিচে নেমে গেছে, বৃষ্টিপাত তেমন না হওয়ায় ও প্রকৃতি পাথুরে থাকায় গাছপালা আর জন্মাতে পারে নি। গ্রামের পাশেই একটা প্রাকৃতিক ঝরনা থাকায় পানির অভাব হয় না তেমন, ফসল ফলানো ও ফলের বাগান গড়ে তোলা যায়। গ্রামটার প্রতিরক্ষা খুব দৃঢ়, তিন দিকেই এরকম খাড়া ঢাল থাকায় শুধু মাত্র সামনের দিক দিয়ে শত্রু আক্রমণ করতে পারে। আমি বলি– এটা বিপদজ্জনকও বটে। কোনো কারণে পালাতে হলে, পথ নেই। ও বলে– পালানোর কথা কখনো ভাবি না আমরা। জানজুয়া পরিবারের নাম শুনেছো নিশ্চয়। পুরো গ্রামটাই জানজুয়াদের, দেশের সেনাবাহিনীতে প্রথম সারির অনেক কর্মকর্তা আছে আমাদের গ্রামের। প্রায় সব পরিবারেই সৈনিক পেশায় রয়েছে কেউ না কেউ, শারীরিকভাবে দুর্বল অথবা অন্য কোনো কারণে যারা সেনাবাহিনীতে যেতে পারে না, ওরা চাষবাস করে। আমাদের পরিবারের অধিকাংশ পুরুষ সদস্যই সৈনিক।
ভালোই তো, তোমাদের পরিবারের লোকজন জানে কীভাবে নরহত্যা করতে হয়, লুটতরাজ করতে হয়।
ওভাবে দেখা ঠিক না, সামরিক বাহিনীর প্রধান কাজ দেশ রক্ষা, নিজেদের রক্ষা করা।
অবশ্যই, সব দেশের সেনাবাহিনী একই কাজ করে, কেউই আক্রমণ করে না। কিছু মনে করো না, ছোট্ট কৌতুক একটা।
এবার হোয়াইট ক্রিসমাস এসেছে বিলেতে, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ, রেসিডেন্সের প্রায় সবাই গেছে ছুটি কাটাতে। অনেক দিন থেকে এলিনাদের বসবাস এই অক্সফোর্ড শহরে, ওর দাদা এদেশে এসেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, ফিরে যায় নি আর। ওদের পরিবারের মালিকানায় কর্ণার-সপ আছে কয়েকটা, বেশ ভালোই চলে ব্যবসা। দু’বোন ওরা, ছোট বোন চিনতির স্কুল ছুটি থাকায় বাবা-মায়ের সঙ্গে দেশে গেছে। ক্রিসমাস-ইভে পুরো অক্সফোর্ড উৎসবমুখর, ঘরে বসে আছি একা একা, ক্রিসমাস পার্টির নিমন্ত্রণ ছিল অনেক ক’টা, সবগুলোই এড়িয়ে গেছি এ বছর, কেন জানি না। স্পেইনিশ পেড্রো ডোমেকের বোতল খুলে টিভির সামনে বসেছি। দরোজায় কড়ানাড়া, একটু অবাক হই, দরোজা খুলে পুরোপুরি তাজ্জব! বাইরে তখনো অবিরাম তুষার ঝরছে, প্রায় হাঁটু পর্যন্ত বরফে ঢাকা রাস্তাঘাট, সব কিছু সাদা, পুরোপুরি সাদা। সামনে দাঁড়িয়ে এলিনা, গায়ে জড়ানো টুকটুকে লাল জ্যাকেট। বাইরের ঠাণ্ডায় শাব্দিক অর্থেই বরফের মতো সাদা ওর মুখ, ঠোঁট দুটো শুধু জ্যাকেটের মতো উজ্জ্বল লাল, প্রায়-বোকা অন্তরঙ্গ এক হাসি মিশে আছে সেখানে। যেন, আরে, কী করে ফেললাম এটা! বাতাসের ধাক্কায় কিছু তুষারও ঢুকে পড়ে ঘরের ভেতর, তাড়াতাড়ি ওকে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেই।
ভাবতেই পারি না এলিনা।
আমিও পারি নি এক মুহূর্ত আগে। চলে যাবো?
না, এসেছো যখন, আর যাবে কেন, বসো।
ওভারকোটটা খুলতে সাহায্য করি, বৃটিশ এ ভদ্রতাটা এরি মধ্যে শিখে নিয়েছি, তুষার ঝেড়ে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে রাখি, নিঃসন্দেহে কোনো দামি সৌরভ ব্যবহার করেছে, পুরো করিডোরে ফুলের হালকা সুগন্ধি ভেসে বেড়ায়, চট করে গুছিয়ে নেই অগোছালো জিনিসপত্র, এয়ারফ্রেশনার ছড়িয়ে দেই। এসব করি আমার আপাত নার্ভাসনেস কাটাতে। ও বুঝতে পেরেছে কিনা বুঝি না।
অস্থির হচ্ছো কেন, সবই তো ঠিক আছে। আমি নিশ্চয় আশা করি না যে খুব গোছানো কোথাও এসে পড়েছি।
তা না, তুমি তো অতিথি, অবশ্যই।
ওভাবে দেখার দরকার নেই।
ঠিক আছে, বলো কি খাবে, চা কফি, অথবা জু্যস ড্রিঙ্কস?
বসি একটু, ভেবে দেখি?
ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই।
একটা কমেডি সিরিয়াল চলছে টিভিতে, ওটার হাসিতে মনে হয় ঘরের ভেতর অনেক মানুষ একসঙ্গে হাসছে, চ্যানেল পাল্টাতে থাকি, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে এসে থেমে যাই, বলিভিয়ার একটা গ্রামের ছবি, পুরো আমেরিকায় এই একটা দেশ যেখানে জনসংখ্যার বেশির ভাগ এখনো রেড ইন্ডিয়ান! পাশ্চাত্যের ক্যামেরা সাধারণত যা দেখায়, ওদের অনুন্নয়ন বা দারিদ্র, কুঁড়েঘর, হালকা পোশাকের মানুষজন, আদুল গায়ে খেলাধুলায় মেতে থাকা শিশুরা, ওদের কথিত উন্নয়ন যেখানে দাঁত ফোটাতে পারে নি, আকাশচুম্বী শেয়াল-চোখ ভবন নেই, শপিংমল, ফার্স্টফুড নেই, চওড়া রাস্তা আর ঝকঝকে গাড়ি নেই, আছে এখনো নির্মল প্রকৃতি।
ঘরের পেছন দিকের জানালার পর্দা সরিয়ে ছড়িয়ে যেতে দেই দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা। বাইরে, স্ট্রিটলাইটের আলোর গোল বৃত্ত জুড়ে ঝরে পড়া তুষার দারুণ সুন্দর দেখায়, গাছপালায় কোনো পাতা না থাকায় শহরের অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়, অসংখ্য জোনাকির মতো ছোটো ছোটো আলোর বৃত্ত ঘিরে থাকা তুষারের শত শত ফুল ফুটে রয়েছে, এমন নিবিড় নির্জন রাত শ্রাবণের বর্ষারাতের মতো অন্তর আকুল করে দেয়।
উঠে এসে এলিনাও দেখে তুষারপাত। জিজ্ঞেস করি–
গাড়ি পার্ক করেছো কোথায়?
কাছেই ফাঁকা জায়গা পেয়েছি, ভাগ্য ভালো।
যেভাবে তুষার পড়ছে, গাড়ি বের করতে পারবে তো আবার?
তাই তো।
মনে হয় প্রকৃত অর্থেই হোয়াইট ক্রিসমাস।
হ্যাঁ, রেইনডিয়ার নিয়ে শান্তা আসছে তোমার কাছে।
আমি খ্রিস্টান নই।
আমিও না। তাতে কি, খ্রিস্টানদের দেশে বাস তো করছি। ওদের প্রথাই তো চলবে এখানে।
এভাবেই দেখো?
কেন নয়!
আমি ভেবেছি অনেকটা কট্টর তোমরা।
হ্যাঁ, কট্টর আমার পরিবার, দেশের মানুষ, কিন্তু এখন তো আমি অন্য কোথাও।
তুমি অবশ্যই ঠিক। বলো এখন কি খাবে?
না, বরং যাই।
যাবে?
হ্যাঁ, সত্যিই জানি না কেন এসেছিলাম, অন্য কিছু ভেবো না দয়া করে।
না না, ভাববো না। বসো তুমি। মনে হয় একাকিত্বের চাপ এসে পড়েছিল তোমার উপর। বলো, কি ড্রিঙ্কস দেবো?
তুমি তো এলকোহোল নিচ্ছো।
সে জন্যই তো জিজ্ঞেস করছি, ওটা তোমার চলবে না।
চেখে দেখতে দোষ কি?
ওটা নিষিদ্ধ তোমার জন্য।
নিষিদ্ধ তো অনেক কিছুই, এই যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি, এটাও তো নিষিদ্ধ। ভাবতে পারো আমার পরিবারের কেউ জানতে পারলে পরিণতি কি হবে আমার?
হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, খুব বড় ঝুঁকি নিয়েছো।
এবং আমি জানি, কোনো কারণ ছাড়াই এটা করেছি।
হয়তো অবচেতন মনের এক ধরনের বিদ্রোহ তোমার।
হতেই পারে।
সত্যিই কি এলকোহোলিক ড্রিঙ্কস নেবে?
নিতে পারি একটু। শেকল যখন কেটেছি, খোলা আকাশে একটু পাখা মেলতে দোষ কি?
দু’মিনিট সময় দাও, প্লীজ।
চট করে শীতের পুরু পোশাক প’রে বেরিয়ে আসি। তুষার ঝরা বন্ধ হয়েছে আপাতত, হয়তো কিছুক্ষণের জন্য। এত কনকনে ঠাণ্ডা এখন বোঝা যায় না, চারদিক একেবারে সাদা, গোড়ালি পর্যন্ত পা দেবে যায় রাস্তায় জমে থাকা তুষারে, এরকম তুষারে পা পিছলানোর ভয় নেই তেমন। ক্রিসমাস ইভে আনন্দমুখর পুরো দেশ, প্রতিটা ঘরে আলো জ্বলে, অনেকে যায় গির্জায়, বিশেষ করে একটু বয়স্করা, তরুণতরুণীরা প্রায় সবাই পাবে ও বিভিন্ন পার্টিতে। নগরীকে এক অসাধারণ রূপ দিয়েছে ক্রিসমাসের বর্ণাঢ্য আলোকসজ্জা, ঐসব আলোর প্রতিফলন বরফের উপর অবর্ণনীয় সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। হাঁটতে হাঁটতে এসব দেখি মুগ্ধ চোখে, রক্তে এলকোহোল থাকায় শীত অনুভূত হয় না তেমন, বেরিয়ে এসে বেশ ভালোই লাগে, সঙ্গে কেউ থাকলে আরো ভালো জমতো, এলিনাকে বলা যায় না। একটু ভেতরের দিকে একটা অফ-লাইসেন্স দোকানে ঢুকে এক বোতল ম্যালিবু, স্পার্কলিং এপল, ক্রেইনবারি ও অরেঞ্জ জু্যস নেই, সঙ্গে বেশ ক’রকম ক্রিস্প। ইচ্ছে হয় একটু ধূমপান করি, এত স্নিগ্ধ পবিত্র বাতাসটাকে কলুষিত করবো? থাক। ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় মনে হয় নি, কাঁধের ব্যাগটা আনা উচিত ছিল। সপিং ব্যাগ ঝোলাতে যেয়ে পকেটের বাইরে রাখতে হয় একটা হাত, এক মিনিটের ভেতর জমে বরফ, হাত পাল্টাতে হয় বারবার, গ্লাভসও আনি নি। ভেবেছিলাম, একটু ঘুরে পার্কের পাশ দিয়ে যাবো, তা আর হয় না। ঘরে ফিরে আসি খুব তাড়াতাড়ি।
এক কাপ কফি নিয়ে আরেকটু সহজ হয়ে বসেছে এলিনা।
ঠিক আছো?
হ্যাঁ, আমি তো ভেবেছি, তুমি পালিয়েছো।
কী যে বলো!
কিছুটা সময় একা থেকে মাথায় এলো যে ঝোঁকের মাথায় একটা বাজে কাজ করে ফেলেছি।
কি ওটা?
এই যে, হুট করে চলে এলাম তোমার এখানে।
এ নিয়ে আর ভেবো না, আমি কিছু মনে করি নি, কোনো অন্যায় করো নি।
বিষয়টাকে মনে রেখো না তাহলে।
অবশ্যই না।
আমি বরং যাই এখন।
যাবে? ড্রিঙ্কসটা নিয়ে যাও। এটা শুধু তোমার জন্য। খ্রিস্টের উদ্দেশ্যে।
হো হো হো, ঠিক আছে দাও।
কোনটার সঙ্গে মেশাবো। জু্স ড্রিঙ্কসগুলো দেখাই।
ক্রেইনবারির সঙ্গে দিতে পারো।
বরফ মিশিয়ে পরিবেশন করি। ভয়ে ভয়ে এক চুমুক দিয়ে বলে–
বাহ্, ভালোই তো। অন্য রকম কিছু মনে হচ্ছে না!
তা হবে কেন, চালিয়ে যাও।
আবার হালকা তুষার ঝরতে শুরু করেছে বাইরে, পাতা ঝরে যাওয়া গাছের নগ্ন শরীরে তুলোর মতো ঝুলে আছে তুষার। খাটো, কিছু চিরসবুজ ঝোপে তুষার জমে পুরোপুরি সাদা হয়ে রয়েছে, গাছের অস্তিত্ব প্রায় বোঝাই যায় না। গত কয়েক বছর ধরে সিনেমা হলগুলোয় হাউসফুল থাকা চলচ্চিত্র ‘অ্যা ম্যান ফর অল সিজনস’ দেখানো শুরু করেছে টেলিভিশনে। গ্লাসে ড্রিঙ্কস নিয়ে বসি টিভির সামনে, সিনেমায় মন বসানোর চেষ্টা করি। পল ও ওয়েন্ডি যুগলের অসাধারণ অভিনয় সত্যি মুগ্ধ করে।
এলিনার গ্লাসের ড্রিঙ্কস শেষ হয়ে যাওয়ায় আর এক গ্লাস বানিয়ে দেই আপেল জু্যস মিশিয়ে। চুমুক দিয়ে বলে ‘ওয়াও’। বুঝতে পারি একটু একটু করে এনজয় করা শুরু করেছে। একটু পরে বলে–
আর একটা ভুল করে ফেললাম ডাউ!
কি?
এখন তো ইচ্ছে করলেও যেতে পারবো না। ড্রিঙ্ক-ড্রাইভ করবো কীভাবে?
যেতে বলছি না তো।
তা কি কেউ বলে? আমারই তো যাওয়া উচিত। ঠিক আছে, ট্যাঙ্ িডেকে চলে যাবো, কাল এসে গাড়ি নিয়ে যাবো।
এতো কিছু ভাবার দরকার নেই, সময়ই নিয়ে যাবে, কোথাও না কোথাও।
তাহলে সময়ের হাতেই ছেড়ে দিলাম আমাকে।
ভাগ্য ভালো তোমার, আমার হাতে ছাড়ো নি, হো হো!
হো হো হো, ভালোই বলেছো, তবে তোমাকে বোধ হয় ভরসা করা যায়।
খুব বেশি না।
ঘুম পাচ্ছে। হাই তোলে এলিনা।
বিছানায় যেয়ে শুয়ে পরতে পারো।
তুমি শোবে কোথায়?
ভেবো না, সিনেমা দেখতে দেখতে অনেক রাত সেটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি, আজও তাই হবে।
পরনের কার্ডিগান খুলে হালকা হয়ে টয়লেটে যায়, এই ফাঁকে বিছানা পরিপাটি করে রাখি, এক মিনিটের জন্য জানালা খুলে ঘরের গুমোট বের করে এয়ারফ্রেশনার স্প্রে করে দেই। টয়লেট থেকে বেরিয়ে সোজা যেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, এলকোহোলে অভিজ্ঞতা না থাকায় দু’পেগেই কাজ হয়ে গেছে। রাত জেগে টিভি দেখি, মনের মধ্যে দুর্ভাবনা উঁকি দেয়, কোনো কিছুতে জড়িয়ে যাচ্ছি না তো! এদের বিশ্বাস করি না কোনোভাবে, সাপের মতো বিষাক্ত ছোবল দিতে পারে যে-কোনো সময়। পরদিন ঘুম ভাঙ্গে প্রায়-দুপুরে, জানালার পর্দা খোলা থাকায় কিছুটা আলো এসেছে ঘরের ভেতর, খুব আলসেমি লাগে, একমিনিটের জন্য দরজা খুলে বিশুদ্ধ বাতাস ঢোকাই, জানালা খোলা রাখি একটু সময়ের জন্য। হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেস হয়ে আবার গা এলিয়ে দেই সেটিতে, এলিনা ওঠে নি এখনো, টিভির সাউন্ড বাড়িয়ে দেই, শব্দে কাজ হয়, শোবার ঘর থেকে নেমে আসে, অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে চোখের নিচের দিকটা ফুলিয়ে তুলেছে, ঘুমের রেশ নিয়ে দুলতে দুলতে কাছে আসে। এমনিতেই অপূর্ব সুন্দরী এলিনা, এখন দেখায় অপরূপ! মাথা ঘুরে ওঠে, সামলে নেই, বলি–
সুপ্রভাত।
সুপ্রভাত ডাউ।
ঘুম হয়েছে?
ঘুম কিনা জানি না, অসাধারণ এই অভিজ্ঞতা, এটা থেকে মানুষকে কেন বঞ্চিত করা?
কারণ নিশ্চয় আছে, এবং তা খুবই যুক্তিসঙ্গত। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে যদি পারো, তাহলে তোমাকে বাধা দিচ্ছে কে! হুম… ঘুম ভেঙ্গেছে অনেক আগে, কোথায় আছি সেটা বুঝতেই অনেক সময় লেগেছে, তারপর তোমার সাড়া-শব্দ শুনছিলাম। কেমন একটা আবেশের ভেতর ছিলাম, নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, আমিই এসব করছি কিনা! এটা তো কোনো কৌতুক না, জানো তো, আমার জন্মও হয়েছে এদেশে, আমার কাছে এসব অজানা কিছু না। সহপাঠী বন্ধুদের দেখেছি আঠারো পেরোনোর পরই ডেইটিং করে আসছে, তাও তো করছি না, এসব কি করছি আমি, পাগলামো! কেনই বা?
সহজভাবে নাও না কেন, একধরনের এডভেঞ্চার।
অথবা বলতে পারো একধরনের জেদ, তোমাকে বোঝার চেষ্টা করা, অদ্ভুত মনে হয় তোমাকে, ওসব সম্পর্কে আমার ধারণা হওয়ার আগে থেকে এপ্রোচ পাওয়ার অভিজ্ঞতা পেয়ে আসছি, একেবারে স্কুল-বয়স থেকে, বিশেষ করে আমাদের কমিউনিটির ছেলেদের কাছ থেকে, এতো নোংরাভাবে এপ্রোচ করে ওরা, একেবারে সরাসরি, সেসব ক্ষেত্রে ইংরেজরা অনেক ভদ্র, অনেক ধাপ না পেরিয়ে কখনোই তোমাকে এপ্রোচ করে না। প্রথমে হ্যালো হাই দিয়ে শুরু, দিনের পর দিন একটু একটু করে কথা বলার মাত্রা বাড়ায়, তারপর হয়তো একসঙ্গে চা-কফি খেতে ডাকবে, তারপর ডিনার, লং ড্রাইভ, আউটিং, তারপর হয়তো একসঙ্গে কোনো হলিডেতে যেতে চাও কিনা জানতে চাইবে।
যথেষ্ট অভিজ্ঞতা তোমার, এলিনা!
হ্যাঁ ডাউ, তবে যথেষ্ট নয়, একটা অভিজ্ঞতাই হয়েছিল। কলেজে পড়াকালীন সময়ে ইংরেজ এক ছেলের সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল। একেবারে শেষে, হলিডেতে যাওয়ার জন্য প্রস্তাব দেয়ার পর না বলাতে বুঝতে পেরেছে, ওর সঙ্গে আর এগোবো না, এখনো ভালো বন্ধুত্ব বজায় রয়েছে ওর সঙ্গে। গার্লফ্রেইন্ড নিয়ে এসেক্সে থাকে এখন, ভালোই আছে, সত্যিই ভালো ছিল সে।
হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, নিশ্চয় ভালো ছিল সে।
ঈর্ষা হচ্ছে? তবে তোমার চেয়ে ভালো নয়, মনে হয়।
কীভাবে বুঝলে?
তোমাকে বিশ্বাস করা যায়।
পুরুষমানুষকে কোনো মেয়ে বিশ্বাস করে এটা আবার আমি বিশ্বাস করি না। তাছাড়া তোমাকে এপ্রোচ করি নি বলে অন্য কাউকেও করি নি এটা ভাবলে কীভাবে? আমি তো সাধুপুরুষ না, ব্রহ্মচারী ব্রতধারীও না।
ওটা আবার কি?
ঐ, সেইন্টেরই রকমফের, রাখো ওসব।
হ্যাঁ, কথায় কথায় খামোকা পেঁচিয়ে তোলা অর্থহীন।
ক্ষুধা পেয়েছে মনে হয়।
হাতমুখ ধুয়ে আসো, কি খাবে বলো?
টয়লেট থেকে বেরিয়ে এসে বলে–
আগামী বছরের আগে তো ইউনি যেতে হচ্ছে না, চলো বাইরে কোথাও, লাঞ্চ ব্রেকফাস্ট একসঙ্গে হয়ে যাবে।
মন্দ হয় না।
কফি ও বিস্কুট খেয়ে বেরিয়ে পড়ি।
বরফ পরিষ্কার করে গাড়ি বের করতে যেয়ে নাস্তানাবুদ। রাস্তায় বেরিয়ে বলে–
চলো ব্রিজ পেরিয়ে কাউলিতে যাই কোথাও, অক্সফোর্ডে চেনাজানা কার-না-কার চোখের সামনে পড়ে যাই, বোঝোই তো কোথায় আমাদের সমাজের অবস্থান।
কাউলিতেই বা চোখে পড়বে না ভাবছো কেন?
তাহলে চলো আর একটু এগিয়ে চিপিং নর্টন যাই। ভালো একটা লেবানিজ রেস্টুরেন্ট আছে ওখানে।
দুপুরে খোলা থাকবে ওটা?
হ্যাঁ, বারোটা থেকে তিনটা পর্যন্ত খোলা থাকে, যদ্দূর জানি।
ঠিক আছে, যাও।
শহর ছাড়িয়ে আসার পরই শীতের অবাধ প্রকৃতি, শুভ্র সৌন্দর্য, গাড়ির ভেতর চমৎকার উষ্ণতা ও সুন্দরী রমণী। গতিশীল সময় ও প্রকৃতি, সব কিছু মিলেমিশে মুগ্ধ হওয়ার মতো এক অনন্য সুন্দর পরিবেশ। পাহাড়গুলোর গায়ে কোথাও কোথাও জমে আছে সাদা তুষার, ঢালু জমিগুলোয় গত ফসলের কাটা গাছের গুঁড়িতে ঝুলে আছে বরফ, অসংখ্য গাছের গুঁড়ির উপর জমে থাকা বরফে মনে হয় লক্ষ লক্ষ সাদা কোনো ফুল ফুটে রয়েছে, মাঝে মাঝে চিরসবুজ গাছের সারি, বিশাল ফসলখেতের বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতি গড়ে তুলেছে প্রকৃতির অনন্য ও একান্ত ক্যানভাস।
চিপিং নর্টনের লেবানিজ রেস্টুরেন্টটা ছোটো, কিন্তু বেশ সাজানো-গোছানো। পরিবেশনকারী সব সাদা আরব, খাবারের স্বাদ বেশ ভালো। আমরা নিয়েছি স্কু্যড-ল্যাম্ব-মিট, বাবা-ঘানৌস, হামুস, কিবেত-ব্যাতাতা ও মেঘলি। ইওগার্ট দিয়ে বানানো আয়রান পানীয়টা সত্যি চমৎকার। ওদের তো আর দাদা বলা যায় না, খাওয়ার পর না হয় বলতাম পেট পুরে খেলুম দাদা, অগত্যা ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে আসি। তখনো তিনটে বাজে নি। মাথায় বোধ হয় বায়ু চড়েছে এলিনার, বলে– এখন ঘরে ফিরে আর কি হবে, কারোই তো কাজকর্ম নেই, চলো বার্মিংহ্যাম যাই, মাত্র ঘণ্টাখানেকের ড্রাইভ, ওখানে ডিনার সেরে ঘরে ফিরবো। ওকে বলি, আমিই বরং এখন নিজেকে ছেড়ে দিলাম সময়ের হাতে! সময়ের হাতে, না আমার হাতে, বলে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। মনে হয় এক প্রকৃত পাগলিনীর হাতেই পড়েছি।
গাড়িতে বসে একটা কুর্দি গান ছেড়ে দেয়, অসাধারণ! গানের বাণী না বুঝলেও সুর সত্যিই উষ্ণ করে তোলে। মাঝে মাঝে উর্দুতে কথা বলার চেষ্টা এখনো ছাড়ে নি ও, সরাসরি একদিন বলেছিলাম যে ঐ ভাষাটির প্রতি কোনো আগ্রহ নেই আমার। কথার ফাঁকে দু’একটা বাক্য উর্দুতে বলে ফেলে যখন দেখে চুপ করে আছি, বুঝতে পেরে বলে, দুঃখিত ভুলে উর্দু এসে গেছে। গানের কথাগুলো বোঝে কিনা জিজ্ঞেস করি। না, সেও বোঝে না, ওর এক কুর্দি বান্ধবী ক্যাসেটটা উপহার দিয়েছে, কুর্দি গানের জগতে ঐ গায়িকা এখন সবার সেরা, এটা একটা উদ্দীপনামূলক গান। মনে মনে হাসি, কুর্দিরা কি আর জাগবে কোনো দিন! যে-কোনো জাতির শত শত বছর লাগে একজন সালাদিনের জন্ম দিতে। নিজেরা খুনোখুনি করে মরছে এখন, আর ভাবছে আকাশ থেকে পাখির ঝাঁক পাথর ছুঁড়ে ওদের বিপক্ষ সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে! কোভেন্ট্রির কাছাকাছি এসে শহরে গাড়ি ঢুকিয়ে দেয়, বলে– চা খাবো এখানে। জিজ্ঞেস করি_
ঠিক আছো তো এলি?
বহুত খুব।
এখন আমার বিশ্বাস হতে থাকে যে মেয়েটার মাথায় সত্যিই ছিট আছে। যা খুশি করুক, হাতে তো কোনো কাজ নেই তেমন। তাছাড়া, সত্যি বলতে কি, এই পাগলামোটা ভালোই লাগছে, মুক্ত জীবন, মন যা বলে তাই করা, এটার ভেতর এক ধরনের আনন্দ আছে, এলিনা এখন যেভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে অবাধে, একা অথবা অন্য কারো সঙ্গে হয়তো এটা পারতো না, একজন নির্ভরযোগ্য সঙ্গী পেয়েছে, নিজের মন ও শরীর, দুটোই মুক্ত করে দিয়েছে।
কভেন্ট্রি শহরটা বেশ বড়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বোমার আঘাত থেকে পুরোনো কেথেড্র্যালটাও রক্ষা পায় নি, শহরটাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল জার্মানরা, আবার নতুনভাবে গড়ে তুলেছে সব, শহরের অনেক অংশ বেশ ঝলমলে, আধুনিকতার ছোঁয়া সবকিছুতে, বিশেষ করে নতুন কেথেড্র্যাল ভবনটা অনন্য সুন্দর। দেয়ালের ট্যাপেস্ট্রি, কাচ ও ব্রোঞ্জের কারুকাজ অসাধারণ। কিছুটা সময় বের করে নেই শহরটা এক নজর ঘুরে দেখার জন্য, এ কাজটা না করে কেন জানি কোনো জায়গা ছেড়ে আসতে পারি না।
চা খাওয়ার পর মনে হয় এক কাপ চায়ের প্রয়োজন ছিল আমারও, শরীরের চাহিদা বোঝা যায় না অনেক সময়, বেশ চাঙা হয়ে ওঠি। বার্মিংহ্যামের বুলরিঙে ঢুকে বেশ রমরমা লাগে, ক্রিসমাসের পর বক্সিং ডেতে প্রায় সবকিছুই সেইলে বিক্রি হচ্ছে, প্রচুর কেনাকাটা করছে মানুষ, এসময়টার অপেক্ষায় থাকে অনেকে। আমাকে একটা জ্যাকেট কিনে দেয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে এলিনা। আমি বলি, তোমাকেই তো আমার কিনে দেয়া উচিত, সেখানে আমার জন্য তুমি নেবে, এটা হয় না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হই একটা জ্যাকেট নিতে, দোকান থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি একটা বেঞ্চে বসে বলে, গায়েরটা পাল্টাও, তাও করি। দুটো লিপস্টিক গছাতে সমর্থ হই ওকে, ঘুরে ফিরে অনেক কিছু কেনে এলিনা, অক্সফোর্ড থেকে অনেক বেশি সস্তা মনে হয় সবকিছু। এতো মানুষের ভিড়ে ঘুরে ঘুরে বেশ মজাই লাগে, শরীরের জড়তা কেটে যায় অনেকটা। নিঃসঙ্গতা, নিস্তব্ধতা যেমন ভালো লাগে, তেমনি হৈ-হুল্লোড় ও প্রচুর সমাগম, বিচিত্র মানুষজন কখনো কখনো খুব আকর্ষণ করে আমাকে! স্টারবাক্স থেকে দু’কাপ কফি ও স্যান্ডউইচ খেয়ে আরো চাঙ্গা হয়ে ওঠি। উলওয়ার্থে ঢুকে আবার এলিনা, নিজের জন্য অনেক কাপড় কেনে, আমাকে বলে পছন্দ করে দিতে, আমি বলি মেয়েদের পোশাক গায়ে চড়ানোর পর সুন্দর, আর সুন্দরীরা সব পোশাকেই সুন্দরী, যে-কোনোটা নিতে পারো তুমি। একগাদা কাপড় কিনে বেরোয়, এবার মনে হয় তেষ্টা পেয়েছে আমার, ওকে বলি, এক পাইন্ট বিয়ার নিতে ইচ্ছে হচ্ছে খুব। ঠিক আছে, কিনে নেবো, গাড়িতে যেতে যেতে পান করো, ফেরার পথে কোথাও থামবো না আর। সেইন্সবারিতে ঢুকে চারটা স্পেশাল ব্রুয়িং কার্লসবার্গ নেই। এক বোতল ব্র্যান্ডি নিতে বলে ও, জিজ্ঞেস করি, কেন? বলে, নেওই না। পচাত্তর সিএলের একটা কনিয়াক নেই, সঙ্গে মেশানোর জন্য সিরাজ পোর্ট ও লেমনেড নেই, প্রচুর খাবার-দাবার কিনে বেরিয়ে আসি, সবকিছুতে পুরোপুরি ভরে গেছে বিশাল ট্রলি। গাড়িতে বসেই বড় এক ঢোক বিয়ার গলায় ঢেলে দেই। এলিনা বলে, সাবধানে পান করো, সামনের সিটে বসে এলকোহোল নেয়া বৈধ না, মোড়কে জড়িয়ে নেই বিয়ারের ক্যান। বেশ দ্রুত চালিয়ে ঘরে ফিরে আসে এলিনা, ওর ঘরে। একটু অপ্রস্তুত হই, গাড়ি থেকে মালামাল সব নামিয়ে রেখে বলি_
যাই। ও বলে–
যাচ্ছো না, ড্রিঙ্কস কিনলাম কেন?
বলো কি! না না, এটা ঠিক হবে না। আমি যাই।
বলেছি না বাসায় কেউ নেই, একদম একা আমি।
সে জন্যই তো থাকা ঠিক হবে না।
হবে, বলে হাত ধরে টেনে সোফায় বসায়।
আমি চাই না, কোনো বিপদে পড়ো তুমি।
ওটুকু কাণ্ডজ্ঞান আছে আমার, তেমন কোনো সম্ভাবনা থাকলে তোমাকে আনতাম না এখানে। আর বিপদ নেই কীসে? জীবনে টিকে থাকাটাই তো বিভিন্ন ধরনের বিপদের মধ্যে থাকা। চুপ করে বসো একটু, ফ্রেস হয়ে আসি।
কাপড়-চোপড় পাল্টে টয়লেট থেকে বেরিয়ে আসে অন্য এক এলিনা, উপমহাদেশীয় পোশাক, লাল টুকটুকে সালোয়ারের উপর সোনালি কাজ করা বাদামী রঙের কামিজ, উজ্জ্বল লাল রঙের ফিনফিনে উড়নি, চোখে হালকা কাজল ছুঁইয়েছে, অপরূপ লাগছে ওকে, ও যদি বাঙালি হতো, দিব্যি, শত সহস্র দিব্যি রেখে বলি, জীবন সঁপে দিতাম ওর হাতে। কিছুটা বিমর্ষ হয়ে পড়ি, ভয়ও লাগে, এরকম অভিজ্ঞতা আমার তো নেইই, এমনকি শুনিও নি। কোনো ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছি, না এরিমধ্যে ধরা পড়ে গেছি, বুঝতে পারি না। ঘরে ঢোকার আগে কেএফসির স্পাইসি চিকেন ও ফ্রাই কিনে এনেছিল এলিনা, টেবিলে পরিবেশন করে, কনিয়াকের সঙ্গে অন্যান্য ড্রিঙ্কস মিশিয়ে দু গ্লাস তৈরি করে টেবিলে রাখি। টস করে চুমুক দেই দু’জনে, একটু অবাক হই, কোনো রকম উত্তেজনা বা চোখমুখের আদল না পাল্টে দিব্যি ঢোক গেলে এলিনা। জিজ্ঞেস করি, আগে কখনো এলকোহোল নিয়েছো? খুব নিশ্চিত ভঙ্গিতে বলে, নাহ্। আমার সংশয় আরো ঘনীভূত হয়, কখনো ওকে সত্যিই সরল মনে হয়, আবার কখনো খুব বেশি ঘোড়েল, সন্দেহপূর্ণ। যেভাবেই হোক ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হবে, মনে মনে পণ করি, কোনোভাবেই ওর হাতে ছেড়ে দেবো না নিজেকে।
তুমি কি একটু হালকা পোশাক নেবে? একদম নতুন ট্রাউজার আছে, লিনেনের, তোমার হতে পারে।
একদু’ঘণ্টা পর ফিরে যাবো, কি দরকার।
মনে হয় না যাচ্ছো।
তোমার এখানে থাকবো কি করে?
আমি থেকেছি কীভাবে কাল?
না এলি, ফিরে যাবো।
দেখা যাক।
স্পাইসি চিকেনগুলো বেশ মজার, কেএফসির এই আইটেমটা বরাবরই পছন্দ আমার, ঘরে বানানো একটা আচার দিয়েছে এর সঙ্গে, বেশ ভালো লাগে, কথার ফাঁকে ফাঁকে উঠে যেয়ে কাবাব ভেজে আনে, ব্ল্যাক ওলিভ, আঙুলের সমান ছোটো আকারের শসার পিকলস, টর্টিলা, পাপাডাম, নিমকপারা, একটার পর একটা টেবিলে আনতে থাকে, ড্রিঙ্কসের সঙ্গে সব উধাও হয়ে যায়, মনে হয় একটা দৈত্য ঢুকে পড়েছে শরীরের ভেতর। আসার পথে দু’ক্যান স্ট্রং বিয়ার নিয়েছি, সব মিলিয়ে কখন যে মাতাল হয়ে পড়েছি বুঝতে পারি নি। মনে হয় পরিকল্পনা করেই মাতাল করেছে আমাকে এলিনা। ভুল ভাঙ্গে যখন টেবিলে ওর গ্লাস রাখতে যেয়ে এক ফুট উঁচুতে ওটা ছেড়ে দেয়। পানীয় গড়িয়ে টেবিলক্লথ, কার্পেট ভিজে যায়। জড়ানো গলায় বলে, টেবিলটা এতো নিচু হলো কখন? ওকে জড়িয়ে ধরে সোফায় বসাই, টেবিল নিচু হয় নি সোনা, তুমিই উপরে ভেসে উঠেছো। টেবিলক্লথ গুটিয়ে ওয়াশিং মেশিনে ঢুকিয়ে দেই, মোছার কাপড় দিয়ে কার্পেট ভালো করে মুছে এয়ারফ্রেশনার ছড়িয়ে দেই। টেবিলের সবকিছু গুছিয়ে ওর পাশে এসে বসি। দেখি, ঘুমিয়ে প্রায় এলিয়ে পড়ছে। জিজ্ঞেস করি, ঘুমোও কোথায়? হাত তুলে বলে, দোতলায়। বলি, থাক যেতে হবে না ওখানে। সোফাতেই শুয়ে পড়ো। এটুকুই মনে আছে। পরদিন ঘুম ভাঙলে দেখি জড়াজড়ি করে কার্পেটে শুয়ে আছি দু’জনে। ওরও ঘুম ভাঙ্গে, এই প্রথম, ছোট্টো করে একটা চুমো দেই ঠোঁটে, কয়েক হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। ছিটকে উঠি, অনেক হয়েছে, তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড়, চুলটুল ঠিক করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি, মনে মনে বলি, বিদায় এলিনা!
প্রকৃতপক্ষে ঘটে না। কিশোরকালের একটা ঘটনা মনে পড়ে। স্কুলের বাৎসরিক বন্ধ থাকার সময় আমাদের আরবি শেখানোর ব্যবস্থা করতেন বাবা, পাড়ার মক্তবের হুজুর ছিলেন আমার আরবি শিক্ষক। কি এক প্রসঙ্গে বলেছিলেন, মেয়েরা হচ্ছে আগুন আর পুরুষ মোম, ওদের কাছাকাছি যাওয়া থেকে দূরে থাকিস বাবা। বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি। আমার অবস্থা দেখে হুজুর বলেছিলেন, এখন বুঝবি না, পরে বুঝবি, বয়স হলে। হুজুরের ঐ কথাটা পুরোপুরি বুঝতে শুরু করেছি এখন। আমার ভেতর আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে এলিনা, মোমের মতো গলতে শুরু করেছি।
বাসায় এসে দীর্ঘ সময় নিয়ে বাথ নেই, ঘরে রান্না করার চেষ্টা করি, বন্ধু আবীরকে ডাকবো কিনা ভাবছি, ভয় হচ্ছে এলিনা যদি আবার এসে ওঠে, শেষ পর্যন্ত একা থাকারই সিদ্ধান্ত নেই, বই পড়ায় মন বসে না। গ্যারি কূপার ও অড্রে হেপবার্নের ‘লাভ ইন দ্য আফটারনূন’ সিনেমা শুরু হয়েছে টিভিতে, ওটা দেখায় মন বসাই। ভালোই হয়েছে, কেউ আসে না, এলিনার বোধ হয় হ্যাঙওভার হয়েছে, অথবা বোধোদয়। নিউ ইয়ার্স ইভে একটা পার্টিতে নিমন্ত্রণ আছে, ওটায় যাবো, সেলুন থেকে চুল কেটে আসি, শেভ করে চেহারাটা চকচকে করে তুলি। খুব ভালো ঘুম হয় রাতে। সকালে ফ্রেশ হয়ে মনে মনে পরিকল্পনা করি নিউ ইয়ার্সের আগের এই কটা দিন পড়াশোনা করি। কিছু পেপারওয়ার্কস করে রাখি, এসাইনমেন্টগুলো এগিয়ে রাখি।
এগারোটার দিকে দরোজায় টোকা, বুক কেঁপে ওঠে, অন্য কেউ তো হতেই পারে না, ঘরে ঢুকেই বলে–
চটপট তৈরি হয়ে নাও, গ্লাসগও যাবো।
হঠাৎ মেজাজ চটে ওঠে, বাইরে প্রকাশ করি না, ভেবেছে কি, ওর ইচ্ছার দাস হয়ে পড়েছি, ভদ্রতা অনেক করেছি, কটু কথা না বলে ফেলি সেই ভয়ে চুপ করে থাকি।
বুঝতে পারছো ডাউ?
আমি যাচ্ছি না এলিনা… আমাকে বাধ্য করছো কেন?
না ডাউ, বাধ্য করছি না তোমাকে। অনুরোধ জানাচ্ছি, একটা মাসের জন্য মুক্তিতে আছি, মুক্তির আনন্দ তুমি জানো না, যা খুশি করতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার, যা খুশি, কোনো কিছুই আটকাচ্ছে না। জানি না এই অবাধ স্বাধীনতা জীবনে আর আসবে কিনা, অথবা আমিই আনবো কিনা, ঠিক আছে, তুমি যেতে না চাইলে থাক।
পোষা একটা বাজপাখির মতো বশীভূত হয়ে পড়ি, আমার আদিগন্ত আকাশটা ছেড়ে ওর ছোট্ট কাঁধে এসে বসি। এভাবে ভেবে দেখি নি ওর বিষয়টা। ক্ষণিকের এই আনন্দ যাপন থেকে কোনোভাবে বঞ্চিত করতে চাই না ওকে। ওর চিবুকে হাত রাখি, ছলোছলো চোখে অসীম আকাশ, দু’হাতে মুখ তুলে ধরি, ঠোঁটজোড়া স্বর্গের তোরণের মতো স্বাগত জানায়, নিজেকে নামিয়ে দেই ওখানে, অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে যাই যেখানে টেনে নিয়ে যায় জীবনের সুগভীর রহস্য! ভালোবাসি ওকে পূর্ণ আবেগে, পরিপূর্ণ প্রেমে!
ক্লান্তিতে অবসন্ন দু’জনেই, একটু পরে ঘরে ফিরে যায় ও। বুঝতে চেষ্টা করি কি করে ফেলেছি, শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলাম ওর কাছে! ধীরে ধীরে ধাতস্থ হই, মেনে নেই পরাজয়, যা ঘটেছে, তা যেনো অবশ্যম্ভাবী, কোনো হাত নেই এসবের পেছনে আমার, বা কারোই, অপ্রতিরোধ্যভাবে ঘটে চলেছে এসব, যেনো নিয়তি-নির্ধারিত, হাল ছেড়ে দেয়া ছাড়া করার কিছুই নেই, কিই বা করতে পারতাম, জীবনের এসব অনুষঙ্গের সঙ্গে পরিচয় ছিল না, অপরিকল্পিতভাবে কোনো কিছু করার কথা ভাবি না, কিন্তু প্রবল ঝড়, সাইক্লোনের মতো তেড়ে আসে যখন, মানুষের ছোট্টো দুহাতে কি তা ফেরানো যায়? সমর্পণের বাইরে কিছুই করার থাকে না, নিজেকে ছেড়ে দেই প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মের কাছে।
বিকেলে ওর দরোজায় টোকা দেই, দরোজা খুলেই অবাক, এবার আমার ভেতরের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে অকস্মাৎ, ওখানেই জড়িয়ে ধরি, ওভাবেই সোফা পর্যন্ত হেঁটে যাই কোনোভাবে, তারপর উন্মাদ হয়ে যাই দু’জনেই। দীর্ঘ সময় পর উঠে যাই, গুছিয়ে টেবিলে বসি, চা খাই, প্রথম কথা বলি–
বেরোবে কখন? আমি ব্যাগ গুছিয়ে এসেছি।
গ্লাসগও আট দশ ঘণ্টার ড্রাইভ, এমনিতেও ব্রেক জার্নি না নিয়ে যেতাম না, যেটুকু সময় আছে ম্যানচেস্টার পর্যন্ত যাওয়া যাবে, রাস্তায় প্রচুর গাড়ি থাকবে।
বছরের এসময়ে হোটেল পাওয়া যাবে ম্যানচেস্টারে?
কোনো না কোনো তো পাওয়া যাবেই।
তাহলে ওঠো, দেরি করো না।
আধ ঘণ্টা সময় দাও, বোঝো তো মেয়েদের প্রস্তুতি।
বুঝতে শুরু করেছি।
হো হো হো!
ঠিক আধ ঘণ্টার মধ্যেই সেজেগুজে বেরিয়ে আসে। আমার স্যুটকেইস নিতে আসি, যদিও বলেছি গুছিয়ে এসেছি, আসলে তো না, দশ মিনিটের মধ্যে রাস্তায় বেরিয়ে দেখি প্রায় ছ’টা। শীতের রাত দু’ঘণ্টা পেরিয়েছে প্রায়, যদিও একটু একটু করে বড় হতে শুরু করেছে দিন, তুষারপাত থেমে গেছে, প্রকৃতি কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল, ঝড়ো বাতাস ও সামান্য বৃষ্টি, এমন দুর্যোগের দিনে বাংলাদেশের মানুষেরা কল্পনাও করতে পারে না রাস্তায় বেরোবে। ধীরে-সুস্থে গাড়ি চালিয়ে রাত দশটার দিকে ম্যানচেস্টার পৌঁছাই। হোটেল পেতে বেগ পেতে হয় নি, গাড়ি পার্ক করে মালামাল রুমে রেখে রাতের খাবার খেতে বেরোই। ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের জন্য ম্যানচেস্টারের বিখ্যাত কারি-মাইলের একটা হোটেলে খেয়ে নেই। রুমে ফিরে পুরোপুরি পাগল হয়ে যাই, জীবনের এতো মধু কোথায় ছিল কে জানে, দু’জনে উজাড় করে দেই দু’জনকে, শেষরাতের দিকে ওকে বলি, তোমাকে তো ড্রাইভ করতে হবে কাল, হ্যাঁ, বলেই ঘুমিয়ে পড়ে। আমার ছোট্টো টেবিল ঘড়িটা সঙ্গে এনেছিলাম, এগারোটায় এলার্ম সেট করে ঘুমিয়ে পড়ি, গভীর ঘুম। ঘড়িটা যখন ঘণ্টি পেটাতে থাকে মনে হয় অনেক দূরের কোনো এক দেশে স্কুল ছুটি হয়েছে! অবশেষে চোখ মেলে তাকাই, দেখি সেজেগুজে একদম রেডি হয়ে আছে এলিনা! অবাক হই, তাড়াতাড়ি উঠে একটা কুইক শাওয়ার নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়ি, নিচে নেমে ডাইনিং হল থেকে হোটেলের ফ্রি ব্রেকফাস্ট নিয়ে নি, চেক-আউট করে বারোটার মধ্যে বেরিয়ে পড়ি।
বিকেল তিনটের দিকে নিউক্যাসেলে পৌঁছে বলে–
আজ রাত এখানে কাটাই, কাল খুব সকালে এডিনব্রা যাবো, এডিনব্রা ক্যাসেল ঘুরে সন্ধ্যায় গ্লাসগও যাত্রা করবো।
হ্যাঁ, কাল সন্ধ্যায় বলবে, আজ রাত এডিনব্রাতেই কাটাই, কাল খুব সকালে গ্লাসগও যাবো।
কোনো কিছুই তো নির্ধারিত নেই ডাউ, ক্ষতি কি?
না, কোনো ক্ষতি নেই।
টাইন নদীর তীরে চমৎকার একটা হোটেল পেয়ে যাই। আমার মানিব্যাগে হাত দিতে দেয় না। বলে, প্রচুর অর্থ আছে আমার বাবার, আর এসবের উত্তরাধিকার আমরা দু’বোন, টাকাপয়সার বিষয়টা ভাবতে হবে না তোমাকে। দু’হাতে খরচ করে চলেছে এলিনা। স্কলারশীপের হাতেগোনা টাকায় যাপিত জীবনে এসব অনেক বেশি মনে হয় আমার কাছে।
হোটেল থেকে দ্রুত বেরিয়ে পড়ি, আলো থাকতে থাকতে রোমানদের গড়া হা’ড্রিয়ান ওয়ালটা দেখে নেই। তুষার নেই, কিন্তু হাড়-কাঁপানো শীত, উত্তরের এই শীতে অনভিজ্ঞ মানুষেরা, এমনকি স্থানীয় অনেকেও, স্পেইন, বেলজিয়াম, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশের উপকূলীয় উষ্ণতায় পাড়ি জমায়, আর আমরা এসেছি এখানে বেড়াতে, খেপা মানুষের সবই সয়!
সিটি সেন্টারে একটা চায়নিজ রেস্টুরেন্ট দেখে জিজ্ঞেস করি, রাতের খাবার সেরে নেবে নাকি এখানে? রাজি হওয়ায় ঢুকে পড়ি, এখানের চায়নিজের স্বাদ বাংলাদেশের ধারে-কাছেও না। তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে শুয়ে পড়ি, যথারীতি সারারাত জেগে। ভোরে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে গ্লাসগওর পথে নামি, পুরোটা পথ পাহাড়ি চড়াই-উৎড়াই, রাস্তার দু’ধারে বরফ জমে সাদা হয়ে আছে, খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে হয়, এলিনা বেশ ভালো গাড়ি চালায়, ইউরোপের ছেলেমেয়েদের দুটো পায়ের মতোই চারটে চাকা, অসাধারণ নিয়ন্ত্রণ। হোটেল খোঁজার আগে দুপুরের খাবার খেয়ে নেই, ও দেখি আমার মতোই, খাবারের স্বাদ ও রুচির প্রতিই প্রাধান্য দেয়, অনুমোদিত অথবা নিষিদ্ধের ধার ধারে না, যে-কোনো রেস্টুরেন্টে খাবার পছন্দ করতে সমস্যা হয় না।
রাতের গ্লাসগও সত্যিই সুন্দর, এবং শীতের গ্লাসগওর এক অন্যরকম বিশেষত্ব রয়েছে। পরদিন আর গাড়ি নিয়ে বেরই না, একটা সিটি ট্যুর কিনে নেই, শহরটা ঘুরে দেখি, মাঝখানে খাবারের বিরতিতে দু’ঘণ্টায় টুকটাক শপিং করে নেয় ও। ফিরে এসে ক্লান্তি বোধ করি, অথচ ওকে দেখে মনেই হয় না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ড্রাইভ করছে! অফুরন্ত প্রাণশক্তি। রাতে যখন বলে নিউ ইয়ার্স ইভ লন্ডনে কাটাবে, আমার মাথায় বাজ। বলি, আগামীবছর। ও বলে, হ্যাঁ, আগামীবছরই তো। শুধরে বলি, না, তার পরের বছর। গোঁ ধরে, অক্সফোর্ডে ফিরে সারাদিন রেস্ট নেবো। সন্ধ্যায় বাসে যাবো, টেমস নদীর তীরে নিউ ইয়ার সেলিব্রেইট করে রাতেই ফিরে আসবো, তারপর আবার দীর্ঘ ঘুম! হেসে বলি, তোমার ঘুম মানে তো ঘুম নয়। বলে, ঠিক আছে, শোবো!
লন্ডনে নববর্ষ উদযাপনটা সত্যি স্মরণীয় হয়ে রয়েছে, অসাধারণ ঐ রাতের অভিজ্ঞতা, এমন অফুরান আনন্দ জীবনে কমই এসেছে এর পর! ওখান থেকে ফেরার পথে কিছুটা আত্ম-উপলব্ধি আসতে শুরু করে। কি করছি এসব? এলিনার দিকে দৃষ্টি রেখে ভাবছি যখন, চোখ ঠেরে জিজ্ঞেস করে–
কি?
হঠাৎ করে ভেবে পাই না কি বলবো, বলি–
অনেক বেশি সুন্দর তুমি এলিনা, কল্পনার মতো।
তোমার দৃষ্টির স্বচ্ছতা হবে হয়তো।
আমি পরাস্ত, এলিনা।
না, তুমি জয়ী।
জানি না, এলিনা, সত্যিই জানি না।
জানো, তুমি জানো, ডাউ।
এসব যেনো স্বপ্ন হয়, এলিনা।
এসব সত্যি, ডাউ।
জীবন এক রহস্য।
এসব রহস্যের জন্যই বেঁচে থাকা, না হয় জীবন অর্থহীন।
দু’জনেই এতো ক্লান্ত ও অবসন্ন যে ঘরে ঢুকেই ঘুমিয়ে পড়ি, গভীর ঘুমের পর জেগে উঠি প্রায় একসঙ্গে, অথবা আমাকে জাগিয়ে তোলে ও, ঘুম থেকে উঠেই আবার! কিন্তু এই উদ্দামতার অবসান হতে হবে তো! দু’তারিখে ওর বাসা ছেড়ে চলে আসি, পড়াশোনায় মন দিতে হবে, আমার কৃষক পিতা নিজের জীবন অর্পণ করে বিলেতে পাঠিয়েছে আমাকে। বিকেলে আসার পর ওকে বুঝিয়ে বলি, বিষয়টা বুঝতে পেরেছে এজন্য মনে মনে খুশি হই। রাতে শুয়ে শুয়ে গেল হপ্তাটা কল্পনা করি, এরকম একটা ঘোরলাগা সময় জীবনে কখনো আসে নি, আসবেও না আর, নিশ্চিত জানি, এতো আনন্দ, এতো উচ্ছল আবেগ, এতো অবাধ স্বাধীনতা, উচ্ছ্বাস, উদ্দাম, সবকিছুই কল্পনাতীত!
ওর পরিবার না আসা পর্যন্ত প্রায় এক মাস প্রতিরাতই ওর ওখানে কাটিয়েছি, দিনগুলো আমাকে নিষ্কৃতি দিয়েছে পড়াশোনার জন্য। বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে, ওরও যেতে হয় ক্লাশে, বিষয়টা নিয়মিত হয়ে যায়। আচ্ছন্ন এক জীবন কাটাতে থাকি কিছুদিন!
৪
অসাধারণ এক গ্রীষ্ম এসেছে এবার বিলেতে, তাপমাত্রা খুব বেশি ওঠে না, বৃষ্টিপাত নেই। এতো ফুল ফুটেছে, বাতাসে পলেনের পরিমান খুব বেড়ে গেছে, অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। রল্ফের ধরেছে হে-ফিভার, আমার সারা শরীর লাল হয়ে যায় রোদে গেলেই, কিন্তু অবাধ আলোর বন্যা, প্রকৃতির এতো রং, মানুষের এই প্রাণচঞ্চলতা ছেড়ে ঘরে বসে থাকাও যায় না।
এর মধ্যে ছোট্ট একটা খবর জানিয়ে বড় ধরনের এক আতঙ্কের মধ্যে ফেলে দেয় এলিনা, হতে পারতো এটা সুসংবাদও, কিন্তু দুঃসংবাদের মতোই মনে হয় এখন এটা। সবার আগে আবীরের পরামর্শ নেই। ও বলে, বিয়ে করে ফেল। সমাধানটা তো এতো সহজ নয় রে আবীর! এলিনার সঙ্গে সম্পর্কটা অনেক গভীরে পৌঁছেছে, কিন্তু এর প্রায় সবটাই শারীরিক, দু’জনেরই শরীর শিথিল হবে এক সময়, তখন সম্পর্কটা কোথায় যেয়ে দাঁড়াবে? পাশ্চাত্যে বাস করেও আমার আদি ও অকৃত্রিম বাঙালি প্রাণটাকে তো বাতিল করতে পারি নি, বিয়ে করাকে জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় মনে করি এখনো। ভালো হলে ভালো, না হলে আবার চেষ্টা করার মধ্যে নেই আমি। স্ত্রীকে শুধু শরীরসঙ্গী হিসেবে চাই না, আজীবনের বন্ধু, সুখে দুখে, হাসি কান্নায় সব সময় একান্ত প্রাণের সহচরী হিসেবেও চাই। এলিনা তা হতে পারবে না কখনো।
মানসিক এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া হয় না। ঘরে কাটাই সারা দিন। বিপর্যস্ত এ অবস্থায় হালকা সুরা পান, বিশেষ করে হোয়াইট ওয়াইন, ও সকল সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা, সহজ ও জটিল সব মুহূর্তের আশ্চর্য প্রেরণাদাতা ও রক্ষাকর্তা আমার গুরুর গান শুনি: ফেলিলে একি বিষম দায়ে…
পরদিন রল্ফের শরণাপন্ন হই। সব শুনেটুনে বলে–
এতো ভাবাভাবির কি আছে, ঝুলে পড়ো।
আমি কি ঝুলে পড়বো, সেই তো ঝুলে আছে আমার সঙ্গে!
বিয়ে করতে চাইলে করে ফেলো, না চাইলে ক্লিয়ার করে ফেলো।
আমার কাছে না ওটা, যে ক্লিয়ার করে ফেলবো।
জিজ্ঞেস করেছো ওকে?
ক্লিয়ার করার কথা জিজ্ঞেস করি নি।
তাহলে রেখে দাও।
তোমাকে বোঝাতে পারছি না রল্ফ, আমাদের কমিউনিটিতে এটা খুব খারাপ ধরনের অপরাধ।
এলিনা কি বলে?
বিয়ে করে ফেলতে।
তাহলে দুটোর একটা তো করতে হবে, অথবা ফেলতে হবে, অথবা দুটোই।
বিপদে ফেললে রল্ফ।
বলো কি, বিপদে ফেললাম আমি?
না না, ওভাবে মিন করি নি।
বুঝেছি ডাউ, ঠাট্টা করলাম।
সত্যি বুঝতে পারছি না, কি করবো।
অস্থির হয়ো না, সব কিছুরই কোনো না কোনো সমাধান আছে।
সত্যি?
তাই তো জানি।
চুপ করে থাকি অনেক্ষণ। কিছু একটা ভাবছে রল্ফ। আমার মন বলে, ওটাকে ফেলে দেইও বা কীভাবে! আমার প্রথম শরীরশিল্প, একটা প্রাণের প্রথম উল্লাস! উন্মেষ, প্রথম সৃষ্টি! এটা ধ্বংস করে ফেলা! আতঙ্কে শিউরে ওঠে শরীর, কি বিপদে ফেলেছো হে ভগবান! রল্ফের কথায় চেতনা ফিরে আসে।
এক কাজ করো ডাউ, বিকেলে আমার কাছে নিয়ে আসো ওকে, আমার এক বন্ধু, গাইনি, প্রাইভেট ক্লিনিক আছে ওর লিভারপুলে। স্বাস্থ্যের অবস্থাটা দেখি ওর, যে-কোনো কিছু ভাবার আগে প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে, কোথায় আছি আমরা। জানো ওটার বয়স কত?
ও বলেছে দু’হপ্তা পেরিয়েছে স্বাভাবিক ঐ সময়ের।
ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। বিকেলে নিয়ে আসো।
দেখি।
ওর কি ইচ্ছা?
ও তো চায় বিয়ে করে ফেলি।
ওটাই স্বাভাবিক।
ওর পক্ষে।
ঠিক আছে, বিকেলে আসো, দেখা যাক কি করা যায়। আর একটা বিষয় বুঝে উঠতে পারছি না, এটা হয় কীভাবে? এরকম অপরিকল্পিত ঘটনা সাধারণত টিন-এজারদের মধ্যে ঘটে। পরিণত বালক-বালিকারা তো পরিকল্পনা করে এটা করে।
কিছুই জানায় নি আমাকে এলিনা।
নিরোধ নাও নি কেন?
শুরু থেকেই নিশ্চিত করেছে আমাকে, সেই নাকি নিচ্ছিল ওটা।
তাহলে ঘটেছে কীভাবে এটা?
আমি বলবো কেমন করে?
ও, আমি বলতে পারবো।
ফাজলেমো করছি না আমি।
ঠিক আছে, আমি করছি… এখানে এসব কিছু ঘটে গেলে, হয় ওরা বিয়ে করে নেয়, না হয় ক্লিয়ার করে। এমনকি বিয়ে না করেও বাচ্চা নিয়ে নেয়। অনেক সময় ছেলেটা পিতৃত্ব স্বীকার করে নেয়, আবার কখনো নেয়ও না। কি আসে যায় তাতে?
আমাদের সমাজে এটা চলে না, বুঝতে চেষ্টা করো রল্ফ। আমরা এখনো ঐ অবস্থায়ই আছি।
আমি তো মনে করি বরং ভালো অবস্থায়ই আছো।
হয়তো।
যাহোক, একটা কিছু ভেবে দেখবো, একটু সময় দাও, প্লীজ। তোমার এ বিষয়টা আমার কাছেও অভিনব।
ঘরে এসে বসে থাকি জানালায় চোখ রেখে, ক্ষুধা লেগেছে, খেতে ইচ্ছে হয় না, আকাশ পাতাল ভেবেও কূল পাই না। দুপুরের দিকে দরোজায় টোকা। আতঙ্কিত হই, এলিনা নিশ্চয়, কি বলবো এখন ওকে? দরোজা খুলে দেখি, রল্ফ! ঘরে ঢুকেই বলে–
তোমার জন্য খুব ভালো ব্র্যান্ডের একটা সিগারেট এনেছি।
কৌতুকের সময় এটা! মনে মনে রেগে যাই। প্রাইম টাইম সিগারেটের একটা প্যাকেট খুলে ধরে। কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয় না।
সিগারেট দিতে আসো নি নিশ্চয়, রল্ফ।
জানালা খুলে চেয়ার টেনে বসি ওখানে, সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করি–
বলো রল্ফ।
ক্ষুধা লেগেছে ডাউ, সিগারেটের বিনিময়ে কিছু খাবার আশা করতে পারি না?
পারো পারো, নিশ্চয় পারো।
ফ্রিজ খুলে দেখি মেক্সিকান ফাহিতার প্যাকেট আছে একটা। গ্রীন পেপার, চেরি টমেটো ও রেড অনিয়ন দিয়ে স্টা’রফ্রাই করে রুটিতে রেপ করে দেই। আমিও নেই একটা। দু’কাপ কফি নিয়ে খেতে বসি। চুপচাপ খেতে থাকি। রল্ফের চোখের কোনায় সেই অলৌকিক, দুষ্টু হাসিটা লেগে রয়েছে। মনে মনে কিছুটা স্বস্তি পাই, নিশ্চয় কিছু একটা ভেবে বের করেছে, না হলে ওটা থাকতো না ওখানে, রুটি শেষ করে বলি–
বলো রল্ফ।
কি?
আমাকে টেনশানে না রাখলে শান্তি লাগে না তোমার?
কি কারণ আছে এটার বলো তো?
না, কোনো কারণ নেই, বলো এবার।
ঠিক আছে বললাম, ধন্যবাদ তোমাকে, সুখাদ্য পরিবেশনের জন্য। যাই এবার, আশা করি দেখা হবে বিকেলে।
সত্যি উঠে পড়ে চেয়ার থেকে। দ্বিধায় পড়ি, লিভিং রুমে যেয়ে ফিরে দাঁড়ায়, হাসি মুখে বসে ওখানে, বলে–
বিকেলে এসো না ডাউ। আরেকটু ভেবে দেখলাম, তোমাকে একটু অভিনয় করতে হবে, আমাকে নিশ্চিত হওয়ার জন্য।
কি সেটা?
ওকে নিয়ে আমার এখানে আসার আগে খুব হাসি খুশি কিছু সময় কাটাও একসঙ্গে, এবং বলো বিয়ের কথা। বিয়ের বিষয়ে সব রকম কথা বলো, সম্ভাব্য একটা তারিখও ঠিক করে ফেলো, এজন্য কীভাবে এগোবে পরিকল্পনা করা শুরু করো। তারপর যখন মনে করো পুরোপুরি আস্বস্ত সে তোমার উপর, তখন বলো যে, শারীরিক কিছু চেকআপ করা খুব জরুরী, খুব নির্ভরশীল তোমার একজন বন্ধু আছে লিভারপুলে, গোপনে সব কিছু সেরে দেবে, তারপর ওকে নিয়ে যাও ওখানে। কথা বলে রাখবো আমি। আমার কথা কিছু বলো না, তাহলে সম্মত নাও হতে পারে ও।
এটা কি ঠিক হবে রল্ফ, প্রতারণার মতো হয়ে যায় না?
দেখো ডাউ, সব কিছু এখন বলতে চাই না তোমার কাছে, আমাকে যদি বিশ্বাস করো, তাহলে এটার দায়িত্ব আমার।
কিছু ভাবতে পারছি না রল্ফ।
আস্থা রাখতে পারো আমার উপর। কোনো ক্ষতি হোক তোমার এটা কখনোই চাইবো না আমি।
জানি রল্ফ।
ঠিক আছে, যাই এবার।
ওকে, বাই।
সি ইউ এগেইন।
সি ইউ রল্ফ।
বুকের ভেতর অনবরত কাঁটার খোঁচা সহ্য করেও রল্ফের পরামর্শ মতো অভিনয়টা করে যাই। মনে মনে খুশি হই, অভিনয়ে অবিশ্বাস্য পারদর্শিতা আমার। পরদিন বিকেলে লিভারপুল যাই। সবকিছু ঠিকঠাক মতো চলে, বুকের পাথরটা মুহূর্তের জন্য নামিয়ে রাখতে পারি না। আবীর ও রল্ফ দু’জনে আপ্রাণ চেষ্টা করে আমাকে হালকা হাওয়ায় ভাসিয়ে রাখতে। দু’দিন পর টেস্ট-রেজাল্ট পেয়ে মনে হয় শাব্দিক অর্থেই ওজনশূন্য হয়ে পড়েছি।
এলিনাকে দেখে বোঝা যায় না কিছুই, খুশি না হতাশ! আমার মতোই হালকা হয়ে নিঃশ্বাস নেয় আবীর। বলে–
বড় একটা ভাবনা থেকে রেহাই দিয়েছিস দাউদ।
তাই আবীর, তাই।
চল এটা সেলিব্রেইট করি।
অবাক হই। বলি–
উল্টোটাই সেলিব্রেইট করে মানুষেরা।
হ্যাঁ করে। যখন ইচ্ছায় হয় ওটা, এখন আমরা না-হওয়াটা সেলিব্রেইট করবো।
ঠিক আছে, কর।
আউয়াল আসুক, ওকে নিয়ে লং ড্রাইভে যাবো।
কবে আসবে ও?
আর বলিস না, আট মাস হয়েছে দেশে গেছে, এখনো আসার খবর নেই, ফোন করেছিল গত হপ্তায়। আগামী মাসের তিন তারিখে ফ্লাইট।
ভালোই হলো, যাক।
দেশে যেয়ে কি থাকা যায়, বল?
ইচ্ছে থাকলেও পারা যায় না, প্রতিদিনই এটাকে আরো খারাপ করে তুলছি আমরা।
অস্থির হোস না, মানুষের ইচ্ছে নদীর মতো গতিশীল। ক্রমাগত অবদমন ভীষণ চাপের মুখে রেখেছে এসব, কোনো না কোনো ফুটোফাটা দিয়ে বেরিয়ে আসবেই একদিন।
আমরা কি জানি আমাদের ইচ্ছেগুলো কি?
তোমার আমার হয়তো অনেক জটিল ইচ্ছেও আছে। সাধারণ মানুষের ইচ্ছে তো অতি সরল, একটু সহজ একটা জীবন।
মাথাপচা স্থুলবুদ্ধি রাজনীতিবিদদের হাত থেকে নিষ্কৃতি কি পাবে ওরা সহজে?
নিশ্চয় পাবে।
আমাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধটাই তো গড়ে উঠতে পারছে না। সরকারী শব্দটাই হয়ে গেছে ‘ফেলনার’, ওটাও যে ‘আমার’ এবং অনেক বড় করে আমার, এটাই তো বুঝতে দেয়া হচ্ছে না আমাদের।
জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠবে কীভাবে? বাঙালি জাতীয়তাবোধের শৈশবেই তো কোথাকার এক দালাল এসে এক কোপে ওটাকে বাংলাদেশী বানিয়ে ফেলেছে! এর পরের ইতিহাস তো খুনোখুনির, পাল্টাপাল্টি প্রতিশোধের, রাজপরিবারের প্রতিহিংসার। এ পর্বটা শেষ হলেই দেখবি শুভযোগ ঘটবে।
আশা যেনো পূর্ণ হয় তোর, একটা কাজের কাজ যেনো করতে পারে বাঙালিরা।
এখন হয়তো এটা সম্ভব না, এখন তো ওদের দুটো হাতই ব্যস্ত, কাজ করবে কি দিয়ে?
বুঝি নি।
ওদের একটা হাত ব্যস্ত সামনের জনের ওখানে গুঁতোতে, আর দ্বিতীয়টা পেছনে, নিজের ওখানটা বাঁচাতে।
হো হো হো।
কথাটা সত্যিই হাসির না। বেশির ভাগ মানুষই এখন ও কাজে ব্যস্ত।
যাকগে, কি কথা থেকে কি কথা এসে গেলো।
তাই তো দেখি।
এখন একটু হোক।
হোক।
কোথায় যাবি?
চল, একটা পাবে যাই।
চল।
কাউলিতে যাই। পাবে যেয়ে ভুলে যাই সব।
নিয়মিত যাওয়া শুরু করি বিশ্ববিদ্যালয়ে। পড়াশোনার ক্ষতিটুকু সারিয়ে তুলতে মন দেই। ফিরে আসে আগের দিনগুলো, রোদে গলা পিচের মতো লেগে আছে এলিনা, যেখান দিয়েই হেঁটে যাই, ছাপ পড়ে যায়। কি করি বুঝতে পারি না। এটারও সমাধান রল্ফ ছাড়া দিতে পারে কে আর? বলে_
হঠাৎ করে এভোয়েড করার চেষ্টা করো না, হিংস্র হয়ে উঠতে পারে সে, বেরিয়ে আসার চেষ্টা করো, ধীরে ধীরে।
সে চেষ্টাই তো করছি রল্ফ, পারছি না।
কি বলে ও।
একই কথা, বিয়ে করে ফেলতে।
না অন্য কিছু।
অন্য কিছুটাও চাই না।
বলো কি, অমন অপ্সরী থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও কীকরে?
বুঝতে, আমার অবস্থায় পড়লে।
সুযোগ করে দাও না, পড়ে দেখি।
রল্ফ, তোমার খালি ফাজলামো।
তাই কি?
চুপ করে থাকি। আবার বলে–
একটা স্ট্রং ডোজ দেই তোমাকে, এক কাজ করো, আরেকটা প্রেম করে ফেলো, দেখবে সুর সুর করে পালাবে।
তোমাকে বোধ হয় গালাগাল দেয়া শুরু করতে হবে।
বিশ্বাস করো, এটা একটা ভালো অষুধ, প্রথমে হয়তো ওর সঙ্গে একটা ফাইট দেয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু তোমার দ্বিতীয়জন খুব স্ট্রং, জায়ান্ট, সম্ভব হলে আফ্রিকান নেবে, যেনো শিং দিয়ে গুঁতিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারে।
তোমার সঙ্গে আর পারা গেলো না রল্ফ!
কি করবো বলো, কোনো মানুষই অষুধ পছন্দ করে না প্রথমে, তারপর যখন কাজ করতে শুরু করে ওটা, চালিয়ে যায়। প্রেমিকাকে ভালোবাসে মানুষ সবার আগে, ডাক্তারকে সব কিছুর পরে।
শোনো রল্ফ, আমাদের দেশে একটা কথা আছে, নেড়া একবারই বেলতলায় যায়।
বুঝি নি।
বোঝার দরকার নেই।
তাহলে এক কাজ করো, ওর পেছনে তোমার চেয়েও বেশি সক্ষম আরেকজন লাগিয়ে দাও।
উঠি রল্ফ।
না না, বসো ডাউ। একটু ভাবতে দাও।
ঠিক আছে, যাই এখন।
আচ্ছা শোনো, এ মুহূর্তে দুটো মাত্র বিকল্প পেলাম ভেবে, আরো বেশি পেলে পরে জানাবো।
কি ও দুটো?
প্রথমটা, ওকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে আমার হাতে তুলে দিতে পারো কিনা ভেবে দেখো, নিশ্চিত থাকো, খুব ভালোভাবে যত্ন নেবো ওর। দ্বিতীয়টা, লম্বা হলিডেতে কোথাও যেতে পারো কিনা দেখো।
ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, ড. কস্টার্লিৎজ!
বেরিয়ে আসি ওর ওখান থেকে, ওর ঐ বিখ্যাত বা কুখ্যাত হাসিটা যে আমার ঘাড়ের পেছনটায় ছড়িয়ে রয়েছে এখন, বুঝতে পারি। বাইরে এসে মনে মনে ভেবে দেখি লম্বা ছুটিতে যাওয়ার পরামর্শটা মন্দ দেয় নি। একটু একটু করে সময় কম দেয়া শুরু করি এলিনাকে। অস্থির হয়ে ওঠেছে, এর পর আর একবারও বিছানায় যাই নি, যাওয়ার প্রশ্নই আসে না, দু’বার বেলতলায়? ঝাঁকড়া চুল নিয়েও যেন কেউ না যায়, ভগবানের দিব্যি।
মাসখানেক কেটে যায় এভাবে, এলিনা বুঝতে শুরু করেছে যে এড়িয়ে চলেছি ওকে, বিয়ে করার জন্য চাপ দিতেই থাকে। একদিন কেঁদেকেটে বলে, সত্যিই আমি বাঁচতে চাই না তোমাকে ছাড়া। শেষ পর্যন্ত ওকে বলে ফেলি, এটা সম্ভব না কোনোভাবেই। দু’জনের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা ভিন্ন, বিয়েটা আজীবনের বন্ধন, ছেলেখেলা নয়, বা শরীরের চাহিদা মেটানো নয় শুধু।
এরপর প্রায় মাসখানেক কেটে যায়। ইউনিতে আসা ছেড়ে দিয়েছে এলিনা। দুঃশ্চিন্তাটা আরো গভীর হয়, কোথায় যে জড়ালাম, ভালো লাগে না কিছু, কিভাবে কি হয়ে গেলো! একদিন ফোন পাই ওর বাবার কাছ থেকে। পরিচয় দেয়ার পর বলে, ওদের পরিবারে একটা ভয়ানক বিপর্যয় ঘটে গেছে। ইউনিতে একসঙ্গে পড়াশোনা করে এমন কারো ফোন নাম্বারই নাকি নেই ওদের কাছে, একমাত্র আমার ফোন নাম্বার দিয়েছে যোগাযোগ করার জন্য। গত চারদিন থেকে হাসপাতালে আছে ও, সম্ভব হলে বিকেলে ভিজিটর্স আওয়ারে দেখা করতে পারলে খুব খুশি হয় ওরা।
সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানাই। বিকেলে হাসপাতালে যেয়ে দেখি অন্য এক এলিনা, মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসা। প্যান্টোমাইমের মুখের মতো ফ্যাকাসে, সাদা একটা মুখ, চোখের কোল কুচকুচে কালো, ডাইনিদের মতো। অতিরিক্ত ঘুমের অষুধ খেয়ে এ অবস্থা করেছে। সময় মতো হাসপাতালে আনতে পারায় যমে-মানুষে টানাটানি করে রক্ষা করতে পেরেছে। ওর বোনকে বলে একটু একা কথা বলতে দেয়ার জন্য। ও চলে গেলে বলে_ তোমাকে নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলাম ডাউ, একটা মানুষের জীবন চেয়েছিলাম, মুক্ত মানুষের। তোমাকে ছাড়া মরতে চেয়েছিলাম। সব কিছু থেকেই মুক্ত হতে চেয়েছিলাম। দু’টোর কোনোটাই হলো না, যদি বেঁচে থাকি, অথবা থাকতে হয়, জীবনের বাকিটা অন্য কিছু, আমি জানি না, তবে সেটা জীবন নয় আর। এখন যেতে পারো, আমার প্রতি কোনো দায় নেই তোমার। কিছু বলতে চাই, মুখ খোলার চেষ্টা করতেই ডেকে নিয়ে আসে ওর বোনকে। নিঃশব্দে বেরিয়ে আসি। মনে মনে বলি_
বিদায় এলিনা!
ভীষণ মন খারাপ হয়ে থাকে, কোনো কিছুতেই শান্তি পাই না। এলিনার হাত থেকে ছাড়া পেয়েও না। এখন মনে হয় মেয়েটা সত্যিই ভালোবেসেছিল আমাকে। দেশ থেকে আউয়াল এসেছে, বকবক করে দেশের অনেক ভালো ও মন্দ কথা শোনায়, অন্য সময় হলে হয়তো খুব মন দিয়ে শুনতাম এসব, উপভোগ করতাম, এখন ভালো লাগে না, ওকে সহ আবীর একদিন আয়ারল্যান্ডের পথে বেরিয়ে পড়ে আমাকে নিয়ে। মনের গ্লানি কাটে না, এতো গভীরে ছড়িয়ে পড়েছে এটার শেকড়, কোনোভাবেই উপড়ে উঠিয়ে আনা সম্ভব হয় না।
মাস দুয়েক পর আবার এলিনার বাবার ফোন। বলে, খুব বিপদে পড়ে ফোন করেছে, লন্ডনে চলে গেছে এলিনা, সম্ভবত কালো কোনো ক্রিমিন্যালের খপ্পরে পড়েছে। যে ঠিকানা দিয়েছে ওখানে দেখা করতে যেয়ে দু’দিন ব্যর্থ হয়েছে ওরা। পুলিশে বলতেও সাহস পাচ্ছে না, যদি আবার কোনো অঘটনের চেষ্টা করে। আমি কোনো সাহায্য করতে পারি কিনা, ওর বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র আমাকেই চেনে সে, এজন্য অনুরোধ জানাচ্ছে। আমি বলি, ওর সঙ্গে আমারও তেমন আলাপ ছিল না, ক্লাশমেইট হিসেবে মাঝে-মধ্যে দেখা হয়েছে ইউনিতে, এতটুকুই। সে বলে, বিশ্বাস করে আমাকে, কিন্তু ওর বন্ধুদের অন্য কাউকেই সে চেনে না। অগত্যা ওর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে লন্ডনে যাই। ঐ ঠিকানায়ই থাকে সে, কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা হয় না। দৈত্যের মতো এক আফ্রিকান বেরিয়ে এসে বলে, জানি সত্য বলে নি, এলিনা ঘরে নেই, ঠিকানা বা ফোন নাম্বার রেখে যাও, সে যোগাযোগ করবে, কোনো মেসেজ থাকলে দিতে পারো। শুধু আমার নাম বলি, ও এলিনাকে ফোন করতে বলি। ঐ ফোন আর আসে না কখনো। এদিকে অস্থির হয়ে উঠেছে এলিনার বাবা। এটাই স্বাভাবিক।
মুক্ত হয়েও মুক্তি মেলে না, কেমন এক গ্যাঁড়াকলে ফেঁসে গেছি! রল্ফকে জিজ্ঞেস করি–
বল দেখি এখন কি করি, ভায়া?
সত্যি চাও এখান থেকে বেরিয়ে আসতে?
ঠাট্টা মনে হয় রল্ফ?
তাহলে ওকে আমার হাতে তুলে দাও। আগেও বলেছি।
ও কি একটা চকোলেটের প্যাকেট?
তুমি দিচ্ছো কিনা তাই বলো।
আমার উচ্ছিষ্ট কীভাবে তোমার হাতে তুলে দেই।
ওভাবে দেখা উচিত না।
জানি না রল্ফ, কীভাবে দেখা উচিত।
তোমার পুরোনো পোশাক পরি নি কখনো?
ও তো কোনো পোশাক বা সামগ্রী নয় রল্ফ।
মোটেও বোঝাতে চাই নি তা। ভালোবাসার ধন সে। তুমি কতটুকু জানি না, আমার মনে হয় সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিল সে তোমাকে। এখন দেখি, যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, আমি নিংড়ে নিতে পারি কিনা।
ঠিক আছে, তোমার যা খুশি।
লন্ডনের ঠিকানাটা দাও তো।
আমার কাছে যেটা ছিল, দেই। পরের দিন সন্ধ্যায় এসে রাগে ফেটে পড়ে রল্ফ।
আমি ভাবতেও পারি নি এমনটা করবে তুমি!
কেন, কি হয়েছে?
ওটা ভুয়া ঠিকানা, এক কালো বদমাশ থাকে ওখানে, প্রায় হাতাহাতির পর্যায়ে চলে গেছিল অবস্থা।
আমি যা জানি, তাই দিয়েছি।
ইউ আর এ লায়ার।
টং করে রক্ত চড়ে যায় মাথায়।
নট মি। ইউ আর এ স্নব।
এতো বেশি রেগে যেতে দেখি নি কখনো ওকে। শীতল রক্তের মানুষ, হিস্টিরিয়া রোগীর মতো কাঁপতে থাকে। উঠে যেয়ে বলে–
আই এম সরি, এন্ড গুড বাই।
গেট লস্ট।
সব কিছু ভুলে থাকতে চেষ্টা করি। ধীরে ধীরে জীবন স্বাভাবিক করে আনার চেষ্টায় প্রাণপাত করি। মাসখানেক পর সোয়া-ছয়-ফুট আবার এসে হাজির।
সেদিনের দুর্ব্যবহারের জন্য দুঃখিত ডাউ।
অসুবিধা নেই, বলো।
সত্যি দুঃখিত।
ঠিক আছে। আমিও দুঃখিত।
সব ঘটনা খুলে বলে রল্ফ। বড় একটা নাটক ঘটে গেছে এর মধ্যে। ঠিকানা ওটা ঠিকই ছিল। এই এক মাস ধরে নিজেই এক গোয়েন্দা হয়ে উঠেছিল রল্ফ, ঐ ঠিকানা থেকে সরিয়ে ফেলেছিল এলিনাকে। সম্ভবত একটা ট্রিপল এক্স মুভির চরিত্র বানিয়ে ফেলার জন্য এলিনাকে টার্গেট করেছিল ওরা। ঐ কালো শয়তান ওকে বিক্রি করে দেয় একটা গ্রুপের কাছে। অনেক টাকা পয়সা খরচ করে বিভিন্ন সূত্র ধরে শেষ পর্যন্ত ওকে উদ্ধার করেছে রল্ফ। এ যেন বলিউডের এক গোয়েন্দা কাহিনী, ভালো চলচ্চিত্র নির্মাণ করা যায় এটা নিয়ে। এখন এলিনা রয়েছে রল্ফের বাসায়, দু’জনেই ডুবে আছে দু’জনের সব ধরনের প্রেমে। খুব খুশি রল্ফ। এ সুসংবাদটা দিতে এসেছে।
রল্ফের ওখানে ওকে দেখতে যাওয়ার অনুমতি কাউকেই দেয় নি এলিনা। জানায়ও নি কাউকে, বাবা-মাকে নাকি টেলিফোনে জানিয়েছে ভালো আছে সে। রল্ফের সঙ্গে পরামর্শ করে ওকে দেখার জন্য একদিন একটা পাবে যাই আবীর সহ। বিশ্বাস করা কঠিন যে ও-ই এলিনা! অনেক ছবিও দেখিয়েছে ওর রল্ফ। বি্লচ ও ডাই করে চুল ব্লন্ড করে ও ছোটো করে ছেঁটে আল্ট্রামডার্ণ স্টাইল নিয়েছে, পড়নে স্লীভলেস টপস, শর্ট গাউন, হাই হীল জুতো, চোখে নকল মনি লাগিয়েছে, ব্লু, আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত লাভার মতো জ্বলজ্বলে লিপস্টিক! কোনোভাবেই বোঝার উপায় নেই যে ইউরোপীয় নয় সে। খুব ভালোভাবে চেনে যারা ওরাও ধরতে পারবে না। আগের মতো নাদুসনুদুস নেই, স্লিম, ফেটে পড়া গ্ল্যামার। নবজন্ম হয়েছে যেন এলিনার। সত্যি অর্থেই নবজন্ম হয়তো। যাক, মনে মনে খুশি হই, সুখে থাক ওরা, সুখে থাক ধরা। বুকের ভেতর জমাট বেধে থাকা নিঃশ্বাসগুলো পাম্প করে বের দেই। হালকা হয়ে উঠি, আবীরকে বলি, আউয়ালকে ডেকে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে দূরে কোথাও। চ্যানেল পেরিয়ে ‘আইল অব ম্যান’এ নিয়ে ফেলে আমাকে। ক’দিনের জন্য সমুদ্রের নীলে ডুবে থেকে নিজেও হয়ে যাই পুরোপুরি নীল, ও নিল।
প্রায়ই দেখা করতে আসে রল্ফ। দিনের পর দিন, ধারাবাহিকভাবে এতো বেশি খুশি খুব বেশিদিন দেখি নি ওকে। আমারও ভালো লাগে খুব, দু’জনেই আমার প্রাণের খুব কাছের, ওদের ভালোলাগায় আপ্লুত হই। আর কোনো খাদে না পড়ার জন্য সাবধান থাকি, যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে মনে হয়। একদিন জিজ্ঞেস করে রল্ফ–
তোমার কোনো খেদ নেই তো ডাউ?
মোটেও না। তুমি যদি ওকে নিয়ে খুশি হও, আর এলিনাও সুখী হয়, আমার জন্য এর চেয়ে বেশি আর কি চাওয়ার থাকতে পারে, বলো।
একটা দুঃস্বপ্নের মতো ভুলে থাকি দিনগুলো, পড়াশোনায় মন দেই। বিজ্ঞানের জগত দূরে রাখি কিছুদিনের জন্য, লরেন্স স্টার্নের ‘দ্য লাইফ এন্ড অপিনিয়ন অব ট্রিস্ট্রাম স্যান্ডি, জেন্টলম্যান’ বইটা পড়ে অভিভূত হই, সময় পেলে এ বইটা অনুবাদ করবো, অথবা বন্ধু জ্যাককে বলবো এটা অনুবাদ করতে।
দু’মাস না যেতেই উদ্ভ্রান্তের মতো এসে হাজির রল্ফ!
এলিনাকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না ডাউ, এখন কি করি?
মাথায় যেনো বাজ! এতো দিন আমি কি করি তা নিয়ে গেছি রল্ফের কাছে, এখন উল্টো সে আমার কাছে! বলি–
শান্ত হও, কি হয়েছে বলো, আস্ত একটা মানুষ ও, শূন্যে মিলিয়ে যাবে না।
আসলেই কি মানুষ ও?
ভালো একটা প্রশ্ন করেছো রল্ফ। মনে হয় এলিয়েন, এলিনা নয়।
একটা উল্কা, বাতাসের যে স্তরেই যায়, নিজে জ্বলে, ঐ স্তরটাকেও জ্বালিয়ে দেয়।
তোমার কথাই হয়তো ঠিক।
না, তাও না, উল্কা হলে তো জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যেতো।
যাহোক, কবে থেকে উধাও হয়েছে?
পরশু।
আগে বলো নি কেন?
সম্ভাব্য সব জায়গায় খুঁজেছি।
আমার এখানে খুঁজো নি কেন?
মন বলে নি।
এবার তাহলে ভুল বলেছে তোমার মন।
চমকে ওঠে।
সত্যি?
না রল্ফ, ঠাট্টা।
ওহ্, সত্যি হলেই ভালো হতো, দুঃশ্চিন্তায় অভ্যস্ত নই, একটু বিপাকে পড়ে গেছি।
ভেবো না, সব সমস্যারই সমাধান আছে।
ওর কথাটাই ফিরিয়ে দেই, একটু চমকায়।
ওর বাবাকে ফোন করবো কিনা ভাবছি। রল্ফ বলে, আর ক’টা দিন সময় নাও। ওকে উদ্ধারের দিনের ঘটানাটা বলে। প্রায় মাসখানেক ফলো করে একটা সপিং সেন্টারে পেয়ে যায় একদিন। দেখা করে বলে, তোমার জন্য একটা সুসংবাদ আছে এলিনা, একটু আড়ালে আসো। চট করে একটা পাবে ঢুকে যাই, যা ওর সঙ্গী কল্পনাও করে নি। এলিনাও বুঝতে পেরেছে যে কালোদের জালে জড়িয়ে পড়েছে সে। রল্ফের প্রস্তাব পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ওর সাথে অক্সফোর্ড চলে আসতে রাজি হয়ে যায়। একটা ট্যাক্সি ডেকে ভিক্টোরিয়া কোচ স্টেশনের প্রথম বাসটাতেই উঠে বসে। ওটা ছিল হেরিফোর্ডের। তারপর হেরিফোর্ড থেকে আবার অক্সফোর্ড ফিরে আসে। ওকে বোধ হয় ড্রাগেও এডিক্ট করিয়ে ফেলেছিল। নিজে ডাক্তার হওয়ায় সব কিছু ঠিকঠাক করে ফেলতে পেরেছে রল্ফ।
হপ্তাখানেক পাগলের মতো কাটায় রল্ফ, যে ভালোবাসা আমি দিতে পারি নি এলিনাকে, তা বোধ হয় দিয়েছে রল্ফ। এলিনার তো সুখী হওয়াই উচিত ছিল। তা হয়তো হবার নয়। রল্ফের পক্ষে যা যা করার সব করে, যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করি আমিও। বিফলে যায় সব। এক সকালে আমার এখানে এসে হাল ছেড়ে দেয় রল্ফ।
আর পারছি না ডাউ।
ঠিক আছে বসো।
ওর বাবাকে ফোন করি। বলে–
দেশে চলে গেছে এলিনা, গতকাল।
দেশে?
হ্যাঁ, দেশে।
আমি যেনো বুঝতে পারি না। জিজ্ঞেস করি–
ভালো আছে তো ও?
হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো। আপনারা দুশ্চিন্তা করবেন না।
রল্ফ ও আমার, দু’জনেরই শুরু হয়, ‘দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন!’
৫
বিষয়টাকে কীভাবে ধরবো ঠিক বুঝতে পারি না, জীবনকে গভীরভাবে দেখার কোনো কারণ সৃষ্টি হয় নি তখন পর্যন্ত। হলে ভালো, না হলে হলো না, এভাবে দেখতে চেয়েছি সব, বুঝতে চেয়েছি। কোনো জটিলতার ভেতর জড়ানো আমার ধাতে নেই, অথচ পড়ে গেছি পারিবারিক এক টানাপোড়েনের ভেতর। ভালোবাসি ফুটবল, দৌড়ে যেয়ে এক লাথিতে বলটা ঢুকিয়ে দাও গোলের ভেতর, অথবা ক্রিকেট, মারো ছক্কা, নয়তো কট বা বোল্ড আউট, দাবা খেলার মতো জটিল অঙ্কের খেলা আমার ভালো লাগে না।
বিপন্ন আয়ারল্যান্ডের প্রত্যন্ত এক অঞ্চল থেকে আসা কেরোলাইনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠেছে গত চার বছরে। ভালোভাবেই মনে আছে আমার ‘চাচার মেয়ে আয়েশা’! ভবিষ্যতে ওর সঙ্গে কিছু একটা ঘটার বিষয়টা কখনো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নি, ওকে আমি চাচার মেয়ের বাইরে অন্য কোনো কিছু এখনো ভেবে উঠতে পারি নি, প্রেমিকা বা স্ত্রী তো নয়ই, এমনকি বোনও না। সত্যি কথা, আমার মনোজগতে ওর কোনো স্থানই নেই। অথচ পারিবারিক কি এক হিসাব-নিকাশের অঙ্কে বাঁধা পড়ে আছি। মাঝে মাঝে ওর ঐ বিশিষ্ট-নামটাও অন্যরকম কিছু একটা সৃষ্টি করে আমার ভেতর, ওটা মনে হলে আগে বিবি ও পরে সমীহ-জাগানো একটা বাক্য মনে এক পূণ্যভাব সৃষ্টি করে, কদমবুসি করার মতো অনেকটা। ওকে নিয়ে আস্ত একটা জীবন যাপন, শুধু জীবন যাপনই না, একটা পরিবার গড়ে তোলা, হে মহাকালের প্রভু, রক্ষা করো!
গত চার বছর ধরে আমার সহপাঠী কেরোল, আকস্মিকভাবে ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে দু’বছর আগে। কিছুটা অর্থ জমিয়ে ছোট্ট একটা ক্রুইজিঙে যাই নর্থ পোলে। জাহাজেই জমে ওঠে বন্ধুত্ব, গ্রীষ্মে অপরূপ উত্তর মেরুর নিগর্গে পল্লবিত হয়ে ওঠে, মুকুলিত হয়, যদিও ফল ধরে না কোনো। সুন্দরীই বলা যায় ওকে, সাজলে তো বটেই, সোনালি চুল, নীল চোখ, নাকের ডগায় ছোট্ট একটা বল, রেড নোজ ডে’তে কৃত্রিম নাক লাগাতে হয় না ওকে, নাকের ডগাটা লাল রং করে নিলে একেবারে অরজিন্যাল। শরীরের গড়ন ককেশিয়ান, মাঝারি, অথচ পেছনটা আফ্রিকান, আমার জন্য বরং ভালোই, ওকে বলি, এমন মেলানো-মেশানো শরীর আয়ারল্যান্ডে হলো কীভাবে? বলে পেছনটার কথা জানি না, কিন্তু নাকের ঐ গোল অংশটা আলপাইন গোত্রের মানুষের বিশেষত্ব, তোমাদের এশিয়ায় যেমন চায়নীজদের বোঁচা নাক, আর্যদের যেমন কাকাতুয়া পাখির মতো ধারালো নাক, এই আর কি। আমাদের বন্ধুতার দ্বিতীয় বছরে মনস্থির করি একত্রে থাকার, একটা স্টুডিও ফ্ল্যাট ভাড়া নেই, নিচের তলা, শীতে যদিও কিছুটা স্যাঁতসেঁতে, হিটার চালিয়ে গরম ও শুকনো রাখতে হয়, গ্রীষ্ম সেটা পুষিয়ে দেয়। পেছনের খোলা চত্বরে ফোল্ডিং চেয়ার মেলে সমুদ্র-সবুজ মখমল ঘাসের উপর শরীর মেলে দেয়া যায়। টবের ভেতর রকমারী ফুলের গাছ। টমেটো, রেডিশ, পয়েন্টেড ক্যাবেজ, ড্যানিশ লেটুস প্রভৃতি চাষ করা যায়। ভাড়া বাড়িটার মালিক ছিল না, ছিল এক মজার বুড়ি, ওর নাম ধরে ডাকা ছেড়ে দেই বাসাটা ভাড়া নেয়ার দ্বিতীয় হপ্তায়। আমার কিংবা কেরোলের কারোই পুরো নাম ধরে ডাকা বন্ধ না করায় আমরাও ওকে আওয়ার লেইডি মালকিন নামে ডাকা শুরু করি। বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করে মালকিন মানে কীরে? বলি ঔনারের স্ত্রীলিঙ্গ। ওটার আবার স্ত্রীলিঙ্গ হয় নাকি! হয়, আমাদের ভাষায়। তোমাদের ভাষাটাই আমার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে কেন? বাহ্, প্রতি হপ্তায় আট পাউন্ড ভাড়া নিতে পারবে আর ছোট্ট একটা শব্দ নিতে পারবে না? আমার তাহলে আরো এক পাউন্ড ভাড়া বাড়লো।
আমাদের ফ্ল্যাট বিল্ডিংটার পেছনের খোলা জায়গার পর এক সারি হোলি ট্রী, তারপর ছোট্ট একটা মাঠ, মাঠের পর এক সারি বাংলো। সাধারণত বুড়োবুড়িরা বাংলোয় থাকে, যাদের দোতলায় ওঠানামা করার সামর্থ নেই, অথবা এটাকে ঝক্কি মনে করে। বাংলোগুলোর একটায় থাকে আওয়ার লেইডি মালকিন। প্রতি সকালে কুকুর নিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি, অথবা খেলাধুলা করে কাটায়, প্রতিটা হপ্তাহান্তে এসে জিজ্ঞেস করে কেমন আছে খোকাখুকুরা! বসার একটা আসন দেখিয়ে দেবে কেরোল। বাচ্চাদের একটু সময় হবে? হবে, ঘণ্টায় এক পাউন্ড। তাই সই, ঐ যে বিদঘুটে শব্দটা, মাঙ্কি না মিল্কি, ওটার জন্য ভাড়া যে এক পাউন্ড বেড়েছে, তা কাটাকুটি। তারপর শুরু হবে ওর মজার সব কাহানি। ভগবান, এতোও জানে বুড়িটা!
আমাদের ফ্ল্যাটের এক কোনায় একটা গ্যারেজ আছে, ওটার পাশেও খালি জায়গা অনেকটা, একটা ক্যারাভান পার্ক করা ওখানে, শেষ কবে ওটা চালানো হয়েছিল, ভগবানও ভুলে গেছেন, চাকার মেটালে একটু একটু মর্চে পড়া দাগ, জানালার কাচগুলো ধুলোয় ধূসর, ভেতরের স্ক্রিন যদিও দেখা যায়। ওর স্বামী বেঁচে থাকতে পুরো গ্রীষ্ম নাকি ওটার ভেতর কাটাতো। আমাদের ঘর থেকে বেরোনোর সময় প্রতিবারই একটা কথা বলতো মজার বুড়ি, ‘এই, রাতে কিন্তু এক বিছানায় শুবি না তোরা।’ প্রথমবার একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল কেরোল, ‘কেন?’ ‘তাহলে এ ফ্ল্যাট ছেড়ে দিতে হবে তোদের, দু’জনের বেশি এখানে থাকা চলবে না।’ আমরা তো হেসেই খুন। আর ওটাই এখন ওর সম্ভাষণ হয়ে ওঠেছে, আমরাও বলি, ‘আচ্ছা, আচ্ছা মালকিন, আওয়ার লেইডি মালকিন!’ তারপরই ঘরে ঢুকে দীর্ঘ চুমো খাই, উষ্ণতা নেই, পরস্পরে। কেরোলও বলে, ‘এই, রাতে কিন্তু এক বিছানায় শোবে না।’ মুখ কপট-কালো করে বলি, ‘আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে, মাই লেইডি!’
হাঁটতে বেরোই উইকেন্ডে। মাঠের পাশ দিয়ে রাস্তাটা নেমে গেছে ঢালুতে, ওখান থেকে বাঁদিকে বেরিয়ে গেছে একটা কাঁচা পথ, পাথর বিছানো ঐ পথ দিয়ে একটা ট্রাক্টর অথবা গাড়ি যেতে পারে, বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ি কখনোই ক্রস করতে হয় না বলে রাস্তার চওড়া এতো কম যে একটা ট্রাক্টর আসায় রাস্তার পাশে সরে দাঁড়াতে হয়। ওখানটা পেরিয়ে যেতে যেতে হাত নেড়ে ড্রাইভার জানায়, সামনে এগিয়ে যাও, অনেক মজার আবহাওয়া পাবে, ওর ঝোলানো গোঁফ-জোড়া ও অকৃত্রিম হাসি-চোখ মনে থাকে অনেকক্ষণ। দু’পাশে হথর্নের সারি রেখে রাস্তাটা সোজা সমতলে এগিয়ে গেছে অনেকটা. তারপর বাঁয়ে বাঁক নিয়ে বিশাল একটা পাহাড়ের পায়ে শেষ হয়েছে, ওখান থেকে শুরু চষা জমি, পুরো পাহাড়টা ট্রাক্টর দিয়ে লাইন টেনে যেনো ছবি এঁকে রেখেছে। এটার কথাই সম্ভবত বলেছে গোঁফ-ড্রাইভারটা, শুকনো বাদামি রং মাটির নকশা ছুঁয়ে দৃষ্টি উঠে যায় সরাসরি আকাশে, চষা খেতও যে এতো সুন্দর হয় এই প্রথম বুঝতে পারি। ঐ খামারি নিশ্চয় একজন আদর্শ শিল্পী, মনে মনে প্রশংসা না করে পারা যায় না। বাসায় যেয়ে ক্যামেরা এনে ছবি তুলতে চায় কেরোল। এতোটা পথ আবার? কাল না হয়। বোঝানো যায় না ওকে, আমাকে রাস্তার পাশে শুইয়ে ফিরে যায়। একটা মানুষ নেই আশেপাশে, শুধু বাতাসের সামান্য দোলা, আকাশেও কোনো পাখি নেই, বাংলাদেশে এমন নীল আকাশে একটুও ফাঁক থাকে না যেখানে চক্কর কেটে ঘুরে বেড়ায় না পাখির ঝাঁক! ইচ্ছে হয় পাহাড়টার চূড়ায় উঠি, কোনোভাবেই সম্ভব না, ফিরে এসে ছবি তোলায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে কেরোল। পাহাড়ের পাশ দিয়ে হেঁটে যাই কিছু সময়, এবার সামনে পড়ে ছোট্ট আর একটা পাহাড়, ওটার একপাশে ছোট্ট একটা বন, বড় বড় গাছের সারি, কাছে যেতেই আবহাওয়া বদলে যায় হুট করে। শীতল, মাদকতাময়, বুনো শ্যাওলাটে একটা গন্ধ, গা ছম ছম করে ওঠে, হিংস্র কোনো প্রাণী নেই তো ওটার ভেতর। অভয় দেয় কেরোল, ইংরেজদের চেয়ে হিংস্র কেউ নেই, সব শেষ করে দিয়েছে ওরা। বনের ভেতর ঢুকি, ওখানে বাতাসের শব্দ শোনা যায়, অনেক গাছ জড়িয়ে আছে ঘন সবুজ লতা ও পাতায়, ঐসব গাছের কাণ্ড ও শাখা প্রায় সব ঢাকা পড়েছে, আর কোনো কোনো গাছের কাণ্ড একেবারে নেড়া, ওদের গায়ে কোনো লতার শেকড় ঢোকানো সাধ্য নেই, কি খেয়ে বেঁচে থাকবে! মানুষের মধ্যেও এমন কিছু মানুষ আছে যাদের ঘিরে থাকে সবুজ লতাপাতা, ওরা সক্রেটিসের মতো। বনের ভেতরটা এতো অন্ধকার, বোঝা যায় না বাইরে এতো অবাধ আলো! ছোট্ট ঐ বন পেরোলে একটা খোলা জায়গা সামনে আসে আবার, ওখানে ঘাস এতো বড় যে দিব্যি ঢেকে ফেলা যায় নিজেদের। হয়তো এটাও চাষের জমি ছিল, পতিত থাকায় ঘাস জমে জঙ্গল হয়ে উঠেছে। মানুষের সাড়া পেয়ে লাফাতে থাকে একপাল বুনো খরগোশ, কি সুন্দর ও নিরীহ প্রাণী এই খরগোশগুলো, একেবারে হাতের নাগালে এসেছে, শান্ত সুন্দর চোখ-জোড়া মেলে তাকায়, শুধু খেলার ছলে মানুষেরা কীভাবে শিকার করে শান্ত এই প্রাণীগুলো! কি বোকাই না বানায় বোকা এই প্রাণীদের, ধাওয়া করে বিপরীত দিকে ওৎ পেতে থাকা শিকারি বন্দুকের সামনে নিয়ে আসে। জীবন বাঁচাতে ছুটে আসে ওরা যেখানে অপেক্ষায় রয়েছে অবধারিত মৃতু্য, কী নিষ্ঠুরতা! আকাশের পাখি যেমন নির্বিবাদে শিকার করে মানুষেরা হাতের নিশানা ঠিক করতে, ঠিক তেমনি জলে স্থলে সর্বত্রই মানুষের চরম নির্মমতা! ঈশপের ব্যাঙ আজো একই সুরে বলে, তোমাদের জন্য যা খেলা, আমাদের জন্য তা মৃত্যু!
ঘাসের বন পেরিয়ে যাই, ছোট্ট একটা চারণভূমি, অনেকগুলো গাভী, অনেকের সঙ্গে রয়েছে বাছুর, একটু দূরে অলস পায়ে দাঁড়িয়ে তিনটে ঘোড়া, এখান থেকেও বোঝা যায় ওদের একটা অন্তত পুরুষ, কোনো লজ্জা ছাড়াই কালো একটা বাদুড় ঝুলে আছে ওখানে। চারণভূমির এক পাশে বেশ বড় একটা খাল, স্পষ্ট বোঝা যায় বৃষ্টির জল জমে ওখানে পুরো শীত জুড়ে, বরফ হয়ে থাকে কখনো কখনো, এক ধরনের শ্যাওলা শুকিয়ে আছে, বড় ঘাস বা ঝোপ নেই কাছাকাছি, এসব দেখে মনে হয় আদিম দিনের পৃথিবী, সব কিছু প্রাচীন ও পবিত্র, সভ্য বলে কথিত বিশ্বের মানুষেরা সবকিছু যে পাল্টে ফেলেছে তা ভুলে থাকা যায় কিছুক্ষণের জন্য। যদি কিছু পাখ-পাখালিও থাকতো! এসব বনের কোথাও ফিজেন্ট পাখিদের আবাস ছিল, তাও শিকার করে নিধন করা হয়েছে অনেক আগে, বাংলাদেশ থেকে যেমন হারিয়ে গেছে অনেক প্রজাতির ঘুঘু, ডাহুক, সারস প্রভৃতি পাখি। আদিম প্রকৃতির ছোট্ট একটা খণ্ড, বাংলাদেশে যা অভাবনীয়, পেরিয়ে এসে হঠাৎ একটা জাঁকালো খামারবাড়ি সামনে এসে পড়ে। সুন্দর সাজানো গোছানো গাছপালা, বহুবর্ণিল ফুলের বিলেতি বাগান, পাথরের বাড়ি, এক ধরনের ঘাসে ছাওয়া চাল, হোলি ট্রীর চিরসবুজ ও কণ্টকময় দেয়াল, ফণীমনসায় গড়া এরকম দেয়াল বাংলাদেশে একসময় দেখা যেতো। ছোট্ট একটা সাইনবোর্ডে খামার-মালিকের নাম লেখা, চকিতে মনে পড়ে ‘গন উইথ দ্য উইন্ড’ মুভির খামার বাড়িটার স্মৃতি। এরকম খামারেরই রেপ্লিকা গড়ে তুলেছিল ওরা আটলান্টিকের ওপারে, যেসব হারিয়ে গেছে ঝঞ্ঝা বাতাসের সঙ্গে, অথচ এখনো রয়ে গেছে ওগুলো বিলেতের অনেক গ্রামের পাশে।
ট্রেইডমার্ক করে রাখার মতো গোঁফজোড়া না থাকলে বুঝতেই পারতাম না যে কয়েক ঘণ্টা আগে এ মানুষটাকেই দেখেছি ট্রাক্টর চালিয়ে আসতে, রাস্তাটা তাহলে ঘুরে এখানে এসেছে! ধবধবে সাদা গেঞ্জি ও ব্রাউন হাফপেন্টের ভেতর পরিচ্ছন্ন একটা মানুষ, চোখের উজ্জ্বলতা অসাধারণ, কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, ভালো লেগেছে? বহুত খুব। বলেছিলাম না? বামে ছোট্ট একটা জায়গা আছে, বিশ্রাম নিতে পারো। সামনে এগিয়ে দেখি ছোট্ট একটা কান্ট্রি পাব, বেশ কয়েকজন বাইরে বসে আছে বিয়ারের গ্লাস নিয়ে। দুটো বিয়ার নিয়ে বসি আমরাও, ভেতরে ঢুকে ভাজা মাংসের গন্ধে মনে হয় খিদেও পেয়েছে। সরাসরি স্লটার হাউস থেকে তাজা মাংস নাকি ওরা নিয়ে আসে উইকেন্ডে, স্লাইস করা পর্ক সোল্ডারের দুটো প্লেইট বাইরে নিয়ে আসি, হ্যান্ডমিল ঘুরিয়ে গোলমরিচ ও রকসল্ট গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দেই, সবুজ আপেলের আচার মেখে মজা করে খাই, দ্বিতীয়বার আনতে যায় কেরোল, শেয়ার করি ওটা। বিয়ারের আমেজ ও ক্লান্তি মিলেমিশে ইচ্ছে হয় ঘুমিয়ে পড়ি। আবার দেখি ঐ ট্রেইডগোঁফের ছায়া, মনে হয় এ খামারটার মালিক অথবা ম্যানেজার সে, আমার ঢুলো ঢুলো চোখ দেখে এগিয়ে আসে, অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছো, তোমরা বোধ হয় ওখানে থাকো, যৌবনের কাল তো, অনেককিছুই বোঝা যায় না, ইচ্ছে হলে বাস ধরে ফিরে যেতে পারো, বাঁয়ের রাস্তা ধরে পাঁচ মিনিট হাঁটলে একটা বাস-স্টপ পাবে, এই ধরো আর ঘণ্টাখানেক পর একটা বাস আসবে, ওটা একেবারে তোমাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবে। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, আসলেও টায়ার্ড আমরা। কোনো অসুবিধা নেই, চকচকে বোতামের মতো ওর চোখজোড়া নাচিয়ে বলে, খুব আরামের একটা ঘুম দিতে পারবে ঘরে যেয়ে, ইশারায় কেরোলকে দেখিয়ে চোখ টিপে বলে, অবশ্য আরো আরামে রেখে তোমাকে যদি ঘুমাতে না দেয় ও। হেসে চোখ টিপি আমিও। কানে কানে বলে কেরোল, ভাগ্যিস এক বিছানায় শুতে মানা করে নি!
যদি কোনো শনিবার আওয়ার লেইডি মালকিন ভাড়া নিতে না আসতো আমরাই মাঠ পেরোতাম। এমন একদিন ওর ওখানে যেয়ে দেখি রোদে পিঠ রেখে উল বুনছে, আর মিটি মিটি হাসছে।
এই মজার বুড়ি, পেটে পেটে এতো! এই বয়সে কার জন্য সোয়েটার বুনছো শুনি?
ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে থাকে, হাসিটা তখনো মুখ জুড়ে, বলি–
হাসছো কেনো? এবার যেনো সামনে দেখতে পেয়েছে আমাদের। বলে–
হাসছি নারে ছোঁড়া, ওটা একটা স্মৃতি, এই হাসিটা আজকের না, এমন কি ওটা হাসিও না। আমিও জেরা করা শুরু করি–
তাহলে উল বুনছো কার জন্য? এবার প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে মজার বুড়ি।
তোদের ভবিষ্যতের জন্য।
খলবলিয়ে হেসে ওঠে কেরোল।
এক বিছানায় শুতে মানা করে, আবার বলে কিনা …
আমি জানি তোরা আমার কথা শুনিস না।
জানো?
পকেট হাতড়ে আট পাউন্ড বের করে দেই ওর হাতে। ব্যাগ থেকে কারুকাজ করা কাপড়ের খতি বের করে এক দুই করে গুনে রাখে ওগুলো যত্ন করে। বাস-স্টপে পৌঁছে, ওটার ছোট্ট বেঞ্চে বসে মনে মনে হাসি মজার বুড়ির কথা মনে করে। অনেক পুরোনো মনে হয় বাস-স্টপটা, কাঠের ছোট্ট একটা দোচালা, যাত্রী যে কালেভদ্রে মাত্র দু’একজন ওঠে এখান থেকে, বোঝা যায় এটার অবস্থা দেখে। বাস আসে একটা বেশ ঝকঝকে, এতো বড় বাস, পেছনে মাত্র দু’জন যাত্রী। এর গতি দেখে বাংলাদেশের মুড়ির টিনের কথা মনে পড়ে, গড়িয়ে গড়িয়ে চলা ঐ মুড়ির টিনও ফাঁকা রাস্তা পেলে ঝড়ের গতিতে দৌড় দেয়, বাংলাদেশের কোনো ড্রাইভার এমন রাস্তা আর গাড়ি পেলে বাংলাদেশ বিমান নির্ঘাত ফেইল মেরে যেতো।
বাসটার এই ধীর গতিতে চলাটাই বরং এখন ভালো লাগছে, আসল বিলেত রয়েছে বিলেতের গ্রামগুলোয়, ওদের একথাটার মর্ম বুঝতে পারি, এতো সুন্দর প্রকৃতি ও জীবন সত্যিই বিরল। মুগ্ধ হয়ে গ্রামের দৃশ্য দেখতে দেখতে তন্দ্রা নেমে আসে দু’চোখ ভরে। যেখানে নামিয়ে দেয় বাসটা, ঘরের সত্যিই খুব কাছে, ছোট্ট একটা শাওয়ার নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি, সুদীর্ঘ স্মৃতিভরা একটা দিনের শেষে।
কোনো এক শনিবারে যেয়ে দেখি আওয়ার লেইডি মালকিন দু’চোখে জল নিয়ে বাগানের কোনে একটা ফুলের দিকে তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ। জিজ্ঞেস করি, কাঁদছো কেন মজার বুড়ি? বলে এ কান্নাটাও কান্না নয় রে, অন্য আরেক ধরনের স্মৃতি। কত রকম স্মৃতি আছে তোমার মালকিন? শুনবি? হ্যাঁ, শুনবো, মাত্র এক পাউন্ড ঘণ্টায়। এই ছোঁড়া, আর ক’বার বলবো, ঐ যে মাল্টি গিল্টি কি যে ডাকিস আমাকে ওতে এক পাউন্ড কাটাকাটি। আচ্ছা ঠিক আছে, শোনাও তাহলে। এভাবে আমরাও অভ্যস্ত হয়ে যাই, যে হপ্তায় মজার বুড়ি আসে না, ধরে নেই কোনো একটা স্মৃতির ভেতর রয়েছে সে।
অক্সফোর্ডের দিনগুলো আমার আইসিস নদী তীরের প্রাচীন মেপল গাছগুলোর মতো ঝড় ও ঝঞ্ঝা এড়িয়ে, ক্ষয় ও জীর্ণতা উপেক্ষা করে বেড়ে চলে, গ্রীষ্মের রৌদ্র-দিনে নিচের শীতল ঘাসে হয়তো একটু ছায়া ফেলে, কিন্তু সেসবের কোনো চিহ্ন থাকে না ঘাসের বুকে। ওরাও নিজেদের মতো বেড়ে ওঠে, আবার শুকিয়ে যায়, আবার বেড়ে ওঠে একইভাবে, গাছগুলোর সঙ্গে সম্পর্কহীন ঐ বেড়ে ওঠা।
যতোটা জড়িয়েছি কেরোলের সঙ্গে, বলতেই পারি, প্রেমে পড়েছি, ওকে নিয়ে জীবন কাটানো যায়, একটা উদ্বাস্তু পরিবার গড়ে তোলা যায়। কিন্তু দেশে ফেলে আসা জীবনের ঐ গেরোটার বিষয়ে কি করবো ভেবে উঠতে পারি না। রশিটা বাঁধা যে খুঁটির সঙ্গে ওটা উপড়ে উঠিয়ে নিয়ে আসা যায় না, আর ঐ অসম্ভবকে কোনোভাবে সম্ভব করে ফেললেও দৌড়ে যে-কেউ আবার ধরে ফেলতে পারার সম্ভাবনা থেকে যায়, রশিটা ছেঁড়াও অসম্ভব, কোনোভাবে গেরোটা খুলে আসতে পারলে একটা কূল হয়তো হতে পারে, কিন্তু কীভাবে তা করা যেতে পারে মাথায় আসে না। চাচার মেয়েকে বিয়ে না করাটা পুরোপুরি অনৈতিক, বাবার দিকটাও অবশ্যই ভেবে দেখার মতো। চাচার অর্থ আছে, মেয়েকে অন্যত্র বিয়ে দিতে পারবে, কিন্তু বাবার গলায় দড়ি দেয়ার দশা হবে। সিদ্ধান্ত নেয়ার সময়ও ঘনিয়ে এসেছে। অকপটে সব খুলে বলি কেরোলকে।
মেয়েটার সঙ্গে তোমার কোনো কমিটমেন্ট আছে?
অবশ্যই না। যদি জিজ্ঞেস করো, ওর চেহারাটাও এখন বর্ণনা করতে পারবো না, সত্যি বলতে কি, ভালোভাবে কখনো দেখিই নি ওকে।
যদি কোনো কমিটমেন্টই না থাকে তোমার সঙ্গে তাহলে ইগনোর করতে সমস্যা কোথায়?
পারিবারিক কমিটমেন্টটা তো কোনোভাবে উপেক্ষা করার মতো না। ওদের অর্থে পড়াশোনা করেছি, এতোটুকু এসেছি, বেঈমানি করবো কীভাবে, বলো?
হ্যাঁ, অবশ্যই ওটা গুরুত্বপূর্ণ …।
চুপ করে থাকে কেরোল, কী যেনো ভাবে, কিছুক্ষণ পর বলে–
বুঝি না, কীভাবে একটা অজানা অচেনা মানুষের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধো তোমরা!
এভাবেই হয়ে এসেছে আমাদের সমাজে। খুব যে অসুবিধা হয়, তাও না।
ভবিষ্যত নিয়ে এক ধরনের জুয়া।
হয়তো। কিন্তু পাশ্চাত্যে যে এতো চেনা-জানার পর ঘটে এসব, তাতেও তো কম ভাঙ্গাভাঙ্গি হয় না।
সম্পর্কের এডজাস্টমেন্টটা আসলে খুব জটিল।
হ্যাঁ, জটিল।
তোমার ক্ষেত্রে অর্থই যদি মূল বিষয় হয়ে থাকে, তাহলে কম্পেসেট করে সমস্যা সমাধানের দিকে এগোনো যায় না?
ভালো একটা ক্লু বের করেছো, কেরোল।
কত টাকা লাগতে পারে?
অনেক, নিঃসন্দেহে অনেক।
এক কাজ করো, পড়াশোনাটা শেষ করে, চোখ বন্ধ করে চাকরি করতে থাকো, আর বাড়তি খরচ না করে টাকা জমাও।
তার আগে দেশে যেয়ে বিষয়টা মীমাংসা করে আসতে হবে।
তাই করো, আর দু’বছরের জন্য সব আমোদফুর্তি বাদ দাও।
তোমার সঙ্গে শোয়াও!
ডাউ, তোমাকে আসলেও জরিমানা করা উচিত, এক পাউন্ড নয়, দু’পাউন্ড করে।
তাই করো নাহয়, তবু ঐ মজার বুড়ির বুদ্ধিটা নিও না।
আর একটা কথা বলেছো তো তিন পাউন্ড করে জরিমানা।
অভাবনীয় একটা ঘটনা পালের রশি ছিঁড়ে, মাস্তুল ভেঙ্গে নৌকোটা ডোবানোর উপক্রম করে। অক্সফোর্ডের ঝড়োগতি জীবনে যা-কিছু করে থাকি না কেনো, পড়াশোনায় ঢিল দেই নি একটুও। কারণ, জানি যে এটা আমার অর্জনে তো নেইই, এমনকি বাবারও না। এ পর্যন্ত প্রতিটা টার্মে ও এসাইনমেন্টে এ গ্রেইড পেয়ে এসেছি, অথচ চূড়ান্তে এসে আমার থিসিসটা গ্রহণ করেন নি মহাত্মা প্রোফেসর! কারণ জিজ্ঞেস করি। বলে, সে তো রিফিউজাল লেটারে লেখাই আছে।
তাহলে এতো বছর এ গ্রেইড পেয়ে এসেছি কীভাবে?
ওসব ভিন্ন। থিসিসের সঙ্গে ওগুলোর সম্পর্ক নেই।
ভালো করছো ভালো করছো শুনে শুনে বোকার স্বর্গে বাস করে এসেছি দেখছি!
ওটা হয়তো তোমার ধারণা। বোকারা নিজেরাই ওটা রচনা করে।
হ্যাঁ, ভুলের জগতটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, আমাকেই!
মনটা আমার ছুতোরের, ধরো তক্তা, স্বর্ণকারের মতো ঠুকঠুক ভালো লাগে না, কামারের মতো এক ঘায়ে বসিয়ে দিতে ইচ্ছে হয় সব কিছু। একই কাজ দ্বিতীয়বার করতে হবে ভেবে মন খারাপ হয়। একটা বছর যে পিছিয়ে গেলাম, তাই শুধু নয়, জীবনের হিসেবটাই বদলাতে হবে এখন। আমার অবস্থা দেখে এগিয়ে আসে কেরোল।
ভেঙ্গে পড়ার মতো কিছু হয় নি ডাউ। সব ঠিক হয়ে যাবে আবার।
বলছো?
হ্যাঁ, আমার এক বছরের সঞ্চয় ধার দেবো, বিষয়টা মিটিয়ে এসো, তারপর আর কি?
তাহলে শুধু ঋণ করেই জীবনটা গড়ে তুলতে হবে আমার!
ওভাবে দেখো না, আমারও ঋণ নিতে হতে পারে তোমার কাছ থেকে, বিষয়টা সামলানোই বড় কথা।
পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর ঘন ঘন চিঠি আসতে থাকে দেশ থেকে। যাওয়ার উপায় নেই জানিয়ে লিখি যে পড়াশোনা শেষ করার জন্য ধার-দেনা হয়েছে, ওসব শোধ করতে আরো দু’বছর লাগবে। একে তো আসা-যাওয়ার খরচ, তারপর পকেট ভর্তি না করে তো আর দেশে ফেরা যায় না। যুক্তিটা শাঁসালো বুঝতে পেরে ক্ষান্ত দেয় বাবা। দুটো বছর অন্তত হাতে পেয়েছি, দেখা যাক, ভবি কি বলে!
উইকেন্ডে দেরিতে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাসটা গড়ে ওঠেছে বিলেতে আসার পর। কেরোল বোঝে নি যে আমার ঘুম ভেঙ্গেছে, জানালার ধারে চেয়ার টেনে নিঃশব্দে কাঁদছে বসে! চোখ বন্ধ করে ফেলি সঙ্গে সঙ্গে, মনে মনে একটু অবাক হই। কোনো কারণে আঘাত দেয়ার মতো ঘটনা আমার দিক থেকে হয় নি তো? কিছুই ভেবে পাই না। দ্বিধা ঝেড়ে উঠে পড়ি, যেয়ে বসি ওর পাশে।
ইস্টার পর্বের আগে দোকানের অনেকগুলো তাক যখন ইস্টার এগে ভরে যায়। ভাইবোনেরা, কাজিনেরা মিলে বড়দের সঙ্গে দোকানে যাই। সবরকম ডিম থেকে অন্তত এক বাক্স করে চাই আমাদের। বড় দিনের বিশাল আনন্দের পর ওটা একটা বড় উৎসব। সেবার মাটি হয়ে যায় ওটা পরিবারে ঘটে যাওয়া বড় একটা দুর্ঘটনায়। জীবনে প্রথম মৃত মানুষ দেখি, তাও আমার সমবয়েসী, একটা বাচ্চা। সকালেও যে আনন্দে লাফিয়েছে, ইস্টার এগের সংগ্রহটা দেখিয়েছে, একটা বাক্সে মুখও খোলে নি ইস্টারের দিন খাবে বলে, বিকেলেই সে প্রাণহীন! মৃত্যুর মহিমা তখনো বুঝি নি ওভাবে। আমাদের গ্রামে তো গেছো তুমি, এখনই বা ক’টা মানুষ আছে সেখানে, আর এতো বছর আগে, ভাবতেই পারো। গ্রামের বড় রাস্তাটা দিয়ে কখনো একদু’টা গাড়ি চলাচল করতো, আমাদের ঘরের একেবারে সামনে, দু’শ গজও হবে না, একটা বাঁকে যখন পৌঁছি, পেছনে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ শুনি, মাথা ঘোরাতেই দেখি আমাকে ধাক্কা মেরে নিজেও ছিটকে পড়েছে ও, লুটিয়ে পড়ি রাস্তার পাশে, কিছু হয় নি আমার, কিন্তু ও যে ধাক্কাটা খেয়েছিল, ওটা গাড়ির। একটা বাচ্চা শরীরের কতটুকুই বা আর ঝাঁকুনি খাওয়ার ক্ষমতা থাকে বলো? এর পরে আরো অনেক মৃত্যু দেখেছি, কিন্তু ওটা আজীবন রয়ে যাবে আমার সঙ্গে। আমাদের দু’জনকেই এ্যাম্বুলেন্সে করে সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যায়, ওটাই ছিল সবচেয়ে কাছে, কোনো কাজে আসে নি, ওর আঘাতটা ছিল শরীরের ভেতরে। এখন মনে হয়, আমারটা ছিল অন্তরের ভেতর! ওর ঐ ছোট্ট কফিনটা সাদা একটা পাথরের মতো চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়, যেনো একটা জ্যান্ত অস্তিত্ব।
সেজন্যই বুঝি একা একা কাঁদছো এখন?
হ্যাঁ, ঐ যে, মজার বুড়ি বলে না, এ কান্নাটা এ কান্না না, অন্য কোনো কান্না।
আসলে যে কান্না আমরা দেখি তার কোনোটাই ঐ কান্না না, আসল কান্নাটা কেউ দেখতে পায় না।
সত্যি তাই, সত্যি। চলো উঠি। তোমার মন খারাপ করে দিলাম না তো?
কি যে বলো!
দেখো, কত দিনের পুরোনো কথা, সতেরো বছর আগে যখন আঘাতটা এসেছিল, চোখে এক ফোঁটা জলও আসে নি, কত বয়স তখন আমার, সাত বছর! আর এখন, এতো বছর পর কান্না পেয়েছে, হাসির মতো মনে হয় না?
না কেরোল, হাসির মতো মনে হয় না। ওর কোনো ছবি আছে তোমার কাছে?
আছে, বুকের ভেতর। বেঁচে থাকলে হয়তো ওর সঙ্গেই আমার ভালোবাসা হতো।
এবার হাসে কেরোল।
কি সব বলছি!
সেক্ষেত্রে তোমাকে পেতাম না আমি। তারপরেও ওর বেঁচে থাকাটাই কামনা করতাম।
যাকগে, যা নেই, তা নিয়ে কেঁদে কি লাভ বলো, শুধু শুধু মন খারাপ করা।
যা আছে তা নিয়ে এবার একটু হাসো না কেরোল।
ওহ, একটা অসহ্য তুমি, ডাউ!
যদি তোমার কাজিন হতাম, কেরোল!
দেখো দেখি, ব্যাপারটা কি মজার, কাজিন থেকে নিষ্কৃতি চাইছো তুমি, আর আমি কাঁদছি আমার কাজিনের জন্য!
এই, এক কাজ করা যায় না, মজার বুড়ির মতো কাটাকাটি?
না, যায় না, তাহলে তো তোমার কাজিন শুরুতেই বিধবা।
আরে, ওভাবে তো ভেবে দেখি নি। থাক কাটাকাটি না, জোড়-বাঁধা।
হ্যাঁ, জোড়-বাঁধা।
পাঞ্জা ওঠায় কেরোল, আমিও পাঞ্জা উঠিয়ে পট্টাস করি।
এক শনিবারে এক দুই করে পাউন্ডগুলো গুনে নেয়ার পর বলে মজার বুড়ি–
বিকেলে এক জায়গায় যাবি আমার সঙ্গে?
কেরোল বলে, হ্যাঁ যাবো।
না, তুই না, ঐ ছোঁড়া শুধু। আমার দিকে ফিরে চোখ ইশারা করে। বিকেলে এসে হাজির যখন, দু’জনেই অবাক, নাচের কালো পোশাক, মাথায় টিউলিপ-গোঁজা বাহারি টুপি, ঠোঁটে লাল টুকটুকে লিপস্টিক, সুগন্ধি ছড়ানো বাতাস!
কীরে, খুব যে অবাক দেখছি?
কেরোল বলে, না ভাবছি, আমরা কি পোশাক পরবো, তোমাকে দেখে বুঝতে পারছি না।
আবার বলছিস আমরা! একটা নাচের পার্টিতে নিমন্ত্রণ আছে আমার, ও যাবে নাচের সঙ্গী হয়ে, তুই যাবি কি করতে?
আহা, আসুক না মালকিন, বলি আমি।
কপট রাগ দেখিয়ে বলে কেরোল, আমার মানুষটাকে নিয়ে টানাটানি করছো কেন লেইডি? সামলাতে পারবে?
কেনো, খুব তেজ নাকি? কীভাবে বুঝলি, তোরা কি একসঙ্গে শোয়া…
ওকে থামিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বলি, না, না, মালকিন, কখনোই না, তবে এখন সঙ্গে আসতে পারে ও।
আমরা নাহয় নাচবো, ও কি করবে?
সে দেখা যাবে, নাচঘরে গেলে সঙ্গী একজন জুটিয়ে নিতে পারবে আশা করি।
সাহস তো মন্দ নয় তোর ছোঁড়া, ঐ ছেঁমড়ি যদি ওর সঙ্গে ঝুলে পড়ে?
তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে ঝুলে পড়বো।
ওও, গ্র্যান্ড! আয় তোকে একটা চুমো দেই।
তেড়ে আসে কেরোল, না, দিতে হবে না।
ওরে বাব্বা, ঠিক আছে, দেখা যাবে, কতো কঠিন গেরো। এখন কষ্ট করে মাঠটা পেরিয়ে আমার বাসার সামনে আয়, ওখানে গাড়ি আসবে চারটায়।
ঠিক আছে মজার বুড়ি, বলে হাত নাড়ি।
সাজগোজ ও পোশাক মনের উপর কতোটা প্রতিক্রিয়া করে বুঝতে পারি। গটগটিয়ে হেঁটে যায় বুড়ি, বয়স যেনো দশ বছর কমে গেছে, চপল ছন্দ এসেছে শরীরে।
গ্রীষ্মের শেষে, অথবা কোনো গ্রীষ্ম প্রলম্বিত হলে, গোলাপের একটা কি দুটো ডাল দু’একটা অতিরিক্ত ফুল ফোটায়। মজার বুড়ির প্রতিবেশীকে দেখি খুব যত্ন নিয়ে হলুদ গোলাপের একটা ডাল বাঁশের কঞ্চিতে বেঁধে দিচ্ছে। জানি না বাঁশের কঞ্চি এখানে আসে কোন দেশ থেকে, এদেশে তো কোথাও বাঁশ জন্মাতে দেখি নি! ভাগ্যিস! বিভিন্ন সাইজের কঞ্চির তোড়া কিনতে পাওয়া যায় ডিআইওয়াই সেন্টারে। হয়তো আগামীকাল অথবা পরশুই ঝরে যাবে ফুল দুটো, ওটা টিকিয়ে রাখতে কম করে হলেও এক ঘণ্টা ব্যয় করবে বুড়োবুড়ি। এজন্য আবার ঘরের পোশাকও পরিবর্তন করতে হয়েছে, পুরোনো দিনের ইংরেজরা এতো ফর্মাল, এক মিনিটের জন্যও ঘরের পোশাকে বাইরে বেরোয় না, অথচ এখনকার তরুণদের ঘরের ও বাইরের পোশাকের পার্থক্যই বোধ হয় উঠে গেছে। ট্রাউজার ও শার্টের উপর সোয়েট-শার্ট চাপানো বুড়োর, আর জুতো মোজা, বুড়ির পরনে ফুল-হাতা শার্ট ও লম্বা ঝুলের স্কার্ট। সামান্য এই কাজের জন্য হাতে গ্লাভস দু’জনেরই, বুড়ির হাতে প্রুনার, দু’একটা অতিরিক্ত ডাল ছেঁটে দেয়। চুপচাপ যার যার কাজ করে, বাংলোর সামনে এরকম বুড়োবুড়ি প্রায়ই দেখা যায়, বাগানের কাজ করে, নয়তো দরোজা জানালার কাচ পরিষ্কার করে, সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তাকালে অবশ্যই হ্যালো বলবে। জবাবে একটা কথা বেশি বললে, দুটো অতিরিক্ত কথা বলবে।
গুড ইভনিং।
গুড ইভনিং, গুড ইভনিং।
নাইস ওয়েদা’!
ও ইয়া, নাইস ওয়েদা’ ফ’ গার্ডেনিং।
ভেরি নাইস। হ্যাভ এ নাইস ডে।
থ্যাঙ্ক ইউ জেন্টলম্যান, বা-আই।
বা-আ-ই!
পথচারীর সঙ্গে এটুকু কথা বলায়ই যেনো টক-মেশিনটা স্টার্ট হয়ে যায়, শুরু করে নিজেদের মধ্যে কথা বলা, এতোক্ষণ কাজ করছিল চুপচাপ!
বাড়ির সামনে চকচকে কালো রঙের অনেক দামি ও বিশাল এক গাড়ি দেখে কেরোলের চোখ কপালে ওঠে। কাছে আসতেই মজার বুড়ি বেরিয়ে আসে গট গট করে। হ্যালো, আওয়ার লেইডি মালকিন। হ্যালো কিডস। বিলেতে আসার পর এই প্রথম, অথবা বিলেতে আসার পরই বা বলি কেন, জীবনে এই প্রথম এতো দামি গাড়িতে চড়েছি। যখন চলা শুরু করে, মনে হয় ভেতরে বসে চা-কফিও খাওয়া যাবে। তারপর সেই গাড়ি এলো তো এলো আবার ঐ এলোর ঘরে! কান্ট্রি পাবটার পাশ দিয়ে মূল বাড়ির ভেতরে যখন গাড়ি ঢোকে বুঝতে পারি বিলেতের বনেদি ধনীরা কত ধনী। নাইটদের ক্যাসল, এবি, এসবের পরই বোধ হয় বিলেতের লর্ডদের আবাসগুলো, তারপরই এই ধনীক শ্রেণি।
এগিয়ে এসে মজার বুড়িকে চুমো খায় ঐ ট্রেইডমার্ক গোঁফ! আমাদের দিকে ফিরে বলে–
হ্যালো গাইজ।
আমরাও হ্যালো বলে হ্যান্ডসেইক করি।
অবাক হচ্ছো, না? ও আমার আন্টি। তোমাদের কথা প্রায়ই বলে, বেশ ভালো ভাড়াটে নাকি তোমরা, অনেক শর্তটর্ত মেনেও ওখানে রয়েছো কয়েক বছর ধরে, বলেই চোখ টিপে, আমার আন্টি কিন্তু খুব মজার মানুষ।
জানি, মাই ফ্রেইন্ড।
আমার নাম পিটার।
নাইস টু মিট ইউ পিটার, একটু থেমে বলি, পিটার দ্য গ্রেট!
গোঁফে ঝড় তুলে হাসে, না হে, পিটার দ্য গ্রেটদের ভগবান একটা করেই বানায়, এতো এতো গ্রেট বানালে পৃথিবীটাই তো গ্রেট হয়ে যেতো!
যা বলেছো। ও হ্যাঁ, আমার নাম ডেয়ুড, আমার বান্ধবী কেরোল।
হ্যালো কেরোল।
অক্সফোর্ডের কানের এতো কাছে গ্রামটা, মনে হয় ফিসফিসিয়ে কথা বলছে ওরা। পিটারদের মূল বাড়িটা পাহাড়ের চূড়ায়, আশেপাশের পাহাড়গুলোয় মনে হয় না কোনো বসতি আছে। ছক কাটা ফসল খেত, মাঝে মাঝে এক থোক বড় গাছের গলাগলি দাঁড়িয়ে থাকা, পাহাড়ের পর পাহাড়, দূর থেকে সবই ফাঁকা মনে হয়, হয়তো ফসল খেত ছিল এক সময়, বিলেতের অনেক খামার পতিত পড়ে রয়েছে এখন, চাষাবাদে লাভ নেই তেমন, খামারিদেরও আগ্রহ নেই। পাহাড়গুলো যদিও অনেক উঁচু, কিন্তু কোনোটাই খাড়া নয়, অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত, কোনো পাহাড়ের ঢালই দশ থেকে পনেরো ডিগ্রির বেশি না, ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া যায় যেদিকে খুশি। কোনো কোনো পাহাড় দু’ভাগ করে ফেলেছে একটা পথ ও পথের দু’পাশে যত্নে লাগানো হথর্নের ঝোপ। এখানে এতো সোজা উঠে গেছে ঝোপের সারি দুটো, আর যে-রকম সমান করে সুন্দরভাবে ছাঁটা, মনে হয় সবুজ একটা রেল লাইন উঠে গেছে পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত, মাঝখানের সরু পথটা এখান থেকে সরু মনে হলেও বড় একটা ট্রাক্টর অনায়াসে আসা যাওয়া করতে পারে। পাহাড়ের ঢালে, নিচের অংশে বলদের খামার একটা, হাতির মতো বিশাল ঐ বলদগুলো পাল্লা দিয়ে নিজেদের তাগড়া করে তোলে দ্রুত কসাইখানায় যাওয়ার জন্য। বাড়ির লাগোয়া একটা ঘোড়ার আস্তাবল, বোঝা যায় এক সময় অনেক ঘোড়া থাকতো ওখানে, পরিবারের সবারই কম করে একটা, এখন মাত্র এক, দু, তিনটা দেখি, যার একটা মনে হয় না কখনো ব্যবহার করা হয়। লেজ, ঘাড়ের না-ছাঁটা কেশর, ও শরীরের লোমে এখন আর ব্রাশ পড়ে বলে মনে হয় না। আস্তাবলের পাশে যেয়ে দাঁড়ালে পাহাড়সারিটা আড়াআড়ি দেখা যায়, ছক কাটা সবুজ, হলুদ, মেটে রং পাহাড়ের শরীর ছুঁয়ে দৃষ্টি উঠে যায় আকাশে, স্পষ্ট বোঝা যায় ‘স্কাই লাইন’ শব্দযুগলের অর্থ ও বিশেষত্ব। সবুজ ও নীলের পার্থক্য সূক্ষ্ন একটা দাগের মধ্যে দিয়ে এতো স্পষ্ট যে ওখানে একটা মানুষ কেন, ইঁদুর উঁকি দিলেও বোঝা যাবে যে স্কাই লাইনটা ভাঙ্গা হয়েছে। কান্ট্রি পাবের পাশ দিয়ে হেঁটে একটু এগোলে স্ট্রবেরির আবাদ। মাটি থেকে ফুট দুয়েক উঁচুতে মাচা বেঁধে সারি সারি স্ট্রবেরি লাগানো। উইকেন্ডে স্ট্রবেরি পিকিং সেইলে দেয়া হয়। এসে যতো খুশি খেয়ে যাও, তুলে নাও নিজের হাতে, যাওয়ার সময় সেইলস কর্ণারে মেপে পয়সা দিয়ে যাও। রোদ পোহাতে ও তাজা স্ট্রবেরি খেতে আসে অনেকে। মাছের পুকুর আছে বেশ ক’টা, বড়শি ফেলে মাছ ধরে কিনে নেয়া যায় যতো খুশি। হাস মুরগির খামার থেকে বায়ো এগ ও চিকেন কিনে নেয়া যায়।
বনেদি বিলেতি পরিবারগুলো আর কয়েক দশক টিকে থাকবে কিনা কে জানে, এই পরিবারে পিটারই বোধ হয় শেষ খামারি। ওর দু’ছেলের একজন ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে এখন অস্ট্রেলিয়ায় চাকরি করে, মনে হয় না ফিরে আসবে আর, দ্বিতীয়টা ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। খামার চালানোর জন্য, দেখভালের জন্য শ্রমিকও পাওয়া যায় না, শহরের কারখানায় অথবা ওয়্যারহাউসের কাজে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে এই জেনারেশন। বিলেতে প্রত্যন্ত অঞ্চল বলেও কিছু নেই যে পুরোনো দিনগুলো আরো কিছুদিন রয়ে যাবে, বিচ্ছিন্ন কোনো গ্রাম বা শহর নেই, প্রতিটাই অন্যান্য গ্রাম অথবা শহর ও নগরের সঙ্গে যুক্ত, এমনকি ছোট ছোট চ্যানেল আয়ল্যান্ডগুলোও এখন আর বিচ্ছিন্ন বলা যায় না, দিন রাত চবি্বশ ঘণ্টাই কোনো না কোনোভাবে যাতায়াত করা যায় ওসবে।
কেন যে প্রকৃতি এভাবে আপ্লুত করে আমাকে! হোক না বিদেশ, তবুও মনে হয় না এ আমার পর, যেমন প্রকৃতি কাউকে পর মনে করে না। এখানে, এই স্ট্রবেরি বাগানের পাশে আমাদের ফুলবাড়ির সিমের গাছ লাগালে প্রকৃতি আমাকে নিষেধ করবে না, সাধ্য-মতো চেষ্টা করবে গাছে প্রাণ দিতে, সাদা ও বেগুনি ফুল ফোটাতে, আর রানিং বিনের মতো লম্বা লম্বা ঘিয়া-সিম জন্মাতে। অথবা এখানে ঘর বাঁধলে কি বলবে উঠিয়ে নাও, অথবা বেঁধো না। বলবে মানুষেরা, বাঁধা দেবে মানুষেরা, যারা সব কিছু নিজের করে পেতে চায়। সবুজ ঘাস, সবুজ ঝোপ ও সবুজ গাছপালা মন এতো সতেজ করে তোলে! পুরোনো দিনের বাতাসও জমে আছে বনের ভেতর, বুক ভরে নেয়া যায় আদিগন্ধ মেশানো সবুজ বাতাস, কেরোলকে বলি, এতো সবুজ, এতো সবুজ, কেরোল, সহ্য হয় না, নিজেরও ইচ্ছে হয় সবুজ হয়ে যেতে।
তোমাদের দেশটাও তো সবুজ।
হ্যাঁ, সবুজ, চির সবুজ। কখনো তুষারে ঢেকে সাদা হয় না।
আয়ারল্যান্ডে, আমাদের অংশের সবুজ বড় নিষ্ঠুর।
নিষ্ঠুর সবুজ? বুঝি নি কেরোল।
গ্রীষ্মের কয়েকটা মাস এতো সবুজ যে তার চেয়ে বেশি সবুজ আর পৃথিবীতেই নেই, চোখ জুড়াতে না জুড়াতে হলুদ লাল ধূসর, তারপর সব সাদা, সব সাদা।
ও, তাই বলো!
বাড়িটার ডান দিক থেকে অক্সফোর্ডের গির্জার চূড়োটাই শুধু দেখা যায়। বিলেতেই শুধু নয়, ইউরোপের কোনো শহর অথবা নগরের স্কাই-লাইনে গির্জার চূড়া নেই, এমনটা ভাবা যায় না। গির্জা ও পুরোনো ভবনগুলোর বাইরের ও ভেতরের দেয়াল, থাম ও খিলানে পাথরের যে কার্ভিং, কারুকাজ তাও থেমে গেছে অনেক বছর আগে। পাথর কুঁদে ভবনের সৌন্দর্য বাড়ানো মধ্যযুগের শিল্প, যুগ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ঐ শিল্পও শেষ হয়ে গেছে। চার তলা একটা ভবন নির্মাণ করতে এখন এক বছরও লাগে না, অথচ এসব অনেক গির্জা গড়ে ওঠেছে কয়েক প্রজন্মের পরিশ্রমের ফলে। যে টেরাস-ব্লকে আমরা থাকি, তা নতুনদিনের নির্মাণ, ওটার বাইরের দেয়াল দুটো করে। দুই দেয়ালের মাঝে ফাঁকা, ইনসুলেশান রয়েছে, বাইরে থেকে বোঝা যায় না যে দুটো দেয়াল, ছাদেও ইনসুলেশান রয়েছে, কোনো চিমনি নেই, সেন্ট্রাল হিটিং, দরজার পাল্লা ও জানালার শার্সির মাঝখানেও ফাঁকা, দুটো করে কাচের ডাবল গ্লেইজিং, ঘরের উষ্ণতা কোনো ফাঁক গলিয়ে যেনো বাইরে বেরোতে না পারে, এয়ার টাইট। এর ভেতরে অক্সিজেনের অভাব হয় না কেন বুঝি না, বাতাস চলাচল করে না এমন ঘরবাড়ির কথা মনে হলে বাংলাদেশে দমবন্ধ হয়ে মরে যাওয়ার কথা মনে হবে!
একেবারে নিভে যাওয়ার আগে সম্পন্ন এই গৃহস্থবাড়িটার ম্লান হয়ে আসা জৌলুস আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় অতীতে, আমার গ্রামের বাড়িতে, শৈশবের দিনগুলোয়। গ্রামের বাড়ি হিসেবে ওটাকে নিষপ্রভ বলা যায় না কিছুতেই, গ্রামের সম্পন্ন পরিবারের মধ্যে গণ্য হতো আমাদের জ্ঞাতি-পরিবারকুল । কয়েক একর জমির উপর যে বাড়ি দাদার আমলে গড়া হয়েছিল শরিকদের মধ্যে ভাগ হয়ে তা এতোটুকু করে হয়ে যায় দ্বিতীয় প্রজন্মে এসেই, বিলেতে যা একই রকম থেকে যায় প্রজন্মান্তরে। সামনে ও পেছনে এজমালি পুকুর। সামনেরটা বিশাল, পাকা ঘাঁট বাঁধানো, আমাদের সময়ে এসে পলেস্তারা খসে ইট বেরিয়ে লাল রঙের হয়ে পড়ে ওটা। বর্ষায় পানির নিচে তলিয়ে যায় ইটের গাঁথুনির যে সব অংশ ওগুলোর সুরকি ধুয়ে প্রতিটা ইট পৃথক হয়ে পড়েছে, তেচোকো মাছেরা লুকিয়ে থাকে ঐ সব ফাঁদের ভেতর। খেলার ছলে গামছা দিয়ে ছেঁকে ঐসব মাছ ধরেছি কতো! তারপর পানি রাখার ঘটিতে জিইয়ে রেখেছি, অনেক সময় মাটিতে ছোট গর্ত করে পানি জমিয়ে মাছগুলো ছেড়ে রাখতাম, পরে হয়তো এসে দেখতাম মাটি পানি শুষে নেয়ায় মাছগুলো সব মরে গেছে। মানুষের খাওয়ার যোগ্য ছিল না তেচোকো মাছ, পুকুরের সৌন্দর্য, তেচোকো মাছ মনে হয় না বাংলাদেশে কোথাও আছে আর। পুকুরের চারটা পাড় জুড়ে ছিল বিভিন্ন রকম ফলের গাছ। আম, জাম, কাঁঠাল, খেজুর ও তাল গাছ। পুকুর ও বাড়ির মাঝখানের খোলা অংশে একটা বকুল গাছ ও দুটো গাব গাছ ছিল। যখন বকুল ফুল ফুটতো পুকুর পাড় থেকে অনেক রাতেও ঘরে ফিরতে ইচ্ছে হতো না। পাকা লাল বকুলের কষটে স্বাদ মনে হয় কষ্ট করেই নিতে হতো, তারপরও কীসের আকর্ষণে যে অমৃতের মতো মনে করে ঐ স্বাদ নিতাম! পাকা গাবের স্বাদও ছিল কষটে, কখনোই ওটা খেতে পারতাম না। গাইলে ছেঁচে পাকা গাবের কষে ঘরে বোনা জালে রং করতো আমার বাবা-চাচারা, বর্ষাকালে ঐ সব জাল নিয়ে বিলে মাছ ধরতে যেতাম আমরাও। পুকুরের এক কোনায় একটা টাট্টি বানানো হয়েছিল যে কার খায়েসে, জানি না, আমার ইচ্ছে হতো ওটা ভেঙ্গে ফেলি। ওদিক থেকে বাতাস এলে পুকুর পাড়ে বসার আনন্দটাই মাটি হয়ে যেতো, অথচ অন্য কারো রুচিতে মনে হয় না এতোটা আঘাত করতো, নয়তো ভেঙ্গে ফেলা বা অন্য জায়গায় সরিয়ে নেয়ার কথা। জায়গার খুব একটা অভাব ছিল না আমাদের পুরোনো ঐ বাড়িটায়। পুকুরের পাশে একটা মসজিদ বানানোর জন্য কিছুটা জমি ওয়াকফ করে যান আমার দাদামশাই, আশা করি কব্বরে শুইয়া তিনি আজানের সুমধুর ঐ ধ্বনি শুনতে পান এখনো! বাড়ির পেছনের পুকুরটা ছিল শুধু মেয়েদের ব্যবহারের জন্য, ওটার চারধারেও অনেক গাছ ছিল। এজমালি পুকুর হওয়ায় সবার মুরোদ বা ইচ্ছে না থাকায় ওটার গভীরতা আর বাড়ানো হয় নি বছরের পর বছর, শীতকালে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠতো ওটা। পুকুরের মাঝখানে হয়তো এক বুক পানি থাকতো, কিন্তু কাদাপানি পেরিয়ে ওখানে যেয়ে গোছল করায় কোনো শান্তি ছিল না, সামনের পুকুর থেকে কলসি ভরে পানি এনে ঘাটে বসে গোছল করতো মেয়েরা। বর্ষায় মাছ, সাপ, ব্যাঙ সব এক সঙ্গে বাস করে, ভাবা যায় বিলেতে এমন একটা কাণ্ড!
এখন বুঝি আমাদের পরিবারটা, যে অর্থে ইউরোপে পরিবার বোঝায়, কোনো পরিবার ছিল না। জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর কারো নামের শেষাংশ একই রকম ছিল না, শেষ নাম বা পারিবারিক নামের বিষয়টাই ছিল অজানা। আরব দেশের দু’তিনটা নাম মিলিয়ে অশিক্ষিত মোল্লারা একটা নাম ঠিক করে দিতো যার আগা মাথা কিছুই নেই, এমনকি আবু জামাল বা জামালের উট নামে আমার এক কাজিনের নাম রাখা হয়েছিল, আমার নামের অর্থ আমি জানি না।
শরিকদের মধ্যে ভাগ হয়ে বড় বাড়িটা টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও দেয়াল তুলে বা বেড়া দিয়ে পৃথক করা হয় নি কখনো, বাড়ির চারদিকের সীমানায় গাছ পুঁতে যদিও পৃথকীকরণের চিহ্ন রাখা হয়েছিল, সেসব গাছও এখন অনেক বড় হয়ে উঠেছে। টাকা পয়সার টানাটানি না থাকলেও কোনো উদ্বৃত্ত ছিল না আমার বাবার, ওসবের প্রয়োজনও বোধ করেননি কখনো। আঙিনায় একটা বেগুন খেত করে, কিংবা মাচায় কিছু পুঁইশাক, লাউ-কুমড়া ফলিয়ে, জাল ছুঁড়ে মাছ ধরে, দিনান্তের খাবারের পর তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতে পারতেন। তিনিই কিনা পরে স্বপ্ন দেখেছিলেন আমাকে নিয়ে, যেনো একটা সুখী সংসার গড়ে তুলতে পারি। নিজের জন্য কোনো স্বপ্ন তাঁর ছিল না, সত্যি বলতে কি তথাকথিত ঐ সুখী হওয়ার স্বপ্ন আমিও দেখি না। এই সুখ মানে হয়তো বিত্তবান হওয়া, আমার ধাতে নেই ওটা, ইউরোপের যে পরিবার প্রথা, তা গড়ে ওঠার সুযোগও হয় নি আমাদের ওখানে। কৌম সমাজ বা সংস্কৃতি গড়ে ওঠার জন্য নির্দিষ্ট কোনো স্থানে শত শত বছর অনেক কটা প্রজন্মের বাস করতে হয়, তা হয়ে ওঠে নি। অনবরত ঠাঁইনাড়া হতে হয়েছে মানুষগুলোকে, ফলে মানুষের প্রত্যাশা নিজের সন্তানের বাইরে যেতে পারে নি, কামনা করেছে, ‘আমার সন্তান যেনো থাকে দুধে ভাতে’, ঐ পর্যন্তই! এর বাইরে দেখার মতো দূরদৃষ্টি গড়ে ওঠার সুযোগই আসে নি।
প্রাচীন একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে গা ছম ছম করে, কয়েকশ’ বছরের পুরোনো তো হবেই গাছটা, এটার বেড় কতটুকু হবে, কীভাবে বোঝাই, বেড় না বলে ব্যাস বলি, দশ ফুট তো হবেই, উঁচু কত দেখতে হলে মাথা থেকে টুপি পড়ে যাবে, অথচ পুরোনো কোনো গাছই নেই এখন আমাদের বাড়িতে। বিশাল কড়ই গাছগুলো শৈশবেই দেখেছি কেটে বিক্রি করে দিয়েছে। পুকুর পাড়েও ওরকম পুরোনো গাছ নেই। প্রয়োজন কোনো কিছুরই ধার ধারে না, নিজে বাঁচলে বাপের নাম, তারপরে না নাতি পুতি।
পুরো বাড়িটা ঘুরে দেখতে প্রায় এক ঘণ্টা লেগে যায়, এর মধ্যে ছোট্ট একটা অতীত-ভ্রমণও হয়ে গেছে। বাড়ির সামনে এসে দেখি চত্বরে দাঁড়িয়ে রয়েছে পিটার। জিজ্ঞেস করে–
কেমন লাগলো? দু’জনেই একসঙ্গে বলি–
চমৎকার! নিজেদের দিকে ঘুরে তাকিয়ে হেসে উঠি। পিটার বলে–
চলো বলরুমে যাই।
কোনো অনুষ্ঠান আছে নাকি?
তেমন কিছু নেই, নিজেরাই একসঙ্গে একটু গল্প-গুজব করা। আন্টির জন্ম দিন আজ, আমন্ত্রিত শুধু তোমরাই। কেন, বলে নি তোমাদের?
দেখেছো মালকিনের কাণ্ড!
কি বললে? পিটারের দিকে ফিরে বলি–
না ওটা একটা কৌডওয়ার্ড।
ও আচ্ছা, বলে মিটিমিটি হাসে। কেরোল বলে–
মজার বুড়ি সব সময়ই ওরকম একটা করে কাণ্ড করে, দেখো তো, একটা গিফট কেনা দরকার ছিল না?
ও যে কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পারি নি।
গিফট দিবি জানলে তো আগে জানাতাম। দু’জনেই ঘুরে দাঁড়াই। চকচক করছে ওর চোখ দুটো।
দে, কি দিবি। দু’জনে জড়িয়ে ধরে দু’দিক থেকে দুটো চুমো দেই। চোখ মুদে থাকে মজার বুড়ি।
এর চেয়ে বড় আর কোনো গিফট হতে পারে না রে! আমি খুশি, খুব খুশি।
তাহলে আওয়ার লেইডি মালকিন, আজ থেকে একসঙ্গে…
তেড়ে ওঠে বুড়ি–
খবরদার, ও কথা মুখে আনবি না, আমার ভাড়ার শর্ত এক চুল এদিক সেদিক হবে না।
গলা ফাটিয়ে হেসে উঠি সবাই।
নাচঘরটা সাধারণ। সে-তুলনায় আমাদের পুরোনো জমিদার বাড়িগুলোর জলসাঘরে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসার জন্য সামান্য উঁচু মঞ্চ, প্রকাণ্ড সব ঝাড়বাতি, বহুবর্ণিল গালিচা, বাদকদলের সরোদ, এস্রাজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র, ধূপ ধোঁয়া, সব মিলিয়ে যে মাদকতাময় পরিবেশ গড়ে তোলে, তা যেনো আসে না। ওদের বিশাল অর্গ্যানটা অবশ্য দেখার মতো, কেরোলের সঙ্গে নাচার আগে মজার বুড়ির সঙ্গে এক পাক ধীর লয়ের পোল্কা নেচে নেই। পরে যখন দ্রুত লয়ের ভাল্জ নাচার পালা আসে, কেরোলকে ছেড়ে দেই। দ্রুত লয়ের নাচ এখনো রপ্ত করতে পারি নি, কেরোলের সঙ্গে পা মেলাতে যেয়ে মাঝে মাঝে হোঁচট খাওয়ার অবস্থা হয়। পিটারের সঙ্গে বেশ ভালো নাচলো কেরোল।
নাচের এই সময়গুলোতে সংগীতের মানসিক ও শারীরিক প্রভাব মনকে ধুয়ে মুছে কলুষমুক্ত করে দেয়, স্নানে যেরকম দেহসুদ্ধি, সংগীত তেমনি মনের কালিমা মুছিয়ে দেয়, অনেক দুঃখভারও লাঘব হয়ে যায়, মনের পাষাণ সংগীতের তালে তালে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। আমাদের সমাজেও এক সময় নাচ ও গান, বাদ্য ও সংগীত ছিল ধর্ম ও জীবনের সঙ্গে যুক্ত। মাঝখান থেকে তলোয়ার এসে আত্মার খণ্ডন ঘটিয়েছে, সেসব বাঁধা এখন অনেকটা শিথিল হয়ে আসছে অবশ্য। বাঙালির আত্মার প্রকৃত ধর্ম লৌকিক, মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম বাঙালির না, কৃপাণ অথবা তলোয়ার হাতে বাঙালির জন্ম হয় নি, বাধ্য করে যা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তা থেকে একদিন মুক্ত হবেই মানুষ, এর নিষ্ঠুরতাগুলো ঝেড়ে ফেলে প্রকৃত সৌন্দর্যটুকুই রাখবে শুধু।
মাঝরাতে ঘরের দরোজায় যখন নামিয়ে দিয়ে যায় আওয়ার লেইডি মালকিন, দু’জনের চোখে ক্লান্তির ঘুম। বিছানা পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ হয় না, বসার ঘরের কার্পেটে শুয়ে পড়ি দু’জনে, কোরোলের চোখ তৃষ্ণার্ত হরিণীর। বলি, বিছানায় একসঙ্গে শুতে মানা করেছে মালকিন। মেঝেতে তো না, মাদকতাময় দু’চোখ দিয়ে, মারমেইডের দু’ঠোঁট দিয়ে, দু’বাহু দিয়ে, সমগ্র শরীর ও আত্মা দিয়ে জড়িয়ে ধরে, নিঃশেষ হয়ে যাই, মিলিয়ে যাই, শূন্য হয়ে যাই!
অক্সফোর্ডের মের্টোন কলেজে এসিসট্যান্ট টিচারের একটা চাকরি পেয়েছে কেরোল। থিসিসটা আবার লেখার ফাঁকে দুটো খণ্ডকালীন চাকরি করি, যা একটা ফুল টাইমের প্রায় সমান হয়ে যায়। বছর শেষে দেশে ফিরি। বিষয়টা মেটানোই যে শুধু, তা না, পাঁচ বছরে এতো কিছু মিস করেছি, ওসবের কোনো কিছুই যেনো ফিরে পাওয়ার নয়! দেশে পৌঁছে মনে হয় ধন্য হলাম মাগো তোমার কোলে এসে! বেরিয়েছিলাম পরাধীন দেশ থেকে, ফিরে এসেছি স্বাধীন দেশে, এর আনন্দ ও আবেদনকোনোভাবে ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। এতো বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি প্রথম ক’টা দিন শুধু কাঁদতে ইচ্ছে হয়েছে। পাকি ও রাজাকারেরা মিলে কি ভয়ানক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটিয়েছে, কত মানুষ মেরে ফেলেছে, বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে।
জীবনের দাবির কাছে সবকিছুই হার মানে অবশেষে। মোটামুটি সহনীয় একটা অবস্থায় পৌঁছাই আমার চাচার মেয়ে আয়েশাকে নিয়ে। আমারই এক স্কুলবন্ধু আইনে গ্রাজুয়েশান নিয়েছে গত বছর, ভালো ভালো অনেক উপঢৌকন সহ মহকুমা শহরে ওর জন্য একটা বাড়ি কিনে দেই। ওকালতি করার জন্য একটা চেম্বার বানিয়ে, আইনের সব দামি দামি বই কিনে, বুকে পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে, বিয়ের পিঁড়িতে বসাই ওকে। চাচাও ততোটা মনোক্ষুন্ন হয় নি, প্রায় তিন বিঘা পরিমাপের খুব ভালো একটা ধানি জমি কিনে দেই ওর নামে, একই দাগের বাকি চার বিঘা জমি বাবার নামে রেজিস্ট্রি করি। মনে হয় প্রায় সবাই খুশি। চাচার মেয়ে আয়েশার মনের খবর নেয়া অবশ্য সম্ভব হয় নি। এবারই প্রথম ভালোভাবে দেখি ওকে। বেশ ভর-বাড়ন্ত হয়েছে, গায়ের রং শ্যামল হলেও দারুণ সুন্দর শ্যামল। ধারালো চোখমুখ, দেখে মনে হয় নিজেকে ভালোভাবেই প্রস্তুত করেছে গেলো ক’বছর ধরে। শাড়ির অসাধারণ প্যাঁচে বাঙালি রমণী-শরীর যে কী মোহনীয় যাদু সৃষ্টি করে, অপরূপ হয়ে ফুটে ওঠে, বুঝেছিল কবি আল মাহমুদ, রাজাকারদের খপ্পরে পড়ার আগে। এরকম একটা শরীরের জন্য গাঙের ঢেউয়ের লাহান মন ‘কবুল কবুল’ জপতেই পারে! আমার বন্ধুটিকে মনে হয় খুব ভাগ্যবান, আইনের প্যাঁচে পড়ে শাড়ির প্যাঁচ ভুলে না থাকলেই হয়!
ছুটির চারটা হপ্তা এতো দ্রুত শেষ হয়ে গেলো বুঝতেই পারি নি। প্রথমবার যখন বিলেতের উদ্দেশ্যে পা বাড়াই একটা এ্যাডভেঞ্চারের উত্তেজনা ছিল, কিন্তু এবার মনে হয় শিকড় ছিন্ন হয়ে যাওয়ার বেদনা। আমার মন বলে, এ দেশটা আর আমার, একান্তই আমার রইলো না। আসলেও থাকে নি আর!
ফিরে এসে ইউনিভার্সিটিতে যেতেই অভিনন্দন জানায় আমার প্রোফেসর। দুটো থিসিসের মধ্যে এতো পার্থক্য কীভাবে করেছিলে ডেয়ুড? অবাক হয় সে, বুঝতে পারি, খুব খুশি হয়েছে। ব্যাখ্যা করে বলি, দেখো, গেলো বছর আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশ নিতে কী ছোটাছুটিই না করতে হয়েছে, পড়াশোনা অথবা থিসিস লেখার সময় ছিল কোথায়? ওটা ছিল আমাদের বাঁচা-মরার লড়াই, আমার জীবন থেকে শুধু একটা বছর কেটে গেছে, অথচ আমার দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছে, কোটি কোটি টাকার সম্পদ ধ্বংস হয়েছে, শত বছরের পুরোনো গ্রাম, সম্পন্ন সংসার জ্বলে পুড়ে ছাই হয়েছে, পরিবার ধ্বংস হয়েছে, জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়েছে, এসবের তুলনায় আমার একটা বছর কিছুই না, একেবারেই কিছু না, আর এটাকে কোনোভাবেই ক্ষতি হিসাবে দেখি না আমি, বরং জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন আমার, আমার সব চেয়ে বড় সুকৃতি, একটা গ্রাজুয়েশান ডিগ্রি কোনোভাবেই তুলনীয় হতে পারে না ওটার সঙ্গে।
ঠিকই বলেছো ডেয়ুড, একটা দেশের জন্ম নেয়ার সঙ্গে জড়িত হওয়া সত্যিই ভাগ্যবানের কাজ। পৃথিবীর সেরা যুদ্ধটা হচ্ছে নিজেদের স্বাধীনতা যুদ্ধ। ক্রুসেড বলো, ধর্মযুদ্ধ বলো, সবই সাম্প্রদায়িক চালিয়াতি।
এটাই হয়তো সত্যি। কিন্তু মুস্কিল হলো, আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের এই উপলব্ধিটুকু পেতে দেয়া হচ্ছে না।
৬
মনে মনে ভেবেছি তাড়াতাড়ি বিছানায় শুতে যাবো আজ, রাতে ঘুম হবে কিনা ভাবছি, গত কয়েকটা রাত ভালো ঘুম হয় নি। গত হপ্তায় আয়ারল্যান্ডে গেছে কেরোল, ওর মায়ের অসুখ, উচিত ছিল আমারও সঙ্গে যাওয়া, ছুটি নেয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম, কেরোল বললো, দরকার নেই। সন্ধ্যার পর এখন অখণ্ড অবসর, এতো অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি ওর সঙ্গে, এখন একা একা লাগে। সন্ধ্যার পর হোয়াইট রাম নিয়ে টেলিভিশন দেখতে বসি, বই পড়তে ইচ্ছে হয় না, রান্না করতেও ইচ্ছে হয় না, ড্রিঙ্কসের সঙ্গে টুকটাক যা খাই ওতেই হয়ে যায়। সন্ধ্যা সাতটার দিকে দরোজায় টোকা শুনে একটু অবাক হই। খুলে দেখি, আবীর।
আরে তুই?
হ্যাঁ, কেমন আছিস?
ভালো, কোনো খবর, বা সমস্যা?
না না, আগে জানাতে পারি নি যে আসবো। এমনি চলে এলাম, মনটা একটু উতাল।
কেন রে?
না, তেমন কিছু না।
ভালোই করেছিস এসে, চল একটু হোক।
না, বাসায় ফিরে যেতে হবে।
থেকে যা না রাতটা, মজা হবে অনেকদিন পর।
তার চেয়ে বরং আমার ওখানে চল, রাতে থেকে আসবি।
আমি তো কিছুটা নিয়ে ফেলেছি, মুখে গন্ধ নিয়ে তোদের ওখানে যাবো?
যাবি কিনা বল, গেলে আমারও একটা কাজ হয়।
কাজটা কি হয়, বরং ওটাই আগে বল।
আর বলিস না, দেশ থেকে আমার এক কাজিন আমদানি করেছে বাবা। এখন বলে ওটার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে।
হায় আল্লা, তোরও সেই কাজিনের ফের?
সিলেটিদের এটা খুব কমন। তোরটা হয়তো একটু অন্য রকম ছিল। কাজিন থাকলে সিলেটিরা অন্য কোথাও যায় না।
কি করবি এখন?
বাবাকে একটু বোঝাতে পারবি? সময় বদলে গেছে, বিয়ের জন্য মনের মিলটা এখন গুরুত্বপূর্ণ, মনোজগত যদি ভিন্ন স্তরের হয় সঙ্গতি হবে কীভাবে?
কথা বলে দেখেছিস তুই?
সম্ভব না।
চল যাই তাহলে। মুখের গন্ধটার কি করবো?
রান্না করা মুরগির মাংস আছে ঘরে?
আছে।
ভালো করে দাঁত মেজে ভিনেগার দিয়ে কুলি করে দু’টুকরো মুরগির মাংস খেয়ে নে, পানি খাবি না।
ভালো বুদ্ধি তো, কাজ হয়?
চেষ্টা করে দেখ।
ঘর থেকে বোঝা যায় নি বাইরে তুষারপাত শুরু হয়েছে। দরজা খুলতেই ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে কিছু তুষারকণা। আবীরের গাড়িটা তুষারে ঢেকে সাদা হয়ে পড়েছে এই অল্প একটু সময়ের মধ্যে। গাড়ির ভেতরটা জমে বরফ হয়ে আছে, গাড়ির বাইরে এতো ঠাণ্ডা লাগে নি, হিটার চালিয়ে ভেতরটা গরম করতে পাঁচ সাত মিনিট লেগে যায়। অক্টোবরের শেষে তুষার ঝরতে শুরু করেছে এবার, শীতটা বেশ জাঁকালো হবে বোঝা যায়। অক্সফোর্ডের যেদিকে আমি থাকি তার উল্টো দিকে আবীরদের বাসা। পুরো শহর পেরিয়ে সিটি সেন্টারের পাশ দিয়ে যেতে হবে, কালো রাস্তাটার এক দিকের ঢাল ধীরে ধীরে নিচে নেমে গেছে, সামান্য বাঁক নিয়ে একটু একটু করে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে গাড়িটা। সড়কবাতির কমলা রঙের আলোয় রাস্তার ঐ অংশের তুষারগুলোকে মনে হয় অনেক উঁচু থেকে ঝরছে আর নেমে যাচ্ছে অনেক নিচে। ঢালের শেষ দিকে ঘন ঝোপ থাকায় সমানভাবে তুষার জমতে পারে নি ওখানে, অন্ধকারে ওজায়গাটা কালো সাদায় ছোপ দেয়া চিতা বাঘের মতো দেখায়। যে বাঁকটা ফেলে এসেছি, সেখান দিয়ে একটা গাড়ি অতিক্রম করায় ওটার আলো সার্চলাইটের মতো দূরের পাহাড়ের শরীর ছুঁয়ে যায়, ঝরা তুষারে একটা সাদা তুলির ক্ষণিক ছোঁয়া পাহাড়ের শরীর থেকে সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়, আবার প্রাচীন পৃথিবীর পবিত্র অন্ধকারের ভেতর ডুব দেয় রাতের ব্যথা-জাগানো প্রকৃতি।
আইসিস নদীর সেতু পেরিয়ে এগ্রৌভ পার্কের পাশ দিয়ে যখন এগোতে থাকে গাড়িটা, আবীরকে বলি সামান্য একটু সময়ের জন্য থামাতে। রাস্তার পাশের ফাঁকা জায়গায় পার্ক করে আলো নিভিয়ে কয়েক মিনিটের জন্য বসতে বলি। ডানদিকের প্রকৃতি এখন রেমিংটনের আঁকা ছবির মতো, প্রায় পুরোটা কালো, স্ট্রিট লাইটের বাতি ঘিরে সাদা মুক্তোর মালার মতো পেঁচিয়ে থাকা শুভ্রতার একটা আঁকাবাঁকা আলোর সারি। শূন্যের নিচে নেমে আসা তাপমাত্রায় রাতের প্রকৃতি এতো ভাবগম্ভীর, কল্পনা করা কঠিন। তীব্র সুন্দর বলার সুযোগ নেই এটাকে, সবই তো কালোর ভেতর আরো কালো কিছু ছায়া, কোনো কিছুরই আকৃতি দাঁড় করানো যায় না, কল্পনায় নির্মাণ করতে হয় ঐ কালো জমাট বাধা অংশটা খাদ, ওটা গাছের সারি, ওটা গির্জার ডানের অংশ, কালো আকাশেও গির্জার চূড়া পৃথক করা যায়, স্কাইলাইন বোঝা যায়। গাড়ির ইঞ্জিনের সামান্য শব্দও প্রকৃতির এই নীরবতায় বিঘ্ন ঘটায়, ইঞ্জিন বন্ধ করে আর ক’মিনিট বসতে বলি, যেটুকু উষ্ণতা আছে ভেতরে, থাকা যাবে কিছু সময়। খুব ইচ্ছে হয় একটু হুইস্কি পান করি এখন, ধীরে ধীরে অন্ধকার সয়ে আসে চোখ, গাছপালা ও বাড়িঘরের আকৃতি বোঝা যায়, শহর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা আলোর আভা এখন স্পষ্ট। পুরোনো পৃথিবী আবার জেগে ওঠার আগে আবীরকে বলি, চল যাই। গাড়ি চলা শুরু করলে ফিরে আসি আবার নিরেট বাস্তবতার ভেতর, যা এড়িয়ে যাওয়ার কোনো পথ জানা নেই, এবং খুব যে আকাঙ্খিত এটা, তাও না। জীবন সুন্দর, পুনর্জন্মে প্রত্যাশী মানুষ, কিন্তু সত্যিই যদি এজীবনে আবার ফিরে পাঠানোর ইচ্ছা বা ক্ষমতা ঈশ্বরের থাকতো, মনে হয় না মানুষ ফিরে আসতো, জানা হয়ে যাওয়ার পর জীবনের অবশিষ্ট থাকে কি আর, মৃত্যুতে তো পূর্ণতা এ জীবনের, তামাম শুদ!
সিটি সেন্টারে গাড়ি ঢুকতেই আবীর জিজ্ঞেস করে রাতের খাবার ওদের রেস্টুরেন্ট থেকে খেয়ে যাবো কিনা। ভেবে দেখি, ভালোই হয়, ওখানেই ওর বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। ভেতরে ঢুকে একটু অবাক হই, এই বরফের ভেতর এতো কাস্টমার এলো কোথা থেকে। আমাকে দেখে এগিয়ে আসে আবীরের বাবা, খুশি হয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে– কিতা ওবা, অতদিন বাদে, ইয়াল্লা, বুড়া মাইনষরে কিতা ইয়াদ অয় নানি বা। অয় খালুজান, অয়। বউক্যা বাবা, বউক্যা। আবীর বলে, আপনে গরোত যান গি আব্বা, আমি বন্দ করি আইরাম। হাছানি, পুয়া ইবারে লইয়া আইবি ত? আইরাম। ইহানো ভাতউত খাওয়াইও না, ঘরো খাইরাম একলগে। আইচ্ছা, অইবো নে। বাপ-বেটার কথার মাঝখানে আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো বিষয় নেই, মিটিমিটি হাসি। এরা এতো আন্তরিক, আপন মানুষদের খুব বেশি আপন ভাবে, ফাঁক নেই কোনো।
ওর বাবা চলে যাওয়ায় পর কিছুক্ষণ রেস্টুরেন্ট সামলায় আবীর, একটা পার্টি বুকিং ছিল, এজন্য একটু ভিড় দেখা গেছে, ওরা চলে যাওয়ায় প্রায় ফাঁকা হয়ে যায় রেস্টুরেন্টটা, মনে হয় না গাড়ি থেকে তুষার সরিয়ে আর কোনো কাস্টমার আসবে আজ রাতে।
প্লেইন রাইসের সঙ্গে ল্যাম্ব-কারি ও ডাল-মাখানা দিয়ে ভাত খেতে বসে খুব ইচ্ছে হয় একটু ড্রিঙ্কস নেই। আবীরকে বলায় বলে, দেখি আব্বার সঙ্গে কথা বলে। চমকে ওঠি, মানে? রাতে যদি এখানে থাকা যায়। কাজের ছেলে আবীর, ব্যবস্থা করে ফেলে। যে হুইস্কিটা গাড়িতে বসে পান করতে চেয়েছিলাম, উপরওয়ালার কাছ থেকে ওটার অনুমোদন আসতে দু’ঘণ্টা লেগে যায়, আমার উপরওয়ালা বোধ হয় একটু বেশি উপরে থাকেন! রাতের এই পরিবেশটা বেশ ভালো লাগে, কাস্টমার নেই, ফাঁকা একটা জায়গায় বসে প্রাণ-ভরে জীবনের মধু পান করি। কখনো কখনো এতো সুন্দর হয়ে ধরা দেয় জীবন! চাইতে হয় না, আর চাইলে বোধ হয় কখনোই পাওয়া যায় না।
রেস্টুরেন্টের লোফ্ট কনভার্ট করে স্টাফদের থাকার জায়গা বাড়ানো হয়েছে। কুক মবিন ভাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করে আবীর যে ডে-অফে কেউ বাইরে গেছে কিনা। গেছইন তিনজন, থাকতায়নি কিতা? দুইজনের লাগি একটা রুম খালি করতা পারতায় নি। আমার রুমো এক সিট আর নজিরর রুমো এক সিট খালি আছে, নজিররে কউখ্যা আইজ রাইত আমার রুমোত আইতো। তুমি কওনা কিলা মবিনবাই। আইচ্ছা, অইবো নে।
রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে সবাই খেতে বসে, অনেকখন চলে গল্পগুজব, স্টাফ কারির বাচা মাছ খাই আমি আর আবীর। দারুণ মজা। কায়দা করে আমার জন্য হুইস্কি নিয়ে আসে কয়েকবার, বেশ নেশা ধরেছে, কথা একটু বেশি বলা হয়ে যায়। রাত একটার দিকে সবাই উপরে উঠে যায়। আমার ইচ্ছে হয় না, আবীর বলে, ঠিক আছে থাক, উঠে যেয়ে লাইম মিশিয়ে এক পেগ জিন নিয়ে আসে। জিজ্ঞেস করি, ওটা কেন রে? বলে, আমার জন্য এটাই নিরাপদ, হঠাৎ কেউ চলে এলে বুঝবে না, কোক সপ্রাইট বা লেমনেড ভাববে, মুখেও গন্ধ হয় না। ভালো ভালো, চালিয়ে যা। আমি পছন্দ করি এজন্য আবীরের ছোট ভাইকে দিয়ে একবাটি হাঁসের মাংস পাঠিয়েছে ওর বাবা, সাতকড়া দিয়ে রান্না-করা মাংসটার স্বাদ অপূর্ব, হুইস্কির সঙ্গে খুব ভালো জমেছে ওটা। বেশ আনন্দের একটা রাত, অনেকদিন স্মৃতি হয়ে থাকার মতো একটা রাত, তুষারপাত বন্ধ হয়েছিল অনেকক্ষণ আগে, আবার হালকাভাবে ঝরা শুরু করেছে, আবীরকে বলি, তুই তো ড্রিঙ্ক নেয়া শুরু করেছিস, না হয় গাড়িটা নিয়ে আবার বেরোতাম। এটা কোনো বিষয় হলো, ক’টা ট্যাক্সি চাই। আউয়ালকে ফোন করে আবীর, ও এখন আমারও ভালো বন্ধু হয়ে উঠেছে, স্টেইজকৌচের ড্রাইভার ছিল, চাকরি ছেড়ে এখন দামি ব্ল্যাকক্যাব চালায়। দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছাবে বলে আউয়াল, আসে পয়তাল্লিশ মিনিট পর। ইয়াল্লা, দাউদবাই নি, কিতা বুলি গেছনগই! না আউয়াল, ভুলি নি, আপনাকে কি ভোলা যায়, কেমন আছেন আপনি? আবীর বলে, চল বেরোই, আর এক পেগ নিবি দাউদ? ওরে বাবা, কি বলিস, গাড়ি পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারবো কিনা ভাবছি। আমার এক পেগ লাগবে, বলে আউয়াল। চমকে উঠি, ড্রিঙ্ক-ড্রাইভ করবেন কীভাবে আউয়াল? ভাববেন না, ওটা আমরা পারি, বাঙালি না! উঠে যেয়ে দুটো পাতা দিয়ে বানানো কড়া চায়ের একটা গ্লাস আউয়ালের সামনে এনে রাখে আবীর। এই নিন স্যার, আপনার ড্রিঙ্কস, ডাবল ব্র্যান্ডি। এক চুমুক দিয়ে বলে, দারুণ! ওর এই দারুণ চা খেতে আরো দশ মিনিট যায়। আবার তুষার ঝরতে শুরু করেছে। গাড়িতে উঠে জিজ্ঞেস করে আউয়াল কোথায় যাবো এখন আমার সখের গোয়েন্দারা? বাহ্ ভালোই বলেছো তো আউয়াল! খুব অন্ধকার কোথাও যাওয়া যায়? যাবে না কেন, কি দেখতে চান, তুষারের অন্ধকার, না অন্ধকারের তুষার? ড্রাইভার না হয়ে কবি হওয়া উচিত ছিল তোমার। আমি তো কবিই দাউদ ভাই। তাই নাকি, শোনাও না একটা কবিতা। ঠিক আছে শুনুন: ভুল করে এসেছিনু সখা, ফিরে যাই ভুল পথে। বাহ্, তার পর? তার আর পর নেই দাউদ ভাই, আমার সব কবিতা এক লাইনের। বেশি লেখো না কেন? বেশি লেখলে বেশি দুঃখ লাগে। হো হো হো। তাছাড়া কবিতা লেখতে গেলে গাড়ি চালাবে কে? তুমি বুঝি খুব রবীন্দ্রভক্ত? একমাত্র ঐ কবিতাগুলোই কিছুটা বুঝি। বোঝো!
গাড়ি যেখানে এসে থামে সত্যিই অন্ধকার। আলো নিভিয়ে দেয়ায় ও ইঞ্জিন বন্ধ করায় মনে হয় অন্য এক জগতে চলে এসেছি। নামবো একটু? নিশ্চয়, কিন্তু হাঁটাহাঁটি করতে যাবেন না, একটু পরেই ঢাল। আদিম যুগের অন্ধকার রাতে গুহামানবের মতো মনে হয় নিজেদের। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বুঝতে পারি অন্ধকারের তুষার বলে কি বোঝাতে চেয়েছে আউয়াল। তুষার ঢাকা সামনের দিকটা হালকা নীল, পাহাড়ের যে সব জায়গায় তুষার জমতে পারে নি সেগুলো কুচকুচে কালো, উপরের আকাশ কালচে নীল, কিছু অংশে ধূসর কালো, উত্তর গোলার্ধের শীতের রাতের এক অসাধারণ নিসর্গ! এখানে কেউ আসে আউয়াল? আসে সামারে, খুব সুন্দর দেখায় তখন, শীতে দু’একজন পাগল আসলে আসতেও পারে, একটু পরে অন্য রকম কিছু দেখতে পাবেন, যাবো এখন? শীতে জমে যাচ্ছি। হ্যাঁ, চলো। পৃথিবীর এই ভীষণ কালো রাতের অপূর্ব অন্ধকার রূপ আজীবন মনে থাকবে আমার। গাড়িতে বসে কিছুক্ষণ গরম হয়ে নেই, গাড়িটা ঘুরিয়েই আবার উল্টোদিকে থামায় এক মিনিটের মধ্যে, কেন থামালো প্রথমে বুঝতে পারি নি। নামেন দাউদ ভাই। নেমে দেখি নিচে বাঁদিকে আলো ঝলমল অক্সফোর্ড নগরী! শহরটাকে এতো সুন্দর দেখায় এখান থেকে! ওকে বলি, তুমি সত্যিই কবি আউয়াল। এদুটো স্পট থেকে ছবি তোলে অক্সফোর্ড নগরের, ভিউকার্ড বানায় ওরা, বলে সে। সত্যিই অসাধারণ, আউয়াল, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। জীবনে ভোলার নয় এদৃশ্য। পৃথিবীটাকে অনেক সুন্দর করে তোলার চেষ্টাও করে মানুষেরা। কিছু মানুষেরা যেমন ধ্বংস করে প্রাচীন জনপদ, নগর সভ্যতা, প্রতিমা, চিত্রশালা, গ্রন্থাগার, তেমনি অনেক মানুষেরা আবার গড়েও তোলে। চলো ফিরে যাই। চলেন।
গাড়িতে উঠে কথা বলি আউয়ালের সঙ্গে। এখানে কেমন লাগে তোমার, আউয়াল, কেমন আছো? সত্যি বলবো? ভালো লাগে না দাউদ ভাই, কেন জানি ঠিক ফিট হতে পারছি না। ফকির আলমগীরের গান আছে না একটা, আমি অধম রিক্সা চালাই ডাহা শহরে, আমারও তাই মনে হয়, মাঝে মাঝে…, বেশির ভাগ উইকেন্ডে ট্যাক্সি চালাই অক্সফোর্ডে, প্রায় প্রতি হপ্তায় ট্রিপ নিয়ে যাই লন্ডন শহরে। কেন এমন হয় বলতো, এদেশে আছো অনেক অল্প বয়স থেকে, বাংলাদেশের জন্য তো কোনো পিছুটান নেই তোমার, কোনো স্মৃতি নেই। হ্যাঁ, জন্মের পর থেকেই আছি, কিন্তু দেশটাকে আপন করতে পারছি না কেন আমিও ভাবি, পড়াশোনা করানোর জন্য বাবা-মা অনেক চেষ্টা করেছেন, হলো না তো ভাই, আব্বার রেস্টুরেন্টে কাজ করলাম অনেক দিন, তাও মন বসে না, এই ট্যাক্সিটা তবু কিছুটা স্বাধীন মনে হয়, মনে হলে চালাই, না হলে না। হ্যাঁ, তা করতে পারো তুমি, টাকা পয়সার খুব একটা প্রয়োজন তো নেই। না দাউদ ভাই, টাকার প্রয়োজন সবারই আছে, আমারটাকে সীমিত রাখি। ওটাই বুদ্ধিমানের কাজ আউয়াল। কি জানি ভাই, ভালো লাগে না আমার, আম্মাও আজকাল দেশে কাটান মাসের পর মাস। আমিও যেয়ে থাকি মাঝে মাঝে, ওখানেও মানাতে পারি না, ওখানের মানুষগুলো স্বার্থ ছাড়া যেনো কিছুই বোঝে না আর। সবাই না আউয়াল। হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তো তাই মনে হয়। হয়তো আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কাটাও বেশি সময়, ওরা একটু স্বার্থপরই হয় আমাদের সমাজে। কিছু ভালো বন্ধু জোগাড় করে নিলে পারো, তাহলে দেখবে দেশেও ভালো সময় কাটাতে পারবে। ভালো বন্ধু পাওয়া তো খুব কঠিন দাউদ ভাই, আর এক জীবনে একজনের বেশি ভালো বন্ধু পাওয়ার প্রয়োজন নেই। ওটাই জোটে না অনেকের ভাগ্যে। হ্যাঁ, তাই।
রেস্টুরেন্টে ফিরে আসি যখন পা টলছে তখনো, অতিরিক্ত এলকোহোল নেয়া হয়ে গেছে, উপরে উঠে শুয়ে পড়ি। আউয়ালের বিষয়টা মনের ভেতর খচখচ করে। সারা জীবন সাধনা করে বাবা আমাকে বিলেত পাঠিয়েছে পড়াশোনা করতে, বাবার ধারণা স্বর্গ পেয়ে গেছি। সত্যি বলতে কি খুব অসুখে নেই, আমার চাহিদা তো মেটাতে পারছি অন্তত, দেশের আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজনদেরও খুশি করতে পারছি, আর কি চাই? অথচ পড়াশোনা থেকে শুরু করে ভালো পেশা গ্রহণ, বিত্ত প্রতিপত্তি অর্জন, সব কিছুর সুযোগ ছিল আউয়ালের আয়ত্বে, কিছুই ভালো লাগে নি কেন ওর? ব্যর্থতাটা কার?
আবীর বলে, এটা প্রজন্মের ব্যর্থতা, আমাদের ভেতর কোনো উচ্চাশা সৃষ্টি করতে পারি নি। আমাদের পূর্বসূরিরা কি আমাদেরকে কোনো স্বপ্ন দেখাতে পেরেছে? ওরা যে চেষ্টা করে নি, তা না, আউয়ালের কথা তো শুনেছিস, ওর বাবা-মা যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। তাহলে আমাদের সমস্যাটা কোথায়? আমার মনে হয় আমাদের সংকীর্ণ ধর্মপ্রধান সমাজে। এক কথায় বিষয়টা উড়িয়ে দিলি এভাবে? হ্যাঁ, কারণ ওটা আমাদের চোখ ফুটতে দেয় না। তোমার অন্তরের চোখ যদি না খোলে মানুষ হবে কীভাবে তুমি? তাহলে, জ্ঞানার্জনের জন্য সুদূর কোথায় কোথায় যাও, প্রভৃতি যে বলে! ওসব কথার কথা, ফাঁকা বুলি। ভারতবর্ষে কোন জ্ঞানটা নিয়ে গেছিল ওরা? ফতোয়া? তুমিই বা তাহলে জ্ঞানার্জনের জন্য ঐসব দেশে না যেয়ে বিলেত এসেছো কেন, যদি ওরা জ্ঞানেরই পূজারী হয়? ধর্ম ও জ্ঞানকে এক সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছিস না তো? না, সমস্যাটা ওখানেই, কিছু কিছু অতি উৎসাহী ব্যাখ্যা দেয় যে একটা গ্রন্থই সকল জ্ঞানের আধার, সবকিছুর সূত্র ওখানে আছে, বল এটা কি সম্ভব? এই সংকীর্ণতার জন্যই আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি, জ্ঞান ও ধর্মকে পৃথকভাবে দেখতে পারছি না। তোর কাছে সাহস করে কথাগুলো বলতে পারছি। আমাদের কেউ, মানে সিলেটি কারো কাছে যদি বলি তাহলে এক্ষুণি মুরতাদ ঘোষণা করে দেবে আমাকে, তুই তো জানিস, তা নই আমি। আসলে এদের লোভ খুব বেশি, যা কিছু করছে, সব লোভের বশবর্তী হয়ে। আমি হতাশ নই, আগামী প্রজন্মেই হয়তো দেখবি, জগতটাকে বুঝতে পারবে ওরা, আমাদের যে হতাশ প্রজন্মটা দেখছিস, এরা আরেকটা হতাশ প্রজন্মের জন্ম দেবে বলে আমি বিশ্বাস করি না, কারণ, ঐ অর্থে লোভ ওদের নেই, আউয়ালকে দিয়ে বুঝে নে। তোকে নিয়েও বুঝতে পারি আবীর। তোর কথায় যুক্তি আছে, চল এখন ঘুমোই।
পরদিন বিকেলে ওদের বাসায় যাওয়ার প্রোগ্রাম করে ওর বাবার সঙ্গে কথা বলে। খাবারের প্রতি আমার প্রেমের বিষয়টা চেনাজানা সবাই জেনে গেছে। আয়োজন করেছে সেভাবে। একথা সেকথার পর আবীরের বিয়ের প্রসঙ্গ ওঠায় ওর বাবা–
পুয়ার বিয়া ঠিক করি লাইলাম, হুনছো নি ওবা?
বাধা দিয়ে ওঠে আবীর–
আব্বা সিলটি মাতরায় কিলা, তাইনো সিলটি নি?
আমি বলি–
না না খালু, আপনি সিলেটিই বলেন, আমি সব বুঝি, বলতে না পারলেও। যতটুকু পারি আমিও একটু আধটু বলবো। আমার দেশের মানুষেরা বাঙলার সঙ্গে ইংরেজি মিশেল দিতে খুব পছন্দ করে, কিন্তু কোনো আঞ্চলিক ভাষা, মোটেও না, আমি একটু চেষ্টা করে দেখি না কেন?
আবীর বলে–
হ্যাঁ, ঢাকাইয়া সিলেটি।
আমার সায় পেয়ে আবীরের আব্বা বলেন–
সিলটি না মাতলে মনো অয় না আপন কারো লগে মাতরাম, বুজজোনি ওবা, পুয়া ছাওয়া ইতা বুজতায় না।
না না টিক আছে খালু, আপনে মাতইন।
হেসে ওঠে ওরা। যাক পরিবেশটা একটু হালকার দিকে এগিয়েছে।
পুয়ার বিয়ার কতা মাতরায় আছিলাম। বুজজোনি বা, মাইয়া আমরার গরোর, আমার বাইওর পুরি, বাক্কা সুন্দর। আবীর ফটো আইন্না দেখা।
বসা থেকে আর ওঠে না আবীর। খালু আবার বলা শুরু করে–
ভিসা করি মাইয়া আনি লাইছি এই দেশো, দেখতায় নি কিতা, গরোই আছে।
আমি বলি–
বিয়ের বিষয়ে আবীরের মত জেনেছেন খালু?
ইয়াল্লা, ইতা কি কয়, আমরার খান্দানো ইতার চল নাই ওবা। হুনতায় পুয়ার বাপোর বিয়ার কিসতা?
কইন খালু।
তহন বয়স কত আমার জানো নি?
না খালু।
পনরো পরছে খালি, হুনি আমার বলে বিয়া, কইন্যা আমার মুইয়ের গরর বইন লাগে। বিত্রে আমার কিলা জানি লাগে খালি, কইতায় পারি না কেউরে, বিয়ার দিন গেলাম বাগি, হারা গেরাম খুইজ্জা গাছের খোড়োলর বিতর থাকি দরি আনি আমারে কলমা পরাইয়া দিলা। তুমার খালার কিসতা হুনতায় নি, ইয়াল্লা, কিতা কয়, রাইতে তানোর গরো আমারে পাডাইলে চিল্লাইয়া কাইন্দা উডোন। আমি তো অহন কি করি, কি করি, ও আল্লা মাবুদ! আমারে কয়, আম্মার কাছে পাডাইয়া দেন, আমার ডর লাগে!
পর্দার আড়াল থেকে খালা বলে, আপনের কিলা ছদবুদ গেছেইগি নি, পুয়া অগলতের লগে ইতা মাতরাইন। ঠা ঠা করে হেসে ওঠে খালু, আইও তুমি এই গরো, তুমার পুয়ার বিয়ার মাত মাতরাম।
খালা যে খুব পর্দা করে তা না, কিন্তু এটা বোধ হয় অভ্যাস হয়ে গেছে, দর্জায় ঝোলানো পর্দার ওপাশে বসে সবার সঙ্গে কথা বলে, সঙ্গে সঙ্গে পানের খিলি তৈরি করে, জাতি দিয়ে কুটুস কুটুস করে সুপারি কাটে, কিছুক্ষণ পর পর বাটায় করে পান সাজিয়ে পাঠায়, চা-নাস্তা পাঠায়, কথাবার্তায়ও অংশ নেয়, এরকমই বোধ হয় নিয়মে দাঁড়িয়েছে। আবীরের বিষয়ে ফিরে আসি–
এখন যুগ পাল্টেছে খালু, বিয়ে-শাদির বিষয়ে ছেলেমেয়েদের মতামত নিতে হয়।
হাছা নি? পুয়া তো কুনতা মাতে না, ইবার মায় পুছোন লইছন।
হয়তো ভয়ে কিছু বলছে না।
ইয়াল্লা, ও আবীরের মা, হুনছোয় নি কিলা মাতইন?
তাইনো ঠিকই মাতরায়, ওমলা দিন আছে নি, দরি বান্দি বিয়া দিলাইলা, আর হারা জীবন গর করলায়। বালা অইলে বালা, কালা অইলে কালা।
একটু দমে যান খালু, কিছুটা চিন্তিত দেখায়, বিষয়টা ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য বলি–
আসলে খালু আপনাদের সময়ে মানুষদের মধ্যে যতটা ঘনিষ্টতা ছিল, সম্পর্কগুলো যত সহজ ছিল, এখন কিন্তু তা না, মানুষ জটিল হয়ে গেছে। আপনারা বিয়ের আগে থেকেই দু’জনে দু’জনকে চিনতেন, তা ছাড়া মেনে নেয়ার ব্যাপারটা ছিল। আজকালের ছেলে মেয়ে, দু’জনের সঙ্গেই কথা বলা ভালো।
ঠিক আছে ওবা, কতা কইমুনে, আমার পুয়ার লাগিও কইন্যা আছে, আমার বাইওর গরর পুরির লাগিও দামাদ আছে। আল্লার হুকুম তাকলে ইয়ান অইবো, না অইলে না।
ঠিকই খালু, আল্লার হুকুম থাকলে এটা হবে, না হলে না।
এই সুযোগে বিষয়টা আল্লার উপরে চাপিয়ে দিলাম। আল্লা থাকার কত বড় সুবিধে, মস্ত জটিল কিছুও খুব সহজে তাঁর উপর চাপিয়ে দেয়া যায়।
খালুর দাঁড়িয়ে থাকা সিদ্ধান্তটা যে এত সহজে কাত করে ফেলা যাবে কল্পনাও করতে পারি নি। আশা করি আর দু’এক বৈঠকে একেবারে শুইয়ে ফেলা যাবে। খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরে আসি। আবীর তো দারুণ খুশি, একটা কাজের মতো কাজ করেছিস দোস্ত। তুই না হয়ে আমাদের সিলেটি কেউ হলে ওকে সুদ্ধ মার লাগাতো আব্বা, তুই থাকাতে রাগ করতে পারে নি, বিষয়টা ভেবে দেখতে পেরেছে। রক্ত যদি আগেই মাথায় চড়ে যায় তাহলে সিদ্ধান্ত নেবে কীভাবে, তখন চায় সিদ্ধান্তটাকে অাঁকড়ে ধরে থাকতে, ওটার ভালোমন্দ বোঝার ক্ষমতাই তখন থাকে না। এখন হয়তো ঠিকই ভাববে এ নিয়ে।
আমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে ফিরে যায় আবীর। ভাবছি কেরোল এলে একটা গাড়ি কিনে নেবো, লিফট নেয়ার জন্য খামোকা অন্যকে কষ্ট দেয়া, ট্যক্সি িডাকতে চাইলেও নিতে দেয় না। দু’দিন পর টেলি আসে কেরোলের, মায়ের শরীর ভালোর দিকে যাচ্ছে না, আরো কিছুদিন পরে আসবে। একা একা ভালো লাগে না, ভালো একটা চাকরির সুযোগ পেয়েছি এবারডিনে, কিন্তু কেরোলকে অঙ্ফোর্ডে ফেলে যাবো কি করে, একটু ভাবনায় পড়ে যাই। আবীরের বিষয়টা আরো দু’বার আলাপ করে মিটিয়ে ফেলি। আবীরের বাবা বুঝতে পেরেছে যে ইংল্যান্ডে বেড়ে ওঠা একজন ছেলের মানসিক স্তর ও বিশ্বনাথে বড় হওয়া একটা মেয়ের মানসিক স্তর কোনোভাবেই একই তলে না, এটার ব্যবধান কমিয়ে কোনোদিনই সমতলে পৌঁছাতে পারবে না ওরা, এজন্যই এসময়ের অনেক বিয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে, আগে যা ছিল বিরল।
এক সন্ধ্যায় আবীরের বাবা বাসায় ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, আবীরের পছন্দমতো অথবা আমাদের খোঁজে কোনো ভালো মেয়ে আছে কিনা। দুটো প্রশ্নের জবাবেই না জানাই, জানি যে আবীরের কোনো প্রেম নেই। তবে আমিও খুঁজে দেখবো বলে জানাই। বাইরে এসে বলি এখন থেকে তো তোর গার্জিয়ান হয়ে গেলাম রে, সালাম-টালাম দিস দেখা হলে।
কেরোল না থাকায় উইকেন্ডগুলো এত ফাঁকা লাগে আবীরকে বলি রাতে এসে থাকতে। বাসায় এসে বলে চল এক কাজ করি, দু’দিনে তোর বাসাটা টাইডি-আপ করে ফেলি। ঠিক আছে, ভালোই হয় তাহলে, কেরোল এসে খুশি হবে। ফার্নিচারগুলো বদলাবি নাকি? যদি এবারডিনে যেতে হয়? আমার মনে হয়, যাস নে, এখানেই ওর চেয়ে ভালো না হলেও একইরকম একটা চাকরি পেয়ে যাবি, দু’দিন আগে বা পরে। বলছিস? হ্যাঁ, বলছি। তাহলে চল কাল টাইডি-আপ করে পরশু ফার্নিচারের সঙ্গে কার্পেটটাও বদলে ফেলি, কিন্তু এসবই তো মালকিনের। তোরা কি বাসা বদলাবি? বদলানোই তো উচিত, ছাত্রাবস্থায় নিয়েছিলাম এটা, এখন দু’জনেই চাকরি করি, আরেকটু ভালো একটা বাসা নেয়া উচিত না। হ্যাঁ, তাই করা উচিত। কিন্তু বাসাটার প্রেমে পড়ে গেছি। তোর প্রেম নেই কিসের সঙ্গে, বিশ্বপ্রেমিক আছে জানি, তুই সর্বপ্রেমিক। আসলেই রে, কেন যেনো সবকিছুরই প্রেমে পড়ে যাই, কোনো একটা হোটেলে যদি এক হপ্তাও থাকি, হোটেলের ঐ রুমটার প্রেমে পড়ে যাই, ছেড়ে আসতে কষ্ট হয়। দেশটাই যে ছেড়ে এসেছিস, ঐ প্রেমটা ছাড়লি কীভাবে? সবকিছুই যে মেনে নিতে হয়, এই পৃথিবীটার প্রতি কারো প্রেমের কমতি আছে, ছেড়ে যেতে হবে না সবাইকে! হ্যাঁ, কথার পিঠে কথা দাঁড় করানোই যায়।
আবীরকে সঙ্গ দেয়ার জন্য এক বোতল গর্ডন জিন নিয়ে আসি, টনিক ওয়াটার ও লাইম মিশিয়ে পান করি। সাতকড়া দিয়ে হাসের মাংস ভুনা খেয়ে অভ্যস্ত ওরা, মেথি দিয়ে রান্না করি আমি, চুলোয় থাকতেই দেখি অর্ধেকটা সাবাড়, ভাত না খেলেও চলবে মনে হয়, সিমারে বসিয়ে রাখি, রাত প্রায় পুরোটা পার করে দেয় জিনের সঙ্গে ঐ মাংস। সকালে ভাড়া নিতে আসে মালকিন। বলি তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে, ভেতরে এসো। বল কি বলবি, সোফায় বসে বলে। পরিকল্পনাটা জানাই ওকে। আমি তো ভাবলাম বাসা ছেড়ে দিবি, বিয়ে টিয়ে করবি না ছোঁড়া, এভাবে আর ক’দিন আলাদা বিছানায় শুবি। আবীরও হেসে ওঠে। পুরোনো এসব রাখবি কোথায়, আর বাসা ছেড়ে দেয়ার সময় নিয়ে যাবি না নতুনগুলো? না, নিয়ে যাবো না। তাহলে একেবারে একই সাইজের নিবি, এখানের সব ফার্নিচারই ঘরের মাপমতো, আর বেশি দামি নিবি না, ঘরের সঙ্গে মানানসই যেন হয়। তাই সই, আমার সই। ওটা আবার কি? বুঝবে না। না বুঝলে বলিস কেন বাঁদর। আর এক কাজ করবি তাহলে, ফার্নিচারের বিল অর্ধেকটা আমার নামে দিয়ে দিস, এ ফার্নিচারগুলো আসলেও অনেক পুরোনো হয়ে গেছে, ওগুলো কি চ্যারিটিতে দিবি? আবীর বলে– পুরোনো দোকানেও দেয়া যায়, একই কথা, যারা কিনে, চ্যারিটি শপ থেকে তো বেশি সস্তা পায় না। তা ঠিক, কিছুটা টাকাও যদি তোদের উঠে আসে। আবীর বলে, ঘরটা রং করবে না? তাও তো করানো দরকার। এক কাজ করি, ফার্নিচার ও কার্পেটের দাম পুরোটাই তুমি দাও, ঘরটা আমরা মুফতে রং করে দেই। ওসব হিসেবনিকেশের দরকার নেই, দু’মাসের ভাড়া দিস না। ওয়াও, গ্রেট, আওয়ার লেইডি মালকিন, আসো এক পাক নাচি তোমার সঙ্গে। সাগ্রহে বলি আমি, চা কফি কিছু খাবে মালকিন? খাওয়াবি? তিনজনে বসে কফি খাই, আর মজার সব গল্প শোনায় আওয়ার লেইডি মালকিন।
কফি খেয়েই বেরিয়ে যাই, পুরানো ফার্নিচারগুলোর ব্যবস্থা করে ফেলি, রং রোলার সব কিনে দু’দিনের মধ্যে রঙের কাজ শেষ করি। ভালো একটা বুদ্ধিই দিয়েছে আবীর। নতুন কিছু ক্রোকারিজ ও টুকটাক কিনে একেবারে নতুন করে সাজাই সব কিছু। চমৎকার একটা সারপ্রাইজ দেয়া যাবে কেরোলকে, রোববারে আসবে ও।
বিকেলে বাসায় থাকবো না জানিয়ে আবীরকে পাঠাই এয়ারপোর্ট থেকে পিক করার জন্য। বাসার সামনে নামিয়ে দিয়ে যায় আবীর। ঘর অন্ধকার করে ডাইনিং টেবিলে বসে অপেক্ষা করি কেরোলের জন্য। টেবিলের উপর নতুন একটা ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখা তাজা ফুল। ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালিয়ে চমকে ওঠে কেরোল, আবার বেরিয়ে যেয়ে দেখে ঠিক ফ্ল্যাটেই ঢুকেছে কিনা, মাথায়ও ঢোকে নি যে ওর চাবি দিয়ে অন্য ফ্ল্যাটের তালা খুলবে না, তখনো দেখে নি আমাকে, লাগেজগুলো টেনে ভেতরে ঢুকিয়ে দরোজা বন্ধ করে। বেডরুমের দিকে যাওয়ার জন্য চোখ তুলতেই আমাকে দেখে, প্রথমে চমকে ওঠে, তারপর চিৎকার দিয়ে দৌড়ে আসে, এসব কি, বলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনেকখন ধরে রাখি বুকের ভেতর। তারপর বলি, তোমার মা আজ কেমন আছে কেরোল? অনেক ভালো। আগের থেকে অনেক ভালো, বারবার বলছিল তোমার কথা। ঠিক আছে, ফ্রেশ হও।
৭
এতো সাধ করে বাসাটায় নতুন রূপ দিয়েছি, নতুন একটা জীবন শুরু করবো বলে, মনে মনে প্রস্তুতি নিয়েছি, তা যে বিধাতার ইচ্ছা ছিল না, আগে বুঝবো কি করে? অক্সফোর্ডের চাকরিটা হতে পারতো যদি অগ্রাধিকার তালিকায় প্রথম দিকে আমার অবস্থান হতো, এদের অগ্রাধিকার তালিকা মোটামুটি এরকম: স্থানীয় ইংরেজ>ইংরেজ>স্থানীয় ব্রিটিশ>ব্রিটিশ>স্থানীয় সাদা>সাদা>স্থানীয় অন্যসব>অন্যসব। যদিও এরা বলে ডিসক্রিমিনেশানের বিপক্ষে এদের অবস্থান, কিন্তু এতো সূক্ষ্মভাবে কাজটা করে যে ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যেরা বুঝতে পারে না, ম্যাগডালেন কলেজের যে চাকরিটা আশা করেছিলাম, তা আমার থেকে অনেক কম ক্যালিবারের ইংরেজের হাতে চলে যায়, সে হয়তো এটা করবেও না বেশি দিন।
কিচ্ছু করার নেই, সবই পরম করুণাময়ের ইচ্ছা, এজগতের সবকিছুই তো তাঁর ইচ্ছাধীন, তুচ্ছ এই মানবের কি করার আছে! এতো বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন তিনি, এই পৃথিবী যেখানে ধূলিসমও না, হয়তো এক পরমাণু পরিমাণ, আর একজন মানুষ পৃথিবীর কতটুকু, এবং মহাবিশ্বের সময়ের হিসেবে একটা মানুষের জীবন তো কোনো হিসেবে আসে না, সবাই জানে এসব, এই মানুষকেই কিনা তিনি গ্রহণ করেছেন নিজ পুত্ররূপে, ও অন্যান্য সম্পর্কে, কী অসীম করুণা তাঁর। অবশ্য ঐ মহাপ্রভুর কোটি কোটি নক্ষত্রের এক সামান্য নক্ষত্র সূর্য বিষয়ে হয়তো ভুলেই গেছিলেন মানুষকে জ্ঞানদানের সময়, নাহয় মানুষ কখনোই বলতো না যে সূর্য ঘোরে পৃথিবীর চারদিকে! মহাপ্রভুর ইচ্ছায় এবারডিনে যেতে হচ্ছে আমাকে, আমার কোনো ইচ্ছে তো নেইই, এমনকি আমার শুভাকাঙ্খীদের কারোও নেই।
অক্সফোর্ড থেকে এবারডিন বাসে দশ বারো ঘণ্টার জার্নি, আসতে ও যেতে রাস্তায়ই কেটে যায় উইকেন্ড, প্রথম কয়েক হপ্তা আমিই আসি, পরের দিকে পালা করে দু’জনে আসা যাওয়া করি, আমার অবস্থা হয়েছে গোগোলের ‘নতুন জামাই’এর মতো, মাঝে মাঝে বিমানের সস্তা টিকেট পেয়ে যাই, ইউরোপের পার্টনারদের জীবন এভাবে চলে না, ভেঙ্গে যায়, কেরোল অনেক সহিষ্ণু, সম্পর্কটা টিকে থাকে। এই অসহনীয় ছোটাছুটির অবসানের কথা ভাবতে থাকি মনেপ্রাণে, এবারডিনে শীত এতো বেশি যে অসুস্থ হয়ে পড়ি, সর্দি ভালো হতে চায়ই না, খুব বেশি এলকোহোল নিতে হয় শরীর চাঙ্গা রাখার জন্য।
জীবনের এক সন্ধিক্ষণে এলিনা এসেছিল সাইক্লোনের মতো, ঐ ঘূর্ণাবর্তে আমিও ঘুরেছি এক সঙ্গে, সাইক্লোন সরে যাওয়ার পর সব শান্ত, বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। নতুন করে আবার জীবন শুরু করেছি। তুচ্ছ এই জীবনে বহতা নদীর চঞ্চলতা এনেছে কেরোল, ওর গতি, ঢেউ, স্বচ্ছতা সবই উপভোগ করি, গ্রহণ করি মন-প্রাণ দিয়ে, ওর উষ্ণ জলে অবগাহন করে প্রাণ জুড়াই, ওর অনুপস্থিতি আমাকে মরুজীবনের যন্ত্রণা দেয়, প্রতিটা রাত বড় দীর্ঘ মনে হয়, দিনগুলো কাটে অস্থিরতায়। প্রকৃত ভালোবাসা এসেছে আমাদের মধ্যে, পরিপূর্ণ প্রেম! হয়তো একেই বলে প্রকৃত প্রেম, উজ্জ্বল, হিরন্ময়, নিকষিত হেম, কোনো উদ্দামতা নেই, রয়েছে গভীরতা, প্রশান্ত আবেগ, তীব্র তৃষ্ণা!
আমার অস্থিরতা মাঝে মাঝে ঠেলে দেয় চাকরি ছেড়ে দিয়ে অক্সফোর্ডে চলে যাওয়ার তীব্র ইচ্ছেটার প্রতি পরাভূত হতে, বাধ সাধে কেরোল, ভালো চাকরি নিয়েই ফিরতে হবে, আমার সিভিতে কোনো বাজে আইটেম ঢোকাতে চায় না সে, মেনে নেই।
যেদিন কোনো ক্লাশ থাকে না, সিটি সেন্টারে ঘুরে বেড়াই অকারণে, দুপুরের খাবার হয়তো ওখানেই খেয়ে নেই। বাজার চত্বরের কাচে ঢাকা অংশের কোনো একটা বেঞ্চে বসে মানুষের আসা যাওয়া দেখি। দু’পাশে দু’সারি দোকানের মাঝখানের জায়গাটা কাচ-ঢাকা, সারি সারি বেঞ্চ বসানো, মাঝে মাঝে জ্যামিতিক নির্মাণ, ফোয়ারা, ভেন্ডিংমেশিন, এসব বসিয়ে সৌন্দর্য বাড়িয়েছে চত্বরটার। আমার সামনে এখন হেইচএন্ডএম-এর বিশাল দোকান, শপিংয়ে ব্যস্ত মানুষের ভিড়ে এক তরুণ-যুগল দৃষ্টি কাড়ে, এটা-সেটা দেখছে মেয়েটা, একটু পরপর হাত বাড়িয়ে ওর ডান নিতম্ব টিপে দেয় সঙ্গী ছেলেটা। আশ্চর্য হই, মেয়েটা একেবারে ভ্রূক্ষেপহীন, নির্বিকার! স্কার্টের নিচে ওর জঙ্ঘায় চোখ আটকে যায়, দারুণ সম্বৃদ্ধ গড়ন! একটু পরে ঐ নিতম্ব ও জঙ্ঘা, দুটো নিয়েই উধাও হয়ে যায় ওরা, জায়গাটা যেন ফাঁকা হয়ে যায়। দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে কাচের ভেতর দিয়ে এটা-ওটা দেখে এক তরুণ, মাথার চুলগুলো ওর হেলমেটের মতো করে ছাঁটা, কুচকুচে কালো, নিশ্চিতভাবেই রং করা। একবার চোখ ফেরায় এদিকে, ওদুটো দেখি গাঢ় নীল, চুলগুলোও নীল রং করালে দেখাতো কেমন, ভাবি। একটু পরে এক বুড়ো এসে পাশে বসে, শরীরে চাপানো দামি কোট, পায়ে চকচকে জুতো, অথচ গা থেকে এমন বদ গন্ধ বেরোয়, ভেতর থেকে উগলে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে উঠে যাওয়ার অভদ্রতা দেখাতে না পেরে দম বন্ধ করে বসে থাকি যতক্ষণ পারা যায়, দম ফুরোলে উঠে যাই, হে ভগবান! বুড়োর যে বুড়ি নেই এটা যে-কেউ নিশ্চিত বলে দিতে পারে।
ইচ্ছে ছিল বসবো কিছুক্ষণ, উঠে পড়েছি যখন, অন্য কোথাও আর বসতে ইচ্ছে হয় না, বাসায় ফিরে এক মগ কালো কফি নিয়ে জানালার ধারে বসি। বাসা থেকে দূরের সমুদ্র দেখা যায়, কিছুটা দামাল, ঝড়ো বাতাস, মাঝে মাঝে বৃষ্টি, সমুদ্রের ধূসর ঢেউ তীরে এসে এসবের প্রতিবাদ জানায়, জানালার শার্সিতে, ছাদের কার্ণিশে বাতাস আটকে পড়ে শিস দিয়ে যায়। নিচের তলায় মিস কোরবিন খুব হালকা সুরে পিয়ানো বাজায়, যখন ঘরে থাকি ওর সুর কখনোই উচ্চগ্রামে পৌঁছে না, তারপরেও বলে রাখে, যদি পিয়ানোর সুর কখনো উপরে উঠে যায়, তোমাকে বিরক্ত করে, মেঝেতে গোড়ালি দিয়ে দুটো টোকা দিও, সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দেবো। অনেক আস্বস্ত করেও উঁচু কোনো সুর ওকে দিয়ে বাজাতে পারি নি। বাখ বাজাতে বলেছি একদিন, খুব খুশি হয় নি, শুনিয়েছে কিছুটা, ওর প্রিয় শিল্পী হোল্ডার্লিন, আমার আগ্রহের চাপে মাঝে-মধ্যে বাজিয়ে শোনায়, যখন বাজায় মনে হয় ভুলে যায় অন্য কেউ শুনছে, বাজানো শেষ হলে আমাকে দেখে চমকে ওঠে মাঝে মাঝে, হয়তো সত্যিই ভুলে যায়। শুধু নিজের জন্য বাজানোর ভেতর গূঢ় কোনো রহস্য হয়তো আছে, ব্যক্তিগত এসব কিছু তো জিজ্ঞেস করা যায় না। বয়েস হলেও এখনো সুন্দরী, বয়সকালে কেমন ছিল আন্দাজ করা যায়, চুল প্রায় সবই সাদা, দু’একটা সোনালি চুলের উপস্থিতি বুঝিয়ে দেয় একসময় মাথা ভরা সোনালি চুল ছিল, হয়তো অনেক ধরনের হেয়ার স্টাইলও করতো। একটা বেণি গেঁথে ঘাড়ের পেছনে ঝুলিয়ে রাখে এখন। এলিনার কথা মনে পড়ে ওকে দেখে, সেও মাঝে মাঝে লম্বা বেণি করতো, বেণির সঙ্গে আরো কি কি যেনো ঝুলিয়ে রাখতো। ফুল ও লতাপাতার কাজ করা উলের একটা সোয়েটার গায়ে জড়িয়ে আছে মিস কোরবিন, লম্বা ঝুলের স্কার্টের রং গাঢ় নীল, নিচের দিকে ড্যামসন রঙের কোনাকুনি দুটো স্ট্রাইপ, বেশ স্মার্ট দেখায় ওকে। আমার আগ্রহ দেখে বলে একদিন, তোমাদের সংগীতের কোনো নোটেশান থাকলে দিতে পারো, বাজিয়ে শোনাতে চেষ্টা করবো। বেশ কষ্ট হয়েছে ওকে বোঝাতে যে আমাদের সংগীত সারেগামাপাধানি এই সাতটা সুরে বাঁধা। অবাক হয়েছে, বুঝিয়ে বলেছি এই সাতটারও আবার উঁচু ও নিচু ধাপ রয়েছে, মোট একুশটার পারমুটেশান কম্বিনেশান করে ক’হাজার বিভিন্ন মাত্রার স্বর তৈরি করা যায় কল্পনা করা কঠিন। বুঝতে পারে নি। বলে, খুব জটিল তোমাদের সংগীত, হয়তো চিনা ভাষার মতো। আমি বলি, মোটেও না, বরং তোমাদের তুলনায় অনেক সহজ, তবে সাধনার ধন। আমার একটা মিউজিক প্লেয়ার আছে, স্পুল, ওখানে কিছু উচ্চাঙ্গের বাদন রয়েছে, ওটা ওকে শুনিয়েছি, মুগ্ধ হয়ে শুনেছে, বারবার বাজিয়ে নোটেশান তৈরি করে নিয়েছে, তারপর পিয়ানোয় তুলেছে, আমার কাছে ভালোই লেগেছে, ওর পছন্দ হয় নি, ঐ সুরে ওর আঙ্গুলগুলো নাকি পিয়ানোর রিডের সঙ্গে নাচে না। এতো নিচু স্বরে এখন বাজায় সে দু’একটা টুংটাং শব্দ ছাড়া আর কিছুই উপরে পৌঁছায় না, অথচ এখন আমার কান প্রস্তুত হয়ে আছে কোনো একটা সংগীতের জন্য। সমস্যা হলো, কোনো কিছুর জন্যই ওকে অনুরোধ করা যায় না।
একদিন ঘরে ঢুকে দেয়ালে ঝোলানো জাহাজের একটা ডেকহুইলের দিকে আগ্রহভরে তাকাই, সঙ্গে সঙ্গে বলে, দয়া করে ওটার বিষয়ে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করো না, কেমন চুপসে যাই। নিশ্চয় না, বলে বেরিয়ে আসি।
যে রুমটা ভাড়া নিয়েছি তা ভালোভাবে দেখেশুনে নেয়ার সুযোগ হয় নি, ফোন করে যখন জানি, সেদিনই খালি হয় রুমটা, আগের ভাড়াটে না-নেয়ার মতো টুকটাক কিছু ছেড়ে গেছে। আমাকে বসার ঘরে বসিয়ে কোরবিন বলে, আধঘণ্টা অপেক্ষা করো, রুমটা পরিষ্কার করে দেই। বলি, কোনো দরকার নেই, সব আমি করে নেবো, তুমি বিশ্রাম নাও। দু’বার জিজ্ঞেস করে আমি নিশ্চিত কিনা। ওকে নিশ্চয়তা দিয়ে উপরে এসে বেডকভার পেতে দুবে নিয়ে সোজা ঘুমিয়ে পড়ি, খুব ক্লান্ত ছিলাম সেদিন, ঘুম ভাঙ্গে ওর পিয়ানোর টুংটাং শব্দে। এখনও ওরকমই দু’একটা শব্দ পাচ্ছি। দেয়ালে ঝোলানো একটা ছবি ছিল, পেন্সিল স্কেচ, অনেক পুরোনো কোনো শিল্পীর হবে, নামটা চেনা নয়, ঐ ছবির কুকুরটার দিকে যখনই চোখ পড়ে, মনে হয়, একটু নড়াচড়া করলেই, ঘেউ করে ডেকে উঠবে কুকুরটা! টেবিলের ড্রয়ারে মেয়েদের চুলের বড় একটা ক্লিপ, হয়তো ওর কোনো বান্ধবীর, অথবা, জানি না। শার্টের হাতার একজোড়া দামি কাপলিং, চিঠি লেখার দুটো প্যাড, আরো কয়েকটা জিনিস ফেলে দেই নি, পরের ভাড়াটের জন্য আমিও হয়তো রেখে যাবো এসব, সে যদি হয় আমার মতো কেউ, একইরকম বা অন্যকিছু ভাববে, নয়তো ফেলে দেবে ময়লার ঝুড়িতে, এটারই সম্ভাবনা বেশি। কোনো কিছুই ফেলে দিতে ইচ্ছে হয় না আমার, মনে হয় সবকিছুর সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে কিছু স্মৃতি, কিছু অতীত!
ফাইনাল থিসিস সাবমিট করার জন্য এক বছর সময় পাবো, অবসর সময়ে কাজগুলো করতে হবে, কিন্তু কাজে মন বসে না, কাজ বলতে যা বোঝায় তা হয়তো আমার জন্য না, আমার জন্য শুধু কল্পনা। কাজ করা আসলে অনেক বড় বিষয়, কাজের মানুষেরা কাজ করে, প্রতিভা দিয়ে করতে হয় কাজ, পরিশ্রম দিয়ে গড়ে তুলতে হয় নিজেকে, এ বিষয়টাই মনোপুত নয় আমার, এ পর্যন্ত যাহোক, উতরে এসেছি, শেষটায় কি হবে ঐ মহাপ্রভু জানেন, আমি জানি না। রেডিওলোজির উপর বইপত্র যা আনা সম্ভব নিয়ে এসেছি, মাঝে মাঝে কেরোল লাইব্রেরি থেকে তুলে রাখে, আমি নিয়ে আসি, কখনো সে। আর কিছু না হোক, পড়াশোনাটা অবশ্যই শেষ করতে হবে, এবং ভালোভাবে, এমএস-এর রেজাল্ট যেহেতু ভালো হয়েছে, আশা করি পিএইচডিরটাও ভালো হবে।
পাতা-ঝরা গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে মন আরো বিষণ্ন হয়ে যায়, একটা গাছে দেখি সুন্দর একটা পাখি এসে বসেছে, নাম জানি না পাখিটার, প্রথমে যে ডালে বসে, পাতা না থাকায় ওর ভারে নুয়ে পড়ে, লাফিয়ে অন্যটায় যায়, ওটাও দুলে ওঠে, তৃতীয়টায় যেয়ে ঠিকভাবে বসতে পারে, পাখিটার নাম জানতে হবে, ওয়ান ফর সোরো, ওটার জুটি খুঁজি, কোথাও নেই। পাশের বিল্ডিংএর জানালার পর্দার বাইরে বসে আছে একটা বেড়াল, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে, ওটা আসল না নকল বোঝা যায় না, একটুও নড়াচড়া নেই, আগামীকাল দেখতে হবে একই জায়গায় রয়েছে কিনা।
কোনো একটা উইকেন্ড হয়তো কেটে যায় এভাবে, যে-কোনো কারণে দু’জনেই আটকে থাকি দু’প্রান্তে, হতাশা আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়া মাঝখানে অন্য কিছু থাকে না। দীর্ঘ সময় ধরে পান করার জন্য হালকা বিয়ার নিয়ে জানালার ধারে বসি গান শোনার জন্য, পড়াশোনার কাজটাও চালিয়ে যাই। একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে দরোজায় মৃদু টোকার শব্দ শুনি, নিশ্চিত হতে পারি না আমার দরোজায়ই কিনা, দ্বিতীয়বার টোকা শুনে দরোজা খুলে এতোটাই অবাক হই যে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি কয়েক মুহূর্ত, অবশেষে বলি–
ভাবতেই পারি না!
ভেতরে আসবো?
নিশ্চয়।
সোফায় বসতে বলি ওকে।
এখানে আছি জানলে কীভাবে রল্ফ?
ইচ্ছে থাকলে এটা কোনো বিষয়?
তা ঠিক, কেমন আছো?
ভালো, তুমি?
এই তো, চলে যাচ্ছে।
কেরোলের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়েছি, ও জানালো এ হপ্তায় তোমরা কেউ কোথাও যাচ্ছো না, ভাবলাম এ সুযোগটা নেই, কিছুটা সময় তোমার কাছ থেকে বের করে নেই।
ভালোই হয়েছে, খুশি হয়েছি।
সত্যি?
হ্যাঁ।
সন্ধ্যাটা ফ্রি আছো তো?
কেন কোথাও যেতে হবে?
না, এখানেও কিছুক্ষণ বসতে পারি, অথবা আমার ওখানেও যেতে পারো। জানালা দিয়েই দেখতে পাবে আমার হোটেল রুমটা, ঐ বাঁকে, দু’মিনিটের হাটা-পথ।
ঠিক আছে, তোমার ওখানেই যাবো, বাড়িওয়ালির একটা মৌখিক শর্ত আছে, নিঃশব্দ জীবন যাপন করতে হবে, ওটা মেনে চলি, একটু জোরে গানও বাজাই না।
আরে, ঠিকই তো, কোথাও একটা গান বাজছে মনে হয়, আমি ভেবেছি নিচে কোথাও, তুমি শুনতে পাও ওটা?
হ্যাঁ, অভ্যাস হয়ে গেছে, এখন বরং নিচু স্বরই ভালো লাগে।
এটা ভালোই।
তাহলে আসো আমার ওখানে, রুম নাম্বার একশ’ এগারো।
ঠিক আছে, আধ ঘণ্টা সময় দাও।
কোনো সমস্যা নেই, দেখা হবে শীঘ্র।
অ’রাইট।
একটু খটকায় পড়ি, রল্ফের সঙ্গে যেভাবে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ হয়েছে, আশা করি নি আর কখনো এক টেবিলে বসা হবে, আবার কি ওর রহস্যজালে জড়াতে চায় আমাকে, ওর ঐসব হেঁয়ালি আর ভালো লাগে না, ওকে দেখে মধুকবির বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রহসনটার কথাই মনে পড়ে কেবল, যৌবন পুরোপুরি খুঁইয়েছে সে, এটা বোঝা যায়, এবং অপরিমিত অযাচারে যে নষ্ট করেছে, তাও অনেকটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, যতোই সে নাৎসি ক্যাম্পের অত্যাচারের সাফাই গা’ক না কেন! এলিনার মতো দগদগে আগুন কীভাবে সামলেছিল কিছুদিন, ওটাই এক রহস্য! এলিনা হয়তো আমার প্রতি ওর ক্রোধ, বিতৃষ্ণা, ধিক্কার প্রভৃতির প্রতিশোধ নিতে যেয়ে নিজেকে নিক্ষেপ করেছিল রল্ফের মতো একটা অন্ধকূপের ভেতর। শীঘ্রই যে ওটা কেটে যাবে তখনই বুঝতে পারি, এবং গেছেও, স্বাভাবিক অবস্থায় রল্ফের সঙ্গে এক মুহূর্তও কাটানোর কথা না এলিনার। ওর উত্তুঙ্গ, অস্বাভাবিক সময়টা কেটে যাওয়ার পর নোংরা অন্তর্বাসের মতোই ছুঁড়ে ফেলেছে রল্ফকে। একদিক দিয়ে ভালো হয়েছে, রল্ফ প্রতারক নয়, এক রহস্য! ভগ্নাবস্থা থেকে উঠে আসতে সাহায্য করেছে এলিনাকে, অকুণ্ঠচিত্তে, অকৃত্রিমতার সঙ্গে, এখানে প্রশংসা করি রল্ফের।
আধ ঘণ্টা পর হোটেলের রিসিপশনের দিকে এগিয়ে যেতেই দেখি দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে রল্ফ, হয়তো জানালা দিয়ে আমার রাস্তার দিকে চোখ রেখেছিল। হাত বাড়িয়ে দেয়, সেই পুরোনো রল্ফ, আমাদের ভেতর যে এতো কিছু ঘটে গেছে যেনো মনেই নেই, লাউঞ্জে নিয়ে বসায়, রাতের খাবারের জন্য ডাইনিংএ যাবো, না বারে, জিজ্ঞেস করে। বারে যেতে চাই, মন ঢাকা পড়ে আছে তুষারে, একটু আলো চাই, রোদ চাই, বরফ গলা রোদ।
তোমার থিসিসের কি অবস্থা ডাউ?
এগোচ্ছে ভালোই, সমস্যা হবে না আশা করি, ধন্যবাদ তোমাকে।
অক্সফোর্ড মিস করছে তোমাকে।
হা হা হা, ভালোই বলেছো।
ড্রিঙ্কসটা ঠিক আছে?
হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই, আজ ব্র্যান্ডির রাত, আকাশে অনেক তারা জ্বলছে।
মনে মনে বলি, আসল কথা বলছো না কেন ভায়া! নীরবে পান করি কিছুক্ষণ, অথবা পান করি নীরবতা। অন্ত্রে এলকোহোলের বুদবুদ, চুপ করে তো থাকা যায় না, বলি_
কিছু বলবে রল্ফ?
তেমন কিছু না ডাউ। এলিনা কেমন আছে?
জবাব দেয় না। আবার বলে, ওর সঙ্গে এরকম সমাপ্তি না ঘটলেও পারতো, ভালোভাবেই সরে যেতে পারতো আমার কাছ থেকে, চরম শত্রুকেও হাসিমুখে বিদায় জানানোর মধ্যে একটা আর্ট রয়েছে, মানবিক শিল্প এটা, বিবাদ করে পৃথক হয় ইতর শ্রেণির মানুষেরা, আমি ঘৃণা করি এটা।
ওর কথায় যুক্তি আছে, আপত্তি জানাই না, মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাই।
তাছাড়া ওখানে আমাদের দু’জনের কারোই দোষ নেই, বেজন্মা ঐ সংস্থার লোকগুলোই এলিনাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে।
এবার টোকা লাগে মাথায়, একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলি–
দেখো রল্ফ, তোমার ঐ গোপন সংস্থার প্যাচাল অনেক শুনিয়েছো, ওটায় ক্ষান্ত দেয়ার সময় এসেছে, এখন থামো প্লীজ, একটা শব্দও শুনতে চাই না আর ও বিষয়ে।
রাগ করো না ডাউ, আমি যে নাচার, আমার জীবনের সঙ্গে মিশে আছে ওটা, আমার শরীরে চামড়া যেমন টেনে তুলে ফেলে দিতে পারি না, ওটাকেও ছাড়াতে পারি না তেমনি। বিশ্বাস করো, ওটা এমনকি পোশাকের মতোও যদি হতো, ছুঁড়ে ফেলে দিতাম। পাগল হওয়ার ভান করে ন্যাংটো ঘুরে বেড়াতাম।
আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি তোমাকে, রহস্যটা খুলে বলছোও না।
বলবো একদিন নিশ্চয়, সময় পেতে হবে তো।
বলো, এক্ষুণি বলো।
সে সময় তো আসে নি ডাউ।
হ্যাঁ, আসবে, যখন হয় তুমি, নাহয় আমি আর এ জগতে থাকবো না।
এরকমও হতে পারে।
ঐ গোপন সংস্থা যেহেতু তোমার পিছু ছাড়ছে না এখানে, দেশে চলে যাও না কেন?
তোমাকে তো বলেছি যে দেশে আমার ভাই, বন্ধু, স্বজন কেউ বেঁচে নেই। এতো সব মৃত আত্মার ভেতর একমাত্র জীবিত হিসেবে বেঁচে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব, নিশ্চিত আত্মহত্যা করতে হবে আমাকে।
স্বজাতির ভেতর বেঁচে থাকতে পারো, নতুন নতুন বান্ধবী পেতে পারো, পরিবার গড়ে তুলতে পারো, বন্ধুজগত গড়ে তুলতে পারো, কত কিছুই তো পারো। কিছু মনে করো না, আমার মনে হয় তুমি মানসিকভাবে অসুস্থ।
তা বলতে পারো তুমি।
এদেশে থেকেই বা কি হচ্ছে তোমার! সারাক্ষণ বলছো গুপ্ত সংস্থা তোমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, দেশে গেলে নাহয় স্বজনদের মৃত আত্মারা তাড়া করে বেড়াবে, ওরা তো কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তোমার।
তোমার কথায় পুরোপুরি যুক্তি আছে, সবই মেনে নিচ্ছি ডাউ।
আমার সন্দেহ হয়, তুমি রল্ফ কস্টার্লিৎজ নও, কোনো গুপ্ত সংস্থাই নেই তোমার পেছনে, তুমিও গেস্টাপো বাহিনীর কেউ, ছদ্মনামে এদেশে পালিয়ে আছো।
ওর চোখে কি বিদ্যুৎ খেলে গেল! আমার চোখেও ঘোর থাকায় বিষয়টা বুঝতে পারি নি। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। বলি_
বলো, কি বলতে এসেছো।
তুমি জানো ডাউ, বিলেতে একমাত্র তোমাকেই বন্ধু হিসেবে পেয়েছি, তোমার সঙ্গে দু’চারটা কথা বলি, কিছুটা সময় কাটাই, আমি বিশ্বাস করি বন্ধুত্বের মধ্যে অবিশ্বাস থাকতে নেই, সন্দেহ থাকতে নেই।
বুঝতে পারি যথেষ্ট আহত হয়েছে রল্ফ। বলি–
বিশ্বস্ত থাকার জন্যই সন্দেহটা মনের ভেতর না রেখে প্রকাশ করে ফেলেছি।
ভালোই করেছো।
এক প্যাকেট সিগারেট বের করে দেয়, রল্ফ অধূমপায়ী, আমার জন্য প্যাকেটটা কিনেছে, একটা সিগারেট বের করে পাফ নিতে থাকি। প্যাকেটটা আবার ওর পকেটেই ঢুকিয়ে রাখে, একটা রহস্যই রয়ে গেল সে, বুঝতে পারি না কি করি ওকে নিয়ে, ওর বন্ধুত্বে কোনো খাদ নেই, মনে হয় সত্যিই বন্ধু হিসেবে নিয়েছে, প্রায় সবকিছুই খোলাখুলি বলে আমাকে, কিন্তু এই গুপ্ত সংস্থার রহস্যের জট খুলছে না, অথচ সব সময়ই বলে এ প্রসঙ্গে কথা বলতে হবে আমার সঙ্গে, আশ্চর্য!
আসলে ডাউ, এলিনার বিষয়ে কথা বলতে আসি নি তোমার সঙ্গে, আমার জীবনে একটা ঝড়ের মতো এসেছিল সে, ঝড়ের মতোই মিলিয়ে গেছে। রেখে গেছে অনেক ঝরা-পাতা, ভাঙ্গা ডাল-পালা, দুঃখ ও আনন্দ-দেয়া কিছু সংহার-চিহ্ন।
একটু অবাক হই, একই রকমভাবে আমার জীবনেও এসেছিল এলিনা, একটা সাইক্লোন, হ্যারিক্যান, টর্পেডো একটা ঝড়ের নাম এলিনা!
আমি এসেছি ডাউ, নীৎসে প্রসঙ্গে একটু আলোচনা করতে, একা একা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম অক্সফোর্ডে।
এক পাগল আরেক পাগলের জন্য দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে আসবে, এটাই স্বাভাবিক।
এবার ওর মুখে হাসি ফুটে ওঠে, কেন জানি না ওকে পাগল বলে ডাকলে খুব খুশি হয়, সব পাগলের ডাক্তারই হয় কিনা জানি না। ওর হাসিটা সত্যি অকৃত্রিম, শব্দ করে হাসতে জানে না মনে হয় রল্ফ, কখনো শুনি নি, কিন্তু যখন হাসে, ওর চোখ-মুখ শরীর সবই হাসে। ওর ঐ পুরোনো হাসি দেখে আমিও হেসে ওঠি হো হো করে। আবার সেই পুরোনো দিন, পুরোনো অন্তরঙ্গতা ফিরে আসে। দু’পেগ হয়ে গেছে আমার, রল্ফের প্রথম পেগের অর্ধেকও শেষ হয় নি, ব্র্যান্ডিতে এক ফোঁটাও জল মেশায় না রল্ফ, গুনে গুনে তিনটা আইসকিউব, চুমুক দেয় কিনা তাও বোঝা যায় না, ঠোঁটে ছোঁয়ায় শুধু, এভাবে সারারাত চলবে, সাকুল্যে হয়তো তিন পেগে পৌঁছাবে, বোতলের বাকিটা আমার, মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করি, তুমি কি আমার জন্য রেখে দিচ্ছো? তখন আরেকটা বোতল আনিয়ে নেয়, পারা যায় না ওর সঙ্গে। গ্লাসটা একটু নাড়াচাড়া করে ঠোঁটে ছুঁইয়ে নামিয়ে রাখে টেবিলে, তাকিয়ে দেখি, একটু কমেছে! আরেকটা সিগারেট বাড়িয়ে দেয়, সিগারেটের প্যাকেটটার দিকে তাকিয়ে বলে–
প্রতিভাবানেরাও একধরনের পাগল, অথবা পাগলেরাও একধরনের প্রতিভাবান।
পাগলের ডাক্তারেরা ওরকমই বলে। যাকগে, নীৎসে বিষয়ে কি যেন বলতে চাইছিলে?
হ্যাঁ, নীৎসের অতিমানব দর্শনের সঙ্গে আশ্চর্য এক মিল খুঁজে পেলাম তোমার দেশের এক দার্শনিকের।
উৎসুক হয়ে উঠি, আমার দেশের দার্শনিক!
আগ্রহ নিয়ে তাকাই, বুঝতে পেরে বলে–
হ্যাঁ, তোমার দেশের দার্শনিক, আল্লামা ইকবালের কথা বলছি।
বরফঠাণ্ডা এক বালতি জল যেন কেউ ঢেলে দেয় আমার গায়, আবার ঐ … ! বলি–
ঐ দার্শনিক আমার দেশের না, আমার একসময়ের দেশের অন্য একটা অংশের, ওদের সঙ্গে ভয়ানক বিবাদ হয়েছে আমাদের, পৃথক হয়ে গেছি আমরা, দু’যুগ আগে দু’শিংওয়ালা এক দৈত্যের স্বপ্ন নাকি দেখেছিলেন তিনি, যার ফলশ্রুতিতে ভারত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি আমরা, ঐ দৈত্যদানোর শিং হয়ে থাকা আমাদের মতো নিরীহ জনগোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব হয় নি, যুদ্ধ করে নিজেদের জন্য নতুন দেশের জন্ম দিয়েছি। একটু উত্তেজনা নিয়ে কথা ক’টা বলি। তাড়াতাড়ি আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে দেয় রল্ফ।
ক্ষমা করো ডাউ, এ ব্যপারটা সম্পূর্ণ ভুলেই গেছিলাম। হ্যাঁ, সে এখন আর তোমার দেশের কেউ না। না বুঝে হয়তো ভুল জায়গায় হাত দিয়ে ফেলেছি, কিছু মনে করো না, আমি সত্যিই দুঃখিত। যাহোক, প্রাচ্যের একজন দার্শনিক হিসেবে ওকে দেখায় কোনো আপত্তি আছে তোমার?
মোটেও না রল্ফ, ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে অশ্রদ্ধা করি না, ওর আসরার-ই-খুদি ও জাভেদনামার অনেক কবিতা আমার মুখস্ত, নিঃসন্দেহে একজন উঁচুমাপের পণ্ডিত ও ইসলামী চিন্তাবিদ। ঐ ধর্মটা কোনো দেশ-কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ না।
হ্যাঁ, প্রায় ও-কথাটাই বলতে চেয়েছি, ধর্মজ্ঞান ঐ ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, মানবজাতির জ্ঞান তো ঐ পরিসরে সীমিত না, তাছাড়া যে-অর্থে জ্ঞান, ধর্মের ভেতর কতটুকু রয়েছে তা?
ধর্মের বিষয়টা আলোচনার বাইরে থাক রল্ফ, তুমি ইহুদি, আইনস্টাইন সহ পৃথিবীর অসংখ্য বিজ্ঞানী ইহুদি, ওদের তত্ত্ব, আবিষ্কার, জ্ঞানের ফসল, অনুদান, সবই মুসলমান হিসেবে গ্রহণ করতে অসুবিধা হচ্ছে না, শুধু ওদের ধর্মবিশ্বাসকে স্বীকৃতি দিতে চূড়ান্ত অনীহা আমার, এই বৈপরীত্য নিয়ে কথা বলতে গেলে বরং সমস্যা এসে দাঁড়াবে।
হঁ্যা, ঐ বইটার কথা বলতে চেয়েছিলাম, প্রথমে যেটার উল্লেখ করেছো, ওখানে আল্লামা যে মর্দে মোমিনের ধারণা দিয়েছে, ওটা তো নীৎসে থেকে নেয়া, যদিও সে অস্বীকার করে।
হ্যাঁ, এই অস্বীকার করাটা আমাদের মজ্জাগত, পূর্বের সবকিছুকে অস্বীকার করি আমরা, অন্ধ-কাল বলি। আমাদের সবকিছুই মৌলিক, অন্য সবকিছু ভুয়া।
এটার ক্ষতিকর দিকটা ভেবে দেখেছো?
ভেবে দেখার প্রয়োজন নেই। এজন্যই হিউম্যান রেইসে পিছিয়ে আছি আমরা।
হয়তো এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি একসময় কেটে যাবে।
লক্ষণ দেখি না, একসময় একটা সমপ্রদায় দাঁড়িয়েছিল যারা মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ধর্মচর্চা শুরু করেছিল, মেরে-কেটে শেষ করে ফেলা হয়েছে ওদের, এরপর থেকে আর কেউ সাহস করে না।
কিছুটা পড়েছি ওদের সম্পর্কে, মোতাজিলা সম্প্রদায় সম্ভবত।
হ্যাঁ, কথা তো আবার ধর্মের দিকেই চলে যাচ্ছে।
সমস্যা হচ্ছে, নীৎসে আলোচনা করতে গেলে ধর্ম এসেই যায়, কারণ তিনিই বলেছিলেন ‘ঈশ্বর মৃত’। তাছাড়া জীবনে ধর্ম তো আছেই, ওটা বাদ দিয়ে তো জীবন না।
হ্যাঁ, জীবনযাপনে, জ্ঞানবিজ্ঞানে যতই উন্নত হও না কেন ধর্মীয় উন্মাদনা যাবে না তোমার। কি নেই তোমাদের? অথচ তোমাদের ধুরন্ধর মানুষগুলো আমেরিকা ইউরোপ প্রভৃতি জায়গায় স্বর্গ উপভোগ করছে, আর এক শ্রেণির ধমের্ান্মাদ মানুষ পাঠিয়ে ইস্রায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে, কয়েক লক্ষ মানুষকে তাদের পিতৃপুরুষের মাটি থেকে উচ্ছেদ করেছে, যারা ওখানে বাস করছে ওরাও চারদিকের মুসলমানদের ঘৃণা, অবিশ্বাস ও হিংস্র হুমকির মধ্যে জীবন যাপন করছে। এটা তো চিরস্থায়ী হবে না, কোনো না কোনো দিন অযৌক্তিক শক্তির পতন হবেই, রোমান সাম্রাজ্য নেই, বলকানদের সাম্রাজ্য নেই, সেখানে তুচ্ছ একটা রাষ্ট্র টিকে থাকবে কীভাবে, শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তন হলেই ওটা ধ্বংস হয়ে যাবে।
তোমার কথার পেছনে যুক্তি আছে, ধর্মীয়ভাবে আমরা এখনো সবচেয়ে বেশি গোঁড়া, খ্রীস্টানরা উদার হওয়ায় এগিয়ে যেতে পারছে, তোমাদের গোঁড়ামির অবসান হবে বলে আমার বিশ্বাস, যখন এটার উৎপত্তি হয়েছিল তখন যথেষ্ট প্রগতিশীল ও সহনশীল ছিল, যাহোক, আমরা নীৎসে নিয়ে কথা বলছি।
বাদ দাও বরং, ওটা নিয়ে কথা বলতে গেলে ধর্ম এসেই যাচ্ছে। ধর্ম, রাজনীতি ও যৌনতা, এই তিনটে বিষয় নিয়ে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না আমি।
আমার ভুল হয়েছে আল্লামাকে টেনে এনে।
এবার একটা কাজের কথা বলেছো, খুশি হয়েছি, ওগুলোকে টেবিলে না আনাই ভালো।
কথা বলতে চেয়েছিলাম জারাথুস্ট্রাকে নিয়ে।
আবার তো সেই নবী আর ধর্মই এসে যাচ্ছে।
আসুক না ডাউ, আমাদের দু’জনের কেউই তো কট্টর নই, অসহিষ্ণু নই, অসুবিধা কি?
তা বলতে পারো না, ধর্মের দিক থেকে কতোটা খোলামেলা আমি, তা তো বোঝোই। ধরো, কোনো কারণে যদি আরেকটা ক্রুসেড শুরু হয়ে যায়, ডেফিনিটলি আমি ঐ ধর্মযুদ্ধে যোগ দেবো, যত ঘৃণাই করি না কেন, মানবচরিত্রের এক রহস্য এটা।
রহস্যও ঠিক না, একটা বিশেষত্ব ।
হয়তো।
জানোই তো, যদিও আমরা জানি ক্রুসেড শুধুই মুসলমান ও খ্রীস্টানদের ধর্মযুদ্ধ, আসলে তো তা না, ঐ কয়েকশ’ বছরের অধিকাংশ সময় খ্রীস্টানরাই যুদ্ধ করেছে খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে। মুসলমানেরা ক্রুসেড শুরু করে নি, বরং ওদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, মুসলমানেরা তখন ছিল অপরাজেয়, খ্রীস্টানদের কাছে ওটা ছিল অসহনীয়।
হ্যাঁ রল্ফ, এ সবই ইতিহাসের সত্য। তুমি যে আশাবাদ ব্যক্ত করেছো এক সময় মুসলমানেরা সংকীর্ণতা ছেড়ে প্রগতির পথে আসবে তার সব চেয়ে বড় বাধা হচ্ছে মুসলমানবিশ্বের প্রায় সবটাই দারিদ্র ও অশিক্ষার নিগড়ে বাধা। রোমের সম্রাট খ্রীস্ট ধর্মটাকে ব্যবহার করেছিল হাতিয়ার হিসেবে, পালিত যাজক সম্প্রদায় তৈরি করে নিজেদেরকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বানিয়ে দুর্ধর্ষ ইউরোপীয়দের, কিছু মনে করো না এরকম একটা শব্দ ব্যবহার করায়, অনুগত খ্রীস্টান প্রজা হিসেবে তৈরি করে নিয়েছে। অপর দিকে মুসলমান সেনাপতিরা অধিকাংশ দরিদ্র বিশ্বের দুর্বল ও আত্মকলহে লিপ্ত রাজা উজিরদের পরাজিত করে ঐসব ভুখণ্ডের মানুষদের ধর্মান্তরিত করেছে, উত্তরাধিকার সূত্রেই ওরা বঞ্চিতদের দলে, ওদের উঠে আসা একটু কঠিন বৈকি।
যথেষ্ট যুক্তি আছে তোমার কথায়। ভেবো না, খ্রীস্টানেরাও একসময় খুব কট্টর ছিল, ব্লাসফেমি আইনটাও ওদেরই করা। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে জানে ওরা, ইচ্ছে করেই অচল করে রেখেছে ওটাকে। মনে হয় একটা পেগ অতিরিক্ত নিতে হবে আমাকে, তোমার সঙ্গে কথা বলে কী যে ভালো লাগছে ডাউ।
নাও, কিচ্ছু হবে না, নির্জলা ব্র্যান্ডিই নেবে, না অন্য কিছু মেশাবে?
না, তা পারি না কেন যেন।
ঠিক আছে নাও, আরেকবার ধূমপান করতে পারি?
নিশ্চয়।
বার বন্ধ করে ক’টায় ওরা?
সম্ভবত বারোটায়, জিজ্ঞেস করে আসি।
রল্ফ উঠে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ একা একা ভাবি, আসলে কি কথা বলতে এসেছে সে, একেবারে অকারণে নিশ্চয় খুঁজে বের করে নি আমাকে। টয়লেট থেকে ঘুরে আসি এই ফাঁকে। এসে দেখি দু’প্লেইট ফ্রায়েড চিকেন উইংস ও ক্রিপ্সি নাগেট নিয়ে এসেছে রল্ফ, মুখে দিয়ে দেখি বেশ মজা। ফাইভ স্টার হেটেলের খাবার, মজা না হওয়ার কোনো কারণ নেই, বারটাও বেশ বড়, হলের দু’পাশে দু’সারি ছোট ছোট রুম, একান্তে বসে কথা বলতে চাইলে ওখানে বসা যায়, সামারে নিশ্চয় গমগম করে এ জায়গাটা, নাট্যমঞ্চটাও বেশ বড়, শহরের সেরা বার-ড্যান্সররা নাচতে-গাইতে আসে নিশ্চয়। আসবাবপত্র বেশ দামি, অনেক ফাইভ স্টার হোটেলও আজকাল দেখতে জমকালো আধুনিক সস্তা ফার্নিচার দিয়ে সাজিয়ে রাখে। ওদের সব ফার্নিচার ও কাঠের ডেকোরেশান জর্জিয়ান রীতির। অনেক পুরোনো হোটেল হবে হয়তো, আভিজাত্য ধরে রেখেছে। কার্পেটের রং, নক্সা ও চাকচিক্য দেখে মনে হয় ইরানি, ছাদের কারুকাজ ও ঝাড়বাতি ভিক্টোরিয়ান, দেয়ালে বসানো হালকা আলোর বাতিগুলো আধুনিক ডিজাইনের হলেও সবকিছুর সঙ্গে মিল রয়েছে। বিলেতের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টেরিয়র ডেকোরেশানে ডিগ্রি কৌর্স করানো হয়, আর্কিটেকচারের মতোই গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় এটাকে। ভাবা যায়, চার্চ ও ক্যাথেড্রালের মতো বড় বড় স্থাপনাসমূহের আভ্যন্তরীন অঙ্গসজ্জা করেছেন, ছাদের ও খিলানের চিত্র, দেয়ালের ফ্রেস্কো প্রভৃতি এঁকেছেন মাইকেলেঞ্জেলোর মতো বিখ্যাত সব শিল্পীরা!
আড্ডা দিতে এতো ভালোবাসি, অথচ এই কথা বলায়ও অনেক সময় ক্লান্তি এসে যায়, বিশেষ করে শুধু দু’জনে হলে, পালা করে কারো না কারো কথা বলতেই হয়, সেক্ষেত্রে মেয়েবন্ধু অনেক ভালো, কিছু না বললেও চলে, শুনে যাওয়ার সময়ও পাওয়া যায় না মাঝে মাঝে, বিতর্কে যেতে হয় না, বা যাওয়া বিপদজনক, সবকিছুতে সায় দিয়ে গেলেই হান্ড্রেড পার্সেন্ট! রল্ফের সঙ্গে এখন আর কথা বলতে ইচ্ছে হয় না, একটু বিরতি নেই, চুপচাপ সিগারেট টানি, চেয়ারে বসি অলস ভঙ্গিতে। রল্ফের সঙ্গে কথা বলার মজা হচ্ছে, প্রকৃতই একজন ভালো সাইকোলোজিস্ট সে, মনের কথা আঁচ করতে পারে, চুপচাপ বসে ছাদের কারুকাজ দেখে, কার্পেটের নক্সা দেখে। ওর বিষয়টা অনেক ভেবেও বের করতে পারি নি, ও বলে, সব সময় এক অদৃশ্য গোয়েন্দা সংস্থা পেছনে লেগে আছে ওর। কেন? জানতে চাইলে বলে সময় নিয়ে বলবে, সেই সময়টাও গত তিন বছরে আসে নি, আমার ধারণা কখনোই আসবে না। যথেষ্ট সুপুরুষ সে, আমার চেয়েও দু’ইঞ্চি লম্বা, প্রায় সোয়া ছ’ফুট, একহারা গড়ন, না বললে বুঝতামই না যে আমার চেয়ে বয়সে বড় সে। সুন্দর চেহারা, স্মার্ট, ভালো চাকরি করে, মেয়েদের চাওয়ার সবই রয়েছে ওর আয়ত্বে, অথচ এক রহস্যময় জীবন যাপন করছে। কোন দেশি গোয়েন্দা সংস্থা ওকে ফলো করছে তাও বলে না, জার্মানির যদি হয় তাহলে সে ওদেশে যেতে ভয় পায় কেন, আর এদেশি হলে তো এতো কিছু করার দরকার নেই ওদের, অবাঞ্চিত ঘোষণা করে দেশ থেকে বের করে দিতে পারে যে-কোনো সময়। তাছাড়া, অন্য কিছুতেই বাধা দিচ্ছে না ওরা, শুধু ওর মেয়েমানুষগুলোকে সরিয়ে নিচ্ছে ওর কাছ থেকে!
টয়লেট থেকে ঘুরে এসে জিজ্ঞেস করে–
ঘুমোবে? বলি–
আরো কিছুক্ষণ বসি?
ঠিক আছে, আমার বকবক শোনো তাহলে।
বিলেতে প্রথম আসি অক্সফোর্ডে নয়, এই এবারডিনে। ঐ সময়টায় এমন এক আচ্ছন্নতার ভেতর ছিলাম, মনে হয় না বাস্তবে এসেছিলাম, একটা স্বপ্নের ঘোরের ভেতর কেটে গেছে কিছুদিন, প্রকৃতই একটা স্বপ্ন দেখতাম যে তুষারের মধ্যে পাহাড়ে চড়ছি, বারবার পা পিছলে যাওয়ার আতঙ্কের মধ্য দিয়ে উপরের দিকটা মনে হতো দুরতিক্রম্য, আর নিচে তাকালে আত্মা শুকিয়ে যেতো ভয়ে, কৈশোরকালের যে-সব স্বপ্নে সঙ্গিনী থাকে না, মনে থাকে না সেগুলো, ঐ সব স্বপ্নের ভেতর সে থাকতো ওর সোনালি চুল ও নীল চোখ নিয়ে, আধফোটা ক্যামেলিয়া কুঁড়ির মতো ওর কমনীয় শরীর নিয়ে, ও ভাবতো দারুণ সাহসী আমি, অথচ ভেতরে ভেতরে নিশ্চয় ভীতু ছিলাম। এবারডিনে কাটানো প্রথম শীত ঋতুতে এতো বেশি পুরোনো দিনের কথা মনে পড়েছে, অথচ সেসব পুরোনো দিনের ছিল না, সদ্য অতীতের, দু’জনেই ভালোবাসতাম বাইরে কাটাতে, ঘরের ভেতর কখনো মন বসতো না, রকসাইক্লিং ভালো লাগতো আমাদের, বিশেষ করে ঢালু পথে ঝাঁকুনি খেতে খেতে নেমে যাওয়ার মধ্যে আত্মহারা হওয়ার মতো আনন্দ পাওয়া যেতো। কোনো কোনো দিন সৈকতের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তাটা দিয়ে সাইকেল চালাতে চালাতে সমুদ্রের অসীম সৌন্দর্য দেখতাম মুগ্ধ চোখে, মাঝে মাঝে ইচ্ছে হতো কোনো একটা গান গেয়ে শোনাই ওকে, অথচ কোনো গানই শেখা ছিল না আমার, হয়তো একটা সুর ভাঁজতাম শুধু ড ধ্বনি দিয়ে, ডুডল ডুর মতো, ওতেই সে হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিতো, অনেক সময় আঙ্গুর খেতের ভেতর ঢুকে পড়তাম, একেবারে ভিন্ন একটা গন্ধ ভেসে বেড়াতো আঙ্গুর বাগানে, কখনো বলেছি ওকে–
পাকা আঙ্গুরের গন্ধ তোমার শরীরের গন্ধের মতো অনেকটা!
কিছুটা বিস্ময় মিশিয়ে নাক কুঁচকে জিজ্ঞেস করেছে–
টক টক?
না, মিষ্টি মিষ্টি।
হেসে জড়িয়ে ধরেছে, এক থোকা আঙ্গুরের মতো ওর বেগুনি ঠোঁটে যেনো কোনো ত্বক ছিল না। তুষারে জমে যাওয়া কিছু আঙ্গুর ওরা সংগ্রহ করতো বিশেষ ধরনের মদ বানানোর জন্য, আরেকটা মদ বানাতো আঙ্গুরের ত্বক থেকে, মাত্র কয়েক বোতল মদ তৈরি করা যেতো গোটা বাগান থেকে, খুব দামি ঐ মদ।
পৃথিবীর সব চেয়ে দামি মদ ভগবান জমিয়ে রেখেছেন এইখানে– ওর ঠোঁটে আঙ্গুল ছুঁইয়ে বলেছি।
শেষ করে ফেলছো তো সব!
কখনোই না, অফুরন্ত এটা।
এখন বুঝি, কী এক প্রহসন ছিল ওটা, ঐ বাগানের আঙ্গুর শেষ হওয়ার আগেই ফুরিয়ে গেছে ওটা!
মেয়েদের, না নীৎসে নিয়ে কথা বলছি, রল্ফ!
সুনির্দিষ্ট কিছু তো নেই, কোনো এজেন্ডা অনুসরণ করে কথা বলছি না, ভালো লাগছে তোমার সঙ্গে কথা বলতে, উপভোগ করছি এটা ডাউ।
আমিও উপভোগ করছি। রাত অনেক হয়েছে রল্ফ, বলবে কি, যা বলতে এসেছো?
নিশ্চয়।
তোমার গোয়েন্দা সংস্থার বিষয়টার মতো?
চুপ করে থাকে রল্ফ। মাথা কিছুটা ঝিমঝিম করছে। একটা সিগারেট এগিয়ে দেয় রল্ফ। একটা পরীক্ষা হয়ে যাক, এক পর্তুগীজ বন্ধু, ওস্তাদ ড্রিঙ্কার, একটা কায়দা শিখিয়েছিল, স্টেপ বাই স্টেপ সেটা ফলো করতে হয় নিজের বশ্যতা পরীক্ষা করার জন্য।
যদি সন্দেহ হয়, বেশি পান করে ফেলেছো, তাহলে সিগারেটের প্যাকেট ও লাইটারের জন্য পকেটে হাত দেবে, যদি ঠিকঠাক মতো পেয়ে যাও, ঠিক আছে, না পেলে দেখো দুটোই একসঙ্গে বের করতে পারছো কিনা, না পারলে, থামো, আর পান করো না, কথা বলা চালিয়ে যাও, খোঁয়ারি কেটে যাবে। কিছুক্ষণ পর সিগারেটের প্যাকেট ও লাইটার টেবিলের উপর রাখো, দেখো হাত কাঁপে কিনা, কাঁপলে থামো, কিছুটা সময় নাও, এবার সিগারেটের প্যাকেটের উপর লাইটার রাখো, নামিয়ে একবার বামে, আবার উপরে, এরপর ডানে রাখো, হাত না কাঁপলে লাইটারের উপর প্যাকেটটা বসাও, না পারলে থামো, আর এক ঢোকও না। সিগারেট ধরানোর আগে ঠোঁট থেকে ফিরিয়ে আনো ওটা, দেখো ফিল্টারের দিকটাই ঠোঁটে নিয়েছো কিনা। ভুল হলে থামো আবার, সময় নাও।
বাইরে বেরোনোর জন্য ঠিক আছো কিনা বোঝার জন্য একবার টয়লেট থেকে ঘুরে আসতে হবে। তার আগে দেখে নাও গ্লাসের উপর দিয়ে ওপাশের ছাইদানে ঠিকমতো সিগারেটের ছাই ঝাড়তে পারছো কিনা, এটা করতে যেয়ে অনেকে গ্লাস উল্টে দেয়, সাবধানে থেকো, যদি পারো ঠিকভাবে, চেয়ার থেকে ওঠার আগে একটু ভাবো, উরু দিয়ে ধাক্কা দিয়ে টেবিলের গ্লাস উল্টে দেয় অনেকে, নয়তো পেছনের চেয়ারটা ফেলে দেয়। ওঠার আগে সামান্য উঁচু হয়ে দেখো ঠিক আছো কিনা, তারপর চেয়ারটা সামান্য পেছনে ঠেলে দাও, ফেলে দিও না। পিছিয়ে আসো কিছুটা, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াও, টেবিলের কোনা ছাড়বে না, দাঁড়াতে অসুবিধা না হলে, মাথায় চক্কর না দিলে পোশাক ঠিক করার ভান করে মিনিটখানেক দাঁড়াও, চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে টেবিলের অন্যান্যদের সঙ্গে এক দু’মিনিট কথা বলো, যদি বুঝতে পারো ঠিক আছো, এক দু’টা পা ফেলে দেখো পদক্ষেপগুলো ঠিক আছে কিনা, না থাকলে ফিরে আসো, হঠাৎ কিছু মনে পড়েছে ভান করে হাসির কোনো কথা বলো, যখন বুঝতে পারবে না টলে টয়লেট পর্যন্ত যেতে পারবে, এগিয়ে যাও, দরজা বন্ধ করার কথা ভুলবে না, অনেকেই ভুলে যায়, কিছুটা সময় নাও এখানে, প্রথমেই জিপার ধরে টানাটানি শুরু করবে না, আহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, ভুল করে ওকাজটা বেসিনে শুরু করো না, এটা একটা সাধারণ ভুল। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিজেকেই চোখ টেপো, একটু আড়মোড়া ভাঙতে পারো, সত্যিই যদি বেশি নিয়ে থাকো, গলায় আঙ্গুল দিয়ে বেসিনে বের করে দাও, তার আগে বেসিনের দুটো কলই সাবধানে খুলে দেবে, পুরো খুলবে না, শরীরে যেনো পানি না ছিটায়, গলায় শব্দ করবে না, চশমা খুলে রাখো, খুব ভালোভাবে মুখ ধোয়ার পর বেসিন পরিষ্কার করো, এয়ার ফ্রেশনার ছড়িয়ে দাও, এরপর কমোডে যেতে পারো, জিপার টানতে ভুলো না, বেরোনোর আগে অবশ্যই দেখে নাও নেঙ্ট ইউজারের জন্য টয়লেট প্রপার্লি ক্লিন করেছো কিনা। সাবধানে এসে চেয়ারে বসো।
যদি সত্যিই বেশি পান করে থাকো, তাহলে টয়লেটে যাওয়ার আগেই তোমার বন্ধুকে অনুরোধ জানাও একটা লেমনেড উইথ স্ট্রং লাইম এনে দেয়ার জন্য, পান করে অপেক্ষা করো আগের স্টেপগুলো নেয়ার উপযোগী হওয়ার জন্য। যদি ঠিকঠাক মতো হয়, বিল দিয়ে দিতে পারো, অবশ্যই কার্ডে দেবে, বিল নিতে ভুলবে না। বেরোনোর সময় সিঁড়ির প্রতিটা ধাপ ভালোভাবে লক্ষ্য করবে, যদি দরোজা দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারো ঠিকভাবে, ঘরে ফিরে যাও। না পারলে, কিছু সময় হাঁটাহাঁটি করো, কথা বলো, ডেফিনিটলি ঘোর কেটে যাবে।
সিগারেটটা ধরিয়ে দিতে গেলে লাইটারটা নিয়ে নেই ওর হাত থেকে, সিগারেটটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে দেখি কোন দিকটা ঠোঁটে গুজেছি। লাইটার ও সিগারেট প্যাকেটের গেইমটা খেলতে যেয়ে লাইটারের উপর প্যাকেটটা বসাতে পারি না। ও হেসে বলে–
এটা তোমার দোষ না, লাইটারের শরীরটা উপরের দিকে কিছুটা বাঁকানো।
কিছুটা অবাক হয়ে বলি–
তুমিও জানো ট্রিকটা?
ইউরোপের সবাই জানে।
তা তো জানতাম না।
তুমি বোধ হয় বেরোতে চাচ্ছো। যাও, টয়লেটে যাও, তুমি ঠিক আছো, ভাবতে হবে না।
সত্যি সত্যি ঘুরে আসি টয়লেট থেকে, কোনো অসাধন না ঘটিয়েই। বিলে সই করে বাইরে বেরোনোর জন্য হাত দেখায় রল্ফ, বাইরে এসে মনে হয় বাতাসও জমাট বাধা, রক্তের ভেতর এতোটা এলকোহোল, তারপরও সহ্য করা কঠিন, তাড়াতাড়ি টুপি ও হাত-মোজা পড়ে নেই। ওকে বলি_ অনেক হয়েছে রল্ফ, সবকিছুর জন্য অনেক ধন্যবাদ, তোমার রুমে যাও এবার।
কী যে বলো, তোমাকে না পৌঁছে দিয়ে ফিরি কীভাবে?
তাহলে যে তোমাকে পৌঁছে দিতে আবার ফিরে আসতে হবে আমাকে।
না, হবে না।
বুঝতে পারি, ওর কাছে হার মানতে হবে, তুষার জমে কোথাও কোথাও এতো পিচ্ছিল হয়ে আছে যে ভয়ে ভয়ে রাস্তা পেরোই। ঘরের দোরগোড়ায় এসে বলি_
বিদায় রল্ফ, শুভরাত্রি।
শুভরাত্রি ডাউ, দেখা হবে।
ঘরে এসে দ্রুত কাপড় পাল্টে ফ্রেশ হয়ে জানালার পাশে এসে দাঁড়াই। পর্দা সরিয়ে কিছুটা অবাক হই, রাস্তাটা ক্রস করে সমুদ্রের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে আছে রল্ফ, হাড়-কাঁপানো এই শীতের রাতে সমুদ্রের কোনো সৌন্দর্য আছে কিনা জানি না, সত্যিই উদ্ভ্রান্ত মনে হয় ওকে, ভালো এক রহস্য! গায়ে ওভারকোট চাপিয়ে নিচে নেমে দরজা খুলে ভুত দেখার মতো চমকে উঠি!
রল্ফ! কোনো সমস্যা?
মোটেও না।
তাহলে?
জানালার পর্দা সরিয়ে অবাক হবে তুমি, এটা জানতাম।
শুধু একথাটা বলার জন্যই এসেছো?
সত্যিই তাই।
পাগল?
শুভরাত্রি আবার।
শুভরাত্রি।
গটগটিয়ে হাঁটা দেয় উল্টো দিকে, একবারও পেছনে ফিরে না তাকিয়ে হোটেলের চৌকাঠ পেরিয়ে যায়। উপরে উঠে বিছানায় ছুঁড়ে দেই নিজেকে। নরকে যাক, দুনিয়ার যতো পাগল!
রাতে বেশ ভালো ঘুম হয়, মদ্যপান কিছুটা বেশি হলে যা হয়, দুঃস্বপ্ন দেখা, তা হয় নি। প্রথম ঘুম ভাঙ্গার পর কম করে হলেও ডজনখানেক ছোটো ঘুম দিয়ে যখন দেখি শরীরে কুলোয় না আর, উঠে পড়ি। বড় একটা ব্রেকফাস্ট নেই লাঞ্চের সঙ্গে যোগ করে, ক্যারিবিয়ান কালো কফির সঙ্গে আধপেগ ব্র্যান্ডি মিশিয়ে ডাবল-সুগার দিয়ে এক মগ কফি পান করে শরীরটাকে ঝরঝরে করে নেই। রল্ফের হোটেলে না গেলে সেই এসে হাজির হবে ভেবে প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। দরোজা খুলেই অবাক আরো একবার!
সামনে দাঁড়িয়ে রল্ফ।
রাতে ঘরে ফিরো নি রল্ফ?
সে তো তুমিই দেখেছো ওখানে দাঁড়িয়ে।
তুমি তো কেবল মনস্তত্ত্ববিদই নও, অতিরিক্ত আরো অনেক কিছু!
সামান্য এক বৈদ্য আমি ডাউ, দয়া করে ভুল বুঝো না।
তুমি কি সত্যিই ডাক্তারি পাশ করেছো রল্ফ? চিকিৎসাশাস্ত্রের ঐ ডিগ্রি আসলেই কি দেয়া হয়েছিল তোমাকে?
ওটা তো আমার নিয়োগকর্তাদের বলেছি। আমার সব রেকর্ড জার্মানিতে ধ্বংস করে ফেলেছে ওরা। তোমাকে দেখাবো কীভাবে, প্রয়োজনই বা কি?
ওটা তো একটা চাকরি পাওয়ার জন্য ব্যাখ্যা দিয়েছিলে তোমার নিয়োগকর্তাদের, আমি জিজ্ঞেস করছি তোমার বন্ধু হিসেবে।
যারা চাকরির সাক্ষাৎকার নিয়েছিল ওদের কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে আটকায় নি আমার, বরং কায়দা করে দু’একটা প্রশ্ন করে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিলাম ওদের, আমার কাছ থেকে ওসবের ব্যাখ্যা শুনে অভিভূত হয়ে পড়ে ওরা, আমার চেহারা দেখে চাকরি দেয় নি নিশ্চয়। তাহলে তো কারখানার শ্রমিকের চাকরিতে যেতে হতো আমাকে।
তোমাকে বোঝা আমার জন্য একটু কষ্টকর রল্ফ।
না ডাউ, আমি জানি এদেশে একমাত্র তুমিই কিছুটা বুঝতে পারো আমাকে। তোমার মনের সন্দেহ দূর করার স্বপক্ষে এটুকু বলতে পারি, ইংরেজদের মতো একটা রক্ষণশীল জাতি আমার মতো এক জার্মানকে, যাদের ওরা এক চোখেও দেখতে পারে না, ড. কস্টার্লিৎজ বলে সম্বোধন করে, এবং আমার যোগ্যতাকে স্বীকার করে নিয়েছে, সেক্ষেত্রে তুমি ইচ্ছা করলে দুর্ভাবনা না করলেও পারো, ইংল্যান্ডের মধ্যে তুমি, হ্যাঁ, একমাত্র তুমিই আমাকে রল্ফ নামে ডাকতে পারো, আর কাউকে শুনেছো ওনামে ডাকতে?
না তো রল্ফ, শুনি নি। আমি দুঃখিত, তোমার মনে যদি কষ্ট দিয়ে থাকি, তাহলে সত্যিই দুঃখিত।
কোনো অসুবিধা নেই, আমি বুঝতে পারি তোমাকে।
জানি রল্ফ, আমিও চেষ্টা করবো তোমাকে বুঝতে।
আমরা কি সমুদ্রের আরো একটু কাছে যাবো?
শীতের সমুদ্র খুব বেশি আনন্দ দেয় না আমাকে, তুমি যদি যেতে চাও, যেতে পারি।
তাহলে চলো একটু হাঁটি, ওদিকটায় একটা লোকালয়ের মতো আছে, হারবার আছে, সীফুড রেস্টুরেন্ট আছে বেশ ক’টা, তাজা মাছ খাওয়া যাবে, ওখান থেকে সমুদ্রটাকে ভালো লাগতেও পারে তোমার।
বেশ ঝলমলে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকি, দোতলায় উঠে যাই, ডানে সমুদ্র রেখে বসি, মনে হয় সমুদ্রে মাছের জো এসেছে, এক ঝাঁক মাছ ধরার নৌকো সারি বেধে গভীর সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যায়, কিছুক্ষণ পর একটা মাদার ভেসেল পোতাশ্রয় ছেড়ে যায়, সমুদ্রে থাকবে ওটা কয়েক হপ্তা, মাছ ধরার নৌকোগুলো মাছ ধরে ওটায় খালাস করবে। ফ্রিজিং, প্রসেসিং, প্যাকেজিং প্ল্যান্ট সবই আছে ওটার ভেতর। ওটা বোঝাই হয়ে গেলে সরাসরি ফ্রিজিং ভ্যানে ট্রান্সফার করবে, তারপর সেইলস সেন্টারে। সব ব্যবস্থাই স্বয়ংসম্পূর্ণ।
বিলেতের সীফুড আইটেমগুলো সম্পর্কে ভালো ধারণা হয় নি এখনো, দু’একটা গ্রীল চেখে দেখেছি, সস দিয়ে চালিয়ে দেয়া যায়, মেনু দেখি মন দিয়ে, বুঝতে না পেরে ছেড়ে দেই রল্ফের হাতে, খাবার-দাবারের দিক থেকে আমার অন্য প্রান্তে রল্ফ, যে-কোনো কিছু মুখে দিয়েই বলে ওয়াও, অথচ আমার জিভ গ্রহণ না করলে কোনো খাবার পেট পর্যন্ত খুশি মনে পৌঁছে দিতে পারি না।
অক্টোপাস ও স্কুইডের একটা সালাদ নেয় শুরুতে, সীউইড মিশিয়ে পরিবেশন করেছে, উপরে ওয়েস্টার সস ছড়ানো, সঙ্গে আরো কয়েকটা ছোটো ছোটো বোতল, বিভিন্ন স্বাদের সস। ওসব মিশিয়ে অক্টোপাসের একটা টুকরো চিবিয়ে গেলা যায়, কিন্তু স্কুইডটাকে কায়দা করতে পারি না, মুখ থেকে বের করে টিসু্য জড়িয়ে প্লেইটের কোনায় রেখে দেই, সীউইডগুলো ভালোই লাগে। বুঝতে পারে রল্ফ, ফ্রায়েড প্ল্যাইসের অর্ডার দেয় দুটো, টেবিলে আসতেই মজার গন্ধ, আমাদের পমফ্রেটের চেয়েও বেশি সুস্বাদু। সমুদ্রের তলায় বালু ও নুড়ির সঙ্গে মিশে থাকে, ফ্ল্যাট-ফিশ গোত্রের মাছ, রূপচাঁদা মাছের মতো একটা দিক চকচকে সাদা, অন্য দিকটা বিচিত্র রঙের, বালুকণা ও লাল নুড়ির সঙ্গে এটার পার্থক্য ধরা যায় না, শত্রু-মাছের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রাকৃতিক কৌশল। রল্ফের মনে হয় স্কুইড খাওয়ার ইচ্ছে, উঠে যেয়ে কাউন্টারে বলে আসে এক প্লেইট ওয়েলডান স্কুইড পাঠাতে। এক ইঞ্চি পুরু একটা পাউরুটি টোস্ট এতো মজা করে ভেজেছে কীভাবে বুঝতে পারি না, ভেতরটা নরোম, বাইরে মুচমুচে, ফ্লেভারটা ধরতে পারি না। একটু পড়ে গার্লিক সস দিয়ে রান্না করা অক্টোপাস ও স্কুইড নিয়ে আসে টেবিলে, স্কুইডটা সত্যিই মজা হয়েছে এবার। অক্টোপাস, যথারীতি ভালো লাগে নি। এর থেকে বরং কঙ্বাজারের রাখ্যাইনদের রান্না করা অক্টোপাস অথবা স্কুইডের স্বাদ অনেক ভালো। রে ফিস ফিন গ্রীল করে নিয়ে আসে দুটো, শালুকপাতা বা গোলমাছের মতো স্বাদ অনেকটা। কাঁটাগুলোও ওরকম মুচমুচে, ট্যাবাস্কো সসের সঙ্গে ভালোই লাগে। স্কটল্যান্ডের সমুদ্র তীরে বসে স্কচ না নেয়া তো ওদের প্রতি অবিচার, কাল রাতের কথা ভেবে ওটা বাদ দেই। রল্ফ বলে, তা কেনো, দু’হপ্তা নাহয় ড্রাই উইকস পালন করো। ঠিক আছে। স্কচ না নিয়ে লোকাল বিয়ার নেই? তাই সই। সবশেষে এলো আমাদের চ্যালা মাছের মতো দেখতে, একটু বড় হয়তো, সার্ডিন ফিসের বাচ্চা, ক্রিপ্সি ফ্রাই, দারুণ! যার শেষ ভালো তার সব ভালো, আমার মাথা দোলানো দেখে রল্ফ বলে, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে ‘লাস্ট আইটেম ফার্স্ট’ হলে ভালো হতো, তাই করো নাকি তোমরা? গলা ফাটিয়ে হেসে উঠতে যেয়ে আবার থেমে যাই। রল্ফ বলে, হাসো, হাসো, কেউ কিছু মনে করবে না এখানে, সবাই সি-ম্যান, নট এ-ম্যান! আটকে রাখা হাসিটা ছেড়ে দেই। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে বলে রল্ফ_
চলো হাঁটি। মন্দ লাগছে না, জড়তা কেটে যাচ্ছে।
প্রকৃতিই অভিজ্ঞ করে তোলে মানুষকে, পোতাশ্রয়ে পেঁৗছেই অন্য আবহাওয়ায় এসে পড়ি, অনেক শান্ত সমুদ্র, ছোটো ছোটো ঢেউ, অনেক বেশি উষ্ণ, তুমুল মাতাল বাতাস নেই, ঝাঁকে ঝাঁকে সীগাল উড়ে বেড়ায় অবাধে, মাছের অাঁষটে গন্ধ, পোতাশ্রয় জুড়ে শত শত মাছ-ধরা নৌকো, উদ্ধারকারী জাহাজ, তেল মোবিলের গন্ধ, সমুদ্রের জেলে পাড়ার একেবারে ভিন্ন পরিবেশ, মানুষগুলোও মনে হয় বিশালদেহী। ওপাশের পাহাড়ের গায়ে তিন চারতলা বাড়িগুলোর সবগুলোই পাহাড়ের মতো ঢালু, বাড়ির প্রতিটা তলা পাহাড়ের গায়ে পিছিয়ে যাওয়ায় প্রত্যেকটার সামনে রয়েছে সুন্দর ঝুলবারান্দা, ওগুলোর সামনে বর্ণিল টবে বিচিত্র রঙের ফুল ফুটে আছে। বাড়িগুলোর বেশির ভাগই হোটেল। মাছ-ধরার বিরতিতে, অথবা সমুদ্র অশান্ত থাকলে এখানেই কাটিয়ে দেয় জেলেরা। প্রমোদ যাপনেরও ব্যবস্থা আছে অনেক, পাব, ক্যাসিনো, কন্যা সবই আছে। পোতাশ্রয়ের কাছাকাছি ব্যাংক, পোস্ট অফিস প্রভৃতিও রয়েছে। যে-কোনো পর্যটকও সমুদ্রের স্বাদ পেতে কয়েকদিন কাটিয়ে যেতে পারে এখানে।
প্রায় মাইলখানেক লম্বা সেতুর মতো একটা রাস্তা পোতাশ্রয় থেকে সমুদ্রের ভেতর ঢুকে গেছে, শত শত খুঁটির উপর বসানো কংক্রিটের এই রাস্তাটা কেন বানানো হয়েছে বুঝতে পারি না, হেঁটে সমুদ্রের ভেতর ঢুকে পড়ি, ধারণা ছিল শেষ প্রান্তে হয়তো জেটির মতো কিছু আছে যেখানে বড় জাহাজ ভিড়তে পারে। রল্ফকে জিজ্ঞেস করি। ও বলে–
কোনো কারণ নেই, স্রেফ তোমার আমার হাঁটার জন্য।
কোটি কোটি টাকা খরচ করেছে এজন্য, ভালোই বলেছো।
ক্লান্ত হয়ে সীগালেরা যখন কূল পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে না তখন যেনো এখানে বিশ্রাম নিতে পারে, সে-জন্য আসলে।
কাল রাতে যে ব্র্যান্ডি নিয়েছিলে, ওগুলো বোধ হয় ঢোক গেলো নি রল্ফ, কণ্ঠে জমা রেখেছিলে, এখন গিলছো।
সেই ব্র্যান্ড হাসি!
জিজ্ঞেস করি–
শব্দ করে হাসতে পারো না রল্ফ? সীগালেরা শুনুক অন্তত।
নিশ্চয় হাসবো একদিন ডাউ, সীগালদের জন্য নয়, কারো জন্যই নয়, শুধু তোমার জন্য।
হায়! রল্ফের ঐ হাসি আর শোনা হয় নি এ জীবনে। রহস্যই রয়ে গেছে সে!
৮
বাড়িঘরের ছাদের চিমনিতে পায়রারা আসতে শুরু করেছে, গাছের কালো কঙ্কালে সবুজের ছোঁয়া, এতো দ্রুত আসে বসন্ত যে পরিবর্তনটা চোখে পড়ে খুব, দু’হপ্তার মধ্যে সব কিছু সবুজ, তারপর বিচিত্র রঙে সেজে ওঠে প্রকৃতি। শীতবস্ত্র সেইলের ধুম লেগেছে দোকানগুলোয়, ক’দিন পর দোকানের খালি জায়গাটা ভরে উঠবে আউটিংএর টেন্ট, প্যারাসল, গ্যাজেবো, বাইক প্রভৃতিতে। খাবার-দাবারের ওদিকটায় যোগ হবে রেডি-গ্রীল ফুড, চারকোল, চুল্লি এসব।
গ্রীষ্ম আসার আগেই আসে একটা সুসংবাদ, যে চাকরিটা পাই নি, তার চেয়েও ভালো একটা চাকরি পেয়েছি অক্সফোর্ডে, আরো একটা শীত-ঋতু এবারডিনের বরফের নিচে কাটাতে হবে না ভেবে উষ্ণ হয়ে উঠি সঙ্গে সঙ্গে, বলার অপেক্ষা রাখে না, কেরোলের খুশির পরিমাণ কতটা। ছোট্ট একটা টেলিচিঠি পাঠিয়েছে রল্ফ, ‘ অক্সফোর্ড ইজ ঈগার্লি ওয়েইটিং ফ’ হা’ বেস্ট ফরেইন ফ্রেইন্ড!’
মনে মনে হাসি, পাগল কত প্রকার!
কোরবিনকে বলি বাসা ছেড়ে দেয়ার কথা–
আশা করি আমার চেয়ে ভালো শ্রবণশক্তি-সম্পন্ন ভাড়াটে পাবে তুমি।
বিষয়টা উল্টো বোঝে, একটু অবাক হয়ে বলে–
কখনো কি জোরে বাজিয়েছি মি. এব্রাম?
ফার্স্ট নেইমে কোনোদিনও ডাকে নি সে আমাকে, আমিও মিস কোরবিন নামেই সম্বোধন করেছি সব সময়।
না না, উল্টোটাই বলতে চেয়েছি বরং, কখনোই তোমার বাদন শুনি নি।
তাই বলো।
মনে মনে বলি, অনেক দিন কান পেতে রেখেছি কি বাজাও শোনার জন্য। কিছুটা যেনো ভেবে বলে–
তোমার আগ্রহ থাকলে একদিন বসতে পারি।
নিশ্চয় আছে মিস কোরবিন।
তোমার যদি আপত্তি না থাকে যাওয়ার আগের দিন ডিনার নিতে পারো এখানে, তখন একটা সোনাটা বাজিয়ে শোনাবো নাহয়।
কোনো আপত্তি নেই, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। ঠিক আছে মিস কোরবিন।
মাঝে মাঝে বুঝতে পারি না আমি কি! এতদিন কাটিয়েছি এবারডিনে, অথচ এর কিছুই দেখা হয় নি, সপ্তাহ কেটেছে চাকরি ও থিসিস নিয়ে, সপ্তাহান্ত কেরোলে। যাওয়ার আগে ঘুরে-ফিরে দেখে যাবো পুরো শহরটা। চাকরি ছাড়ার নোটিশ দিয়েছি, যাওয়ার আগে পুরো দুটো দিন হাতে রেখে। অক্সফোর্ড ফেরার পর আরো এক হপ্তা পাওয়া যাবে কেরোলকে দেয়ার জন্য, সেও ছুটি বুক করেছে। আনন্দ! আহা একী আনন্দ! অনন্তকাল বেঁচে থাকো গুরু, আমাদের আবেগে উল্লাসে, সুখে দুঃখে, বীরত্বে নিবীর্যে, নিত্য-অনিত্যে!
স্কুলপাঠ্য কবিতায় পড়া বিখ্যাত ডী নদীর তীরে গড়ে উঠেছে নতুন এবারডিন (বিটউইন ডী এন্ড ডন), শহরের পুরোনো অংশ ডন নদীর তীরে মানব-বসতি শুরু হয়েছিল কম করে হলেও আট হাজার বছর আগে। প্রাচীন এই জনপদের ইতিহাস এই নদী দুটো ঘিরে পত্র-পল্লবিত ও মুকুলিত হয়েছে। বিখ্যাত বীর-যোদ্ধা রবার্ট দ্য ব্রুসের এই শহরের রয়েছে অন্য আরো অনেক নাম। স্কটিশ ও ইংলিশদের মধ্যে অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছে এ শহরের কর্তৃত্ব নিয়ে। এখানের গ্রানাইট পাথর খুব উঁচু মানের, এসব পাথরের সঙ্গে মাইকা-চূর্ণ মেশানো থাকায় পাথরগুলো মসৃণ করার পর রূপোর মতো চকচকে দেখায়। শহরের অনেক ভবন এসব গ্রানাইট পাথরে তৈরি হওয়ায় শহরটাকে সিলভার সিটি অথবা গ্রে সিটি নামে ডাকা হয়। সোনালি বালুর অপরূপ সমুদ্র সৈকতের তীরে গড়ে ওঠা এই শহরের মাটির নিচে রয়েছে তরল সোনার বিশাল মওজুদ, এজন্য এটাকে ইউরোপের অয়েল ক্যাপিটাল, অথবা কখনো এনার্জি ক্যাপিটাল নামেও ডাকা হয়। এখানের হেলিপোর্ট পৃথিবীর অনেক ব্যস্ততম হেলিপোর্টের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, এর সমুদ্র-বন্দর উত্তর-পূর্ব স্কটল্যান্ডের সব চেয়ে বড় ও বিখ্যাত বন্দর। পাঁচশ’ বছরেরও বেশি পুরোনো এবারডিন বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যাশিক্ষায় জড়িতদের জন্য এক পূণ্যভূমি, এখানে ঘুরে ঘুরে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ি, দুপুরের খাবার খেয়ে নেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্টিনে বসে। এর পর ঘণ্টা দুয়েকের জন্য ঘুরে দেখি রবার্ট গর্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, এই প্রথম এলাম এখানে, এর ভবনগুলো ও পরিবেশ চমৎকার। ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরি, ছোট্ট একটা ঘুম দেই।
হাফ ক্যাজুয়্যাল, প্রায় ফর্মাল একটা পোশাক পরে নিচে নেমে আসি কোরবিনকে দেয়া সময় ঠিক চারটায়, অক্সফোর্ডের প্রথম বাড়িওয়ালির বিষয়টা মনে রেখে মনে মনে ভয় ছিল দেরিতে গেলে যদি কিছু খেতে না দেয়, কাল চলে যাবো বলে ঘরের খাবার দাবার সব শেষ করে ফেলেছি। সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে দেখি ডাইনিং টেবিলের কোনা ধরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে কোরবিন।
হ্যালো, মিস কোরবিন, কেমন আছো?
ভালো, খুব ভালো, ধন্যবাদ তোমাকে, তুমি কেমন আছো?
আমিও ভালো, তোমাকেও ধন্যবাদ।
আসো, বসো এখানটায়।
ঠিক আছে, ধন্যবাদ।
ফুলের তোড়াটা ওর হাতে দেই, চকোলেট বা ওয়াইন কিছুই আনি নি, কি খায়, তাই তো জানি না, কখনো টেবিলে দেখি নি ওকে। ধন্যবাদ, বলে ভেতরে যায়, বড় একটা ফুলদানী সাজিয়ে টেবিলে রাখে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে ওগুলো। বলে, খুব সুন্দর ফুলগুলো।
তেত্রিশ আরপিএমের একটা যন্ত্রসংগীতের রেকর্ড এনেছিলাম, রবীন্দ্রসংগীতের, বিশেষ করে ‘গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথে’ গানের সুরটার জন্য, ডিস্কটা ওর হাতে দিয়ে বলি, কিছুক্ষণের জন্য এটা বাজানো যায়?
নিশ্চয়, বলে রেকর্ড-প্লেয়ারে চাপিয়ে দেয়।
এতো মুগ্ধ হয়ে শুনবে এটা বুঝতে পারি নি, ওর সবটুকু মনোযোগ হয়তো এখন ঐ সুরের উৎস খোঁজায় নিয়োজিত।
এরকম সুর শুনেছি নিশ্চয়, কার বল তো?
আমার গুরুর।
তোমার গুরু? গানও শিখেছো, বাহ্, শোনাবে নাকি একটা?
আমার গুরু মানে, আমাদের বাঙালি জাতির কবিগুরু, তোমাদের যেমন শেক্সপীয়র, জার্মানদের গ্যেটে, রাশানদের পুশকিন, ইরানিদের ফেরদৌসি, এরকম।
বাহ্, কি যেনো নাম?
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ট্যাগোর বলো তোমরা।
হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি। তোমাদের একজন বড় কবি।
শুধু আমাদেরই নয়, বিশ্বেরই একজন বড় কবি।
হ্যাঁ, নিশ্চয়, তিনি একজন বিশ্বমানের কবি, তাঁর দু’একটা অর্কেস্ট্রা শুনেছি মনে হয়।
সুরায় মাতাল হয় কেউ, আবার অনেকে সুরে, অথবা সংগীতে। কোরবিনের ঘোর লেগেছে সুরে, গত ক’মাসেও এতো কথা বলে নি, আজ বিকেলে সব শোধ করে দিচ্ছে। সেজেছে দারুণ, মনেই হয় না বয়স ওর চল্লিশ ছুঁয়েছে, কোনাকোনি সাজানো ব্লুবেল ফুলের ছাপ দেয়া কাপড়ের গাউন, প্রিমরোজ রঙের হাফ-হাতা সার্টের বুকের কাছটায় ছোট ছোট পুঁতির নক্সা, অনেকটা গহনার মতো, গোলাপি মুক্তো রঙের লিপস্টিক, সাদায় সোনালি মেশানো চুলগুলো কানের দু’পাশ থেকে চিকন দুটো বেণি গেঁথে পেছনে বাঁধা, এতো সাধারণ, অথচ অপরূপ, মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকার মতো।
দ্রুত লয়ের ‘সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি’ গানের বাজনা শুরু হলে লাফিয়ে ওঠে–
আমার তো নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে, এটা কি কোনো নাচের সুর?
টেগোরের প্রায় সব গানের সঙ্গেই নাচা যায়। এটা একটা অসাধারণ গান।
বাহ্, আরো শুনবো টেগোরের মিউজিক, খুব ভালো লাগছে। এখানে কোথায় পাওয়া যায় জানো?
জানা উচিত ছিল। এই রেকর্ডটা দেশ থেকে নিয়ে এসেছি, রেখে দিতে পারো। স্পুলে অনেক রবীন্দ্রসংগীত আছে আমার।
না না, আমি সংগ্রহ করে নেবো, তোমাকে ধন্যবাদ।
এখানকার হেইচএমবিতে খোঁজ করতে পারো, স্টকে না থাকলেও সংগ্রহ করে দিতে পারবে আশা করি।
ভালো বলেছো, তাই করবো।
প্লেয়ারে ‘আমি চিনি গো চিনি তোমারে’ শুরু হলে বলে–
ঠিকই তো বলেছো, এটার সঙ্গেও নাচা যায়, সালসা ড্যান্সের অনেক সুর আছে এটার মতো! বাহ্!
ঘড়িতে পাঁচটা বাজতেই জিজ্ঞেস করে–
খাবার নেবো?
নিতে পারো।
ড্রিঙ্কস কি নেবো, তুমি নিশ্চয় এলকোহোলিক কিছু নেবে না।
নেবো, নেবো।
অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে–
তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ না এটা, তুমি নাও?
অনেকেই নেয়।
তা জানি। আমি ভেবেছি তুমি নাও না, কোনো ড্রিঙ্কস আনি নি, ক্রিসমাসে পাওয়া কয়েক বোতল ওয়াইন আছে, নেবে কোনোটা?
নিতে পারি।
তাহলে একটু কষ্ট করো, এখানে আসো, তোমার পছন্দ মতো বেছে নাও।
ওয়াইনর্যাক দেখে রীতিমতো অবাক হই! জিজ্ঞেস করি–
এতো ওয়াইন!
আর বলো না, গিফট হিসাবে যত পাই, সবই রেখে দেই, পুরোনো হলে দামি হয় কিনা . . . কেমন ব্যতিক্রম, তাই না?
হ্যাঁ তাই . . . ব্যতিক্রম তো আছে সবকিছুতেই। তা এতো ওয়াইন জমাচ্ছো কার জন্য!
কারো জন্যই না। তোমার মতো কেউ যদি হঠাৎ এসে যায়, দু’একটা কাজে লাগে।
ফাইভ ঔকসের একটা রেড ওয়াইন নেই, ক্যালিফোর্নিয়ান। বোতল ঝেড়ে-মুছে টেবিলে রাখি। সোনালি কাচের দুটো বড় ওয়াইন গ্লাস নামিয়ে আনে কোরবিন। বলে–
থ্রী কৌর্স ডিনার, তোমার কি পছন্দ জানি না, তাই খুব কমন ক’টা আইটেম, এবং খুব সাদামাটা। কিছু মনে করো না।
বলো কি? টু কৌর্সই সামলাতে পারি না!
মাঝখানে একটা করে গ্যাপ রেখো।
হেসে উঠি। কি জন্য?
স্টার্টার নিয়ে আসে। মধু, আদা ও থাইম দিয়ে গ্রীল্ড ডাক-ব্রেস্ট, প্লেইটের পাশে রকেট মেশানো গ্রীন সালাদ। এক টুকরো মাংস মুখে দিয়ে দেখি চমৎকার স্বাদ।
বেশ ভালো রান্না করো তুমি মিস কোরবিন।
মনে হয় না।
গুরুঠাকুরের সুরের ইন্দ্রজাল ঘরটাকে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছে, একটা জীবন তো এই মধুর হাওয়ায় ভেসেই কাটিয়ে দেয়া যায়! ওয়াইনটা দারুণ, বোতলটা হাতে নিয়ে ইয়ার অব প্রোডাকশান দেখি, খুব বেশি পুরোনো না, আমার কিশোর কালের, তবে ক্যালিফোর্নিয়ার ঔক গাছগুলো যে আমাদের চন্দন থেকে মিষ্টি সুবাস নিয়েছে বোঝা যায়, ফ্লেবারটা চমৎকার, ওয়াইনের সঙ্গে এর গন্ধটাও নিতে হয়, তাহলে পুরো স্বাদ পাওয়া যায়, গ্লাসটা ঠোঁটে না নিয়ে কয়েকবার গন্ধ শোঁকায় কোরবিন বলে–
কি হে, গন্ধে মাতাল?
বলো না, মাতাল হওয়ার জন্য আমার নির্দিষ্ট কিছু দরকার পড়ে না। আমার একটা গল্প বলি শোনো, তখন হাই স্কুলে উঠেছি মাত্র, আমাদের দেশে মৌসুমি একটা ফল জন্মায়, এই এতো বড়, তোমার এই টেবিল পুরোটাই জুড়ে যাবে, সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফল ওটা, গাছ থেকে একটা কাঁঠাল নামিয়েছি, খাজা কাঁঠাল, খাওয়া শুরু করেছি তো আর শেষ করি না দেখে বাবা বলে, পেটে অসুখ করবে, শেষে কাঁঠালের একটা বীচি জোর করে খাইয়ে দেয়, পুরো ঐ মৌসুমটা মাতালের মতো কাঁঠাল খেয়েই কাটিয়েছি, এর পরের বছর থেকে কাঁঠালের গন্ধটাই তেমন ভালো লাগে নি আর, এখনো খাই মাঝে মাঝে, ভালো ফ্লেবার হলে, তবে খুব কম।
আমার মনে হয় ফাইভ ঔকসের বোতল আর ঘরে নেই, তোমাকে যোগান দেয়া যাবে না।
জোরে হাসতে যেয়ে সামলে নেই, সে তো মিস কোরবিন!
রেকর্ডের দুটো পিঠ বাজানো শেষ হলে জিজ্ঞেস করি–
ভারতীয় সংগীত কেমন লাগে তোমার?
খুব বেশি শুনি নি।
বেশ ক’জন উচ্চাঙ্গের শিল্পী আছেন আমাদের, শুনবে?
শোনা যায়।
দৌড়ে উপরে উঠে যাই, ওস্তাদ আয়েত আলী ও পণ্ডিত রবিশঙ্করের দুটো রেকর্ড নিয়ে নেমে আসি। রবিশঙ্করের সেতার শুরু হলে একেবারে স্তব্ধ হয়ে থাকে কোরবিন, সুরের ইন্দ্রজালে জড়িয়ে হারিয়ে যায়, বাজানো শেষ হওয়ার পরও কথা বলতে পারে না অনেকক্ষণ, সত্যিই এক সংগীত-রসিক, ওকে এটা শোনাতে পেরে খুব আনন্দ পাই। মেইন কৌর্স ডিনারের পর বলি–
এবার শোনো ওস্তাদের বাজনা।
পুরো রেকর্ডটা বাজানো শেষ না হওয়া পর্যন্ত মনে হয় না একবারও চোখ খুলেছে সে। এসব সুর মানুষকে প্রকৃত অর্থেই অন্য জগতে নিয়ে যায়। প্রকৃতিস্থ হয়ে বলে–
কেন এসব শুনি নি আগে! এসব কি ওদেরই কম্পোজিশান?
নিশ্চয়।
এঁদের অবস্থান তো মোজার্ট, বাখ, বিটোফেনের পাশে হওয়া উচিত।
হয়তো, এঁরা ইউরোপীয় হলে ব্যাপক পরিচিতি পেতেন নিঃসন্দেহে, তবে গুণীজনেরা জানেন এঁদের।
শিল্প তো শুধু গুণীজনদের জন্যই না, সবারই অধিকার রয়েছে এতে।
দরিদ্রের শিল্প হচ্ছে, কুটির শিল্প, মিস কোরবিন!
হো হো!
অনগ্রসর সমাজে জন্মানো শিল্পীদের এটা একটা বড় সমস্যা কোরবিন। যাহোক, এবার তোমার বাজানো শুনবো?
বলো কি মি. এব্রা’ম, এসব শোনার পর বাজানোর সাহস নেই আমার।
না কোরবিন, তোমারটা তোমারই।
ঠিক আছে, ডেজার্টের পর বাজাবো, সব শেষে। যেনো দৌড়ে পালাতে পারো তুমি।
হো হো হো।
আর সামলাতে পারলাম না হাসিটা। কোরবিনকেও এই প্রথম দেখলাম গলা ছেড়ে হাসতে, বড়ো ভালো লাগে, ভেতরের টুকরো পাথরগুলো ছুটে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে।
ডেজার্ট ওয়াইনে ডোবানো রঙবেরঙের ফলের টুকরোগুলো অসাধারণ, চোখ-জুড়ানো, মুখে তুলতে ইচ্ছে হয় না। তাকিয়ে আছি দেখে বলে–
নেবে না? আইসক্রিম দেই তাহলে…
আরে না না, এটার সৌন্দর্যে মুগ্ধ আমি, খাবো কি!
তাহলে তো সত্যিই পিয়ানোয় বসতে হচ্ছে আমাকে।
হা হা, বসো বসো, বলে একটা স্ট্রবেরির টুকরো মুখে দেই।
বাজানো শুরু করে এডোয়ার্ড গ্রেইগের ইংলিশ স্ট্রিং অর্কেষ্ট্রার একটা সুর। শেষ হলে বলি, হাত তালি দিয়ে সুরের আবেশটা নষ্ট করতে চাই না, অসাধারণ বাজিয়েছো। একটু হাসে। কিছুটা দ্রুতলয়ের একটা সোনাটা বাজায়, ব্যাখ্যা করার পরও সুরটা ধরতে পারি না। এরপর বি ফ্ল্যাট ম্যাজোর স্কেইলে হ্যান্ডেলের ভায়োলিন কনসার্টোর সুর বাজিয়ে শেষ করে দেয় কোরবিন। বলি–
আর হয়তো কোনোদিন এখানে শোনা হবে না তোমাকে। বাজাও না আর কিছু।
আর কিছু বাজাতে বলো না আমাকে, প্লীজ।
কবিগুরুর ‘আমায় বলো না গাহিতে বলো না’ গানটা মনে পড়ে। চাপাচাপি করতে সাহস হয় না, গভীর গোপন দুঃখ সবারই থাকে। ডেজার্টের পেয়ালা শেষ করি। যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বলি–
আমি বাজাতে জানি না কোরবিন, না হলে কিছু একটা বাজিয়ে শোনাতাম নিশ্চয়। দু’কলি গান শোনাতে পারি, শুনবে?
সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ প্রকাশ করে–
নিশ্চয়, নিশ্চয়।
যদিও ওর উদ্দেশ্যে নয়, এবং বুঝবেও না সে এ গানের সুগভীর বাণী, শোনাই ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা’ গানটি। শেষ হওয়ার পর বলে–
অসাধারণ তোমার গলা মি. এব্রাম, খুব ভালো লাগলো।
গলা অসাধারণ নয়, গানটার সুর অসাধারণ।
কি জানি কি মনে করে নিজেই উঠে যেয়ে বসে পিয়ানোয়। এটা বাজানো শেষ হলে চলে যেও।
ঠিক আছে।
মুগ্ধ হয়ে যাই, তন্ময় হয়ে থাকি, শিশু হয়ে যাই, বুঝতে পারি না কার রচনা এটা, মনে হয় অনেক দূরে, সুদূর আকাশের কোনো নক্ষত্র কাঁদছে ডুকরে ডুকরে। এতো দুঃখ, এতো দুঃখ! সুরের ভেতর কীকরে জমানো যায় চোখের এতো জল, বুকের এতো যন্ত্রণা, ভেবে পাই না। বসা থেকে উঠে দাঁড়াতে পারি না, পাশ থেকে দেখি কেরোলের চোখ দুটো জলে-ভরা। সকল সৌষ্ঠব ভুলে ওর কাছে যাই, মানবিক আবেদনের কাছে কোনো বাধাই বাধা নয়। বলে–
তোমাকে চলে যেতে বলেছিলাম।
দুঃখিত, ক্ষমা চাইছি এ জন্য কোরবিন।
ঠিক আছে।
আবারো ক্ষমা চাইছি, তোমার হাত দুটো ধরতে অনুমতি দেবে, একবার?
পালকহীন এক পাখি-ছানার মতো আমার করতলের ভেতর কাঁপে ওদুটো, আমি সত্যিই দুঃখিত কোরবিন। তোমাকে দুঃখ দেয়ার কোনো ইচ্ছে সত্যিই ছিল না আমার, বুঝতে পারি নি, সত্যিই বুঝতে পারি নি, তোমাকে শেষবার বাজাতে অনুরোধ করা উচিত হয় নি আমার।
একটু সংযত হয় কোরবিন।
মাপ করো ডেয়ুড, আবেগ সামলাতে পারি নি, ওকে ছাড়া এ সুরটা অন্য কারো জন্য আর বাজাই নি, ভুলেই গেছিলাম যে অন্য সময়ে বাস করছি এখন!
এই প্রথম আমার প্রথম নাম ধরে ডাকে কোরবিন, একটু অবাক হই। না বুঝে ভুল জায়গায় হাত দিয়ে ফেলেছি, এখন ওর কষ্টটা ঘুচাই কীভাবে বুঝতে পারি না। বলি_
এখন ঘুমোতে যাও কোরবিন, অনেক রাত হয়েছে, ভোরে আবার এয়ারপোর্টে যেতে হবে আমাকে, আমার গার্লফ্রেইন্ড আসবে, রিসিভ করতে হবে ওকে।
আকস্মিক একটা কালো ছায়া বাদুড়পাখার মতো বয়ে যায় যেনো ওর সুন্দর মুখের উপর দিয়ে, মনের ভেতরটা বোঝা যায় না। স্বাভাবিক হয়ে বলে_
তাহলে কালই চলে যাচ্ছো কেন? পুরো হপ্তার ভাড়াই তো দিয়েছো, আরো দুটো রাত কাটিয়ে যাও এখানে।
দেখা যাক। কেরোলের সঙ্গে কথা বলে দেখি, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে লিজ, ওর প্রথম নামটাই ব্যবহার করি।
ঠিক আছে ডেয়ুড, শুভরাত্রি।
শুভরাত্রি . . . ।
ঘরে এসে ঘুমোতে চেষ্টা করি, কোনোভাবেই ঘুম আসে না। ‘আমায় বলো না গাহিতে বলো না’ গানটা শুনি আবার, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি, গান শোনানোর জন্য অথবা কোনো সুর বাজানোর জন্য কখনোই চাপ দেবো না আর কাউকে।
সকালে কেরোলকে নিয়ে ঘরে ফিরে দেখি নিচে বসে আছে কোরবিন।
সুপ্রভাত।
সুপ্রভাত মিস কোরবিন। ও কেরোল।
হ্যাঁ বলেছো, ও আসবে আজ, আসো কেরোল, বসো এখানে।
ঠিক আছে, ধন্যবাদ মিস কোরবিন।
কোরবিনকে দেখে রীতিমতো অবাক হই! দু’চার না, মনে হয় দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে এক রাতে। একটুও প্রসাধন নেই মুখে, বলিরেখা স্পষ্ট, হালকা নীল রঙের একটা সাদামাটা পোশাক, এতোদিন বুঝতেই পারি নি বয়স ওর চলি্লশ পেরিয়েছে, মোটা ফ্রেমের একটা চশমা পরেছে চোখে, আরো বয়স্ক দেখায় এতে। বিস্মিত হয়ে মনে মনে ভাবি, মেয়েরা বোধ হয় ভালোভাবেই জানে কার কাছে কীভাবে উপস্থাপন করতে হবে নিজেকে। কেরোলের মনে যেনো সামান্য ভাবনারও উদয় না হয় সেজন্যই হয়তো বুড়িয়ে যাওয়া এই রূপ! যাকগে, কিছু করার নেই, কাল রাতে দেয়া কষ্টের বিপরীতে সুযোগ পেলে একদিন এসে নাহয় কিছুটা আনন্দ দিয়ে যাবো।
আমার লাগেজ অতিরিক্ত হয়ে যাবে বলে একেবারে খালি হাতে এসেছে কেরোল, ফেরার টিকিটও করে এসেছে, থাকা আর হচ্ছে না, রাতেই ফিরবো, স্যুটকেইসগুলো গুছিয়ে বেরিয়ে পড়ি কেরোলকে নিয়ে, নতুনরূপে দেখি এবারডিন। কোথায় ছিল এ নগরের লুকিয়ে রাখা এই সৌন্দর্য এতদিন! কালরাতের হঠাৎ ঝড়ে পাওয়া ছোট্ট একটা ছন্দপতনের পর নতুনভাবে ফিরে আসে পুরোনো আনন্দনৃত্যের দোলা, মুক্ত বিহঙ্গের মতো ভেসে যাই অবাধ আলোর ‘মেঘবিহীন আমাদের উজ্জ্বল আকাশে’।
সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আসি, বেরিয়ে আসার প্রস্তুতি শেষ করে কেরোলকে বলি–
একটা মিনিট বসো প্লীজ, মিস কোরবিনের কাছ থেকে ফর্মালি বিদায় নিয়ে আসি।
নিশ্চয়।
নিচে এসে দেখি বসে আছে কোরবিন। বলি–
একটু পরেই বেরিয়ে যাবো আমরা, তোমার সৌহার্দের জন্য অনেক ধন্যবাদ, লিজেট। অনেক সুখে ছিলাম তোমার এখানে।
ধন্যবাদ মি. এব্রাম, নিশ্চয় বলতে পারি আপনিও কোনো অসুখের কারণ ঘটান নি আমার, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, আপনার শুভ কামনা করবো সব সময়।
সেই পুরোনো মিস কোরবিন!
ঠিক আছে মিস কোরবিন, একটা ছোট্ট অনুরোধ জানাতে এসেছি, অনুমতি দিন তো . . .
নিশ্চয়।
যদি কখনো আপনার বাজনা শোনাতে ইচ্ছে হয় কাউকে, নিশ্চিন্তে স্মরণ করতে পারেন, এখানে ঠিকানা লেখা আছে আমার।
ভাঁজ করা কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে বলে–
অনেক ধন্যবাদ মি. এব্রাম, আপনি অনেক উদার ও চিত্তবান।
ভালো থাকবেন মিস কোরবিন।
উপরে উঠে কেরোল সহ ধরাধরি করে বইপত্র, ব্যাগ, স্যুটকেইস নামিয়ে আনি, ট্যাক্সিও এসে দাঁড়িয়েছে।
শুভরাত্রি মিস কোরবিন।
শুভরাত্রি, বাই।
বাই।
বাসে উঠে ঘুমিয়ে পড়ি দু’জনেই, গভীর ঘুম, মনে হয় একটু পরেই পৌঁছে গেছি অক্সফোর্ড । অনেকটা বাড়ি ফেরার আনন্দ যেনো, চেনা পথ ঘাট, দোকানপাট, ছোট বড় সব ভবন, গাছপালা সবকিছুই অতি-চেনা। রল্ফ যে এতটা নাটকীয়তা করবে ভাবতেই পারি নি, এই সাত সকালে ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে বাস স্টেশানে এসেছে অভ্যর্থনা জানাতে! ধন্যবাদ কি আর দেবো ওকে, বলি–
এসব কি রল্ফ?
অক্সফোর্ডের ছেলে ফিরে এসেছে, স্বাগত জানাতে হবে না?
কি আর বলি, ধন্যবাদ জানিয়ে ফুলের তোড়াটা নিয়ে কেরোলের হাতে দেই। ট্যাক্সির জন্য ফোন করতে হয় না, রেডি রেখেছে রল্ফ। ঘরে ফিরে আরো এক চমক, হয়তো চমকের বদলে চমক! ঘরের দরোজা জানালার পর্দা, বিছানার চাদর বালিশ সব নতুন, বাথরুম, কিচেনে নতুন নতুন গেজেট, ঢাউস একটা গানের যন্ত্র কিনেছে, সব মিলিয়ে দেখি জীবনের বিচিত্র সব আয়োজন! ভালোই, এভাবেই যেনো ঢেউয়ের দোলায় এগিয়ে যায় জীবন-তরী।
ছুটির প্রথম দু’টা দিন পুরো অবসরে কাটাই, গান শুনে, পান-ভোজন করে, এবং কেরোলের মধু-সঙ্গ যাপন করে। তৃতীয় রাতে একটা আড্ডার আয়োজন করে রল্ফ, দীর্ঘ আড্ডার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে সে, এদের আড্ডা আবার বাসায় জমে না, পাবে বা রেস্টুরেন্টে, আমার ভালো লাগে ঘরের ভেতর, ঢিলেঢালা পোশাকে, সহজ চলাফেরার ভেতর, ইচ্ছে মতো খাওয়া দাওয়া, ওঠা বসার ভেতর আড্ডা চালিয়ে যাওয়া, মেনে নেয় রল্ফ, বাইরে থেকে খাবার ও ড্রিঙ্কস নিয়ে আসবে সে, রাজি হয়ে যাই।
ঘরে এসেই বলে–
গান শুনবো আজ। তোমাদের জন্য একটা ডিস্ক কিনেছি।
রেকর্ডটা কেরোলের হাতে দিয়ে বাজাতে বলে। আলেকজান্ডার জেমলিন্সকির কম্পোজ করা লিরিক সিম্ফনি, রবীন্দ্রনাথের কবিতার সুর করা অসাধারণ অর্কেষ্ট্রা, এত জীবন্ত কম্পোজিশান, নতুন যন্ত্রটাও এত পাওয়ারফুল, মনে হয় ঘরের ভেতরই যেন গোটা একটা দল ঢুকে পড়েছে। মুগ্ধ হয়ে শোনে কেরোল, বলে_
আমি জানতামই না এটা সম্পর্কে ডাউ, বলো নি কেন আগে?
টেগোরের নিজের গাওয়া গান শুনিয়েছি তোমাকে, এর চেয়ে বেশি কি আর পারতাম?
মিটি মিটি হাসে রল্ফ।
বুঝেছো কেরোল, তোমাকে এটা দেয়ায় ঈর্ষা হচ্ছে ডেয়ুডের।
মোটেও না কেরোল। আর আমি না দিলেও আমারি এক বন্ধুই তো দিয়েছে এটা।
ঠিক আছে, ঠিক আছে, বন্ধুর সাফাই গাইতে হবে না, বাজনাটা শোনো মন দিয়ে।
রেকর্ডের এক পিঠ শেষ হলে ঘুরিয়ে অন্য পিঠ চাপিয়ে দেয় কেরোল। এই ফাঁকে রল্ফের আনা খাবার-দাবার সামনে এনে রাখে, সব চেয়ে বড়, দেড় লিটারের এক বোতল জার্মান ভোদকা এনেছে, বেশ কয়েক রকম জ্যুস ও আইস-কিউব সাজিয়ে রাখে, মনে হচ্ছে রাতটা জমবে বেশ। এক ঢোক প্লেইন ভোদকা গলায় ঢেলে বলে রল্ফ_
সেদিন নীৎসে নিয়ে কথা বলা শুরু করেছিলাম, শেষ করতে পারি নি, অন্য দিকে ঘুরে যায় সব।
আবার নীৎসে! মেজাজটা একটু বিগড়ে যায়, বলি–
তোমার সমস্যাটা কি রল্ফ? নীৎসে বিষয়ে আলোচনা করার কি আছে? ওর বইগুলো পড়ে নাও, ওর সম্পর্কে যদি এতোই আগ্রহ থাকে তোমার।
ওর সব বইই পড়েছি।
তাহলে ওর বিষয়ে যেসব আলোচনা আছে সেগুলো পড়ো, নীৎসে যা লিখেছে তার চেয়ে অনেক অনেকগুণ বেশি লেখালেখি আছে ওর বিষয়ে।
একটু যেনো দমে যায় রল্ফ। কেরোল বলে–
সেদিন বাসে যেতে যেতে দ্য হোলি ব্লাড এন্ড দ্য হোলি গ্রেইল সম্পর্কে পড়ছিলাম, বেশ ইন্টারেস্টিং, তোমাদের আগ্রহ থাকলে এটা নিয়ে কথা বলতে পারো, হয়তো যোগ দিতে পারবো আমিও।
আমার নেই, বলি আমি।
আমার আছে, প্লেইটে একটা চিকেনের টুকরো রাখতে যেয়ে বলে রল্ফ।
হ্যাঁ, তা তো থাকবেই তোমার, যেহেতু আমার নেই।
ঝগড়া না করে থাকতে পারো না তোমরা?
ঝগড়া আমি করি না, বলে রল্ফ।
আসলে হোলি গ্রেইল বিষয়টাতে প্রায় কিছুই জানি না আমি।
তাহলে তোমার ভালোই লাগবে ডাউ।
ঠিক আছে, বিষয়টা একটু বুঝিয়ে বলো দেখি কেরোল।
এটা অনেকটা কিংবদন্তীর মতো। কিং ডেইভিডের উত্তরসূরি, যেসাসের পরিবার, তাঁর ক্রুসিফিকেশান হওয়া-না-হওয়া, কিং আর্থারের পরিবারচক্র, এসবের এক জটিল ও আশ্চর্য মিশেল, বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছে বিভিন্নজনে, এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে অথবা কথা বলে কিছু একটা ধারণা করা যায় হয়তো, কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। তবে বিষয়টা ইন্টারেস্টিং, নবীদের ধারণা গড়ে ওঠার সময়টাকে কিছুটা ধরা যায়।
গ্রেইল জিনিসটা কি?
কারো কারো বর্ণনায় এটা একটা পাত্র, যেখানে ক্রুসিফাইড যীশুর রক্ত ধারণ করা হয়েছিল, কারো ব্যাখ্যায় এটা লাস্ট সাপারের পাত্র, হতে পারে কোনো ডিস, প্লেইট বা বাটি। ধরে নেয়া হয় অলৌকিক ক্ষমতা আছে এটার, বারো শতকে হোলি গ্রেইল বিষয়টার উৎপত্তি ধরা হয়, হোলি চেলিসের সঙ্গেও এই কিংবদন্তী যুক্ত হয়েছে।
হোলি চেলিস?
হ্যাঁ, মহামান্য পোপ এটার রক্ষাকর্তা এখন, খুব দামী পাথরে তৈরি। যাহোক, রোমান সম্রাট যখন খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করে অনুসারীদের নিয়ে, প্রজাদেরও তা করতে হয়। রাজার ধর্মই প্রজার ধর্ম! হো হো হো। রোমান সম্রাট খুব ভালোভাবে বুঝতে পারেন যে সাম্রাজ্যের সাধারণ ঐক্যের জন্য ধর্মটাকে খুব ভালো হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগ করা যায়। ওদের সামনে ছিল তখন মুসলমানদের ধর্মীয় ঐক্যের বলিষ্ঠ উদাহরণ, ইসলামের পতাকাতলে প্রায় পুরো বিশ্ব পদানত করতে যাচ্ছে ওরা! রোমানদের নতুন করে পাওয়া এই খ্রীস্ট-ধর্ম ছড়িয়ে দেয়ার কাজে হাজার হাজার নাইট টেম্পলার্স জড়িত ছিল, এদের সঙ্গে সম্রাটের একটা ভারসাম্য অবস্থা বজায় ছিল।
হ্যাঁ, মাঝখানে ওটা আবার নষ্টও হয়ে যায়, কর্তৃত্বের প্রশ্নে।
ঠিকই বলেছো রল্ফ, ধর্মীয় গোপনতা জনগণের কাছে ফাঁস করে দেয়ার হুমকি দেয় নাইট টেম্পলার্সরা। বারো শতকে নাইট টেম্পলার্সদের নিশ্চিহ্ন করা শুরু হলে ওদের অনেকে পালিয়ে এবারডিনে এসে সেইন্ট মেরিস চ্যাপেল প্রতিষ্ঠা করে, ওখানে স্থাপন করে হোলি গ্রেইল। এটা জানতে পেরে স্কটল্যান্ডের পথে বিশাল এক বহর পাঠনো হয়। খবর পেয়ে নাইট টেম্পলার্সরা আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে কানাডার নোভা স্কোশিয়ায় গোপন করে ওটা। তুষার-জমা এমন এক জায়গায় লুকিয়ে রাখে ওটা যে ওখানটা যদি কেউ খনন করতে যায় তাহলে যারা খনন করবে ওরা আটলান্টিকে ভেসে যাবে, ওভাবেই ওটা নির্মাণ করা হয়েছে।
আর ঐ হোলি চেলিস?
মুসলমানদের আগ্রাসী আক্রমণ থেকে হোলি চেলিস নিয়ে খ্রীস্টান যাজকেরা পালিয়ে বেরিয়েছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দেশে। কোনো এক গির্জায় আছে এখন এটা, পোপ বেনিডিক্ট জানেন। রহস্যটার নিষ্পত্তি হয় নি ডাউ, আমিও ঠিক বলতে পারছি না, আর এ পর্যন্ত যা বলেছি তাও ঠিক কিনা আমিও জানি না। হো হো হো। এর সবই গুজব, বিশ্বাস করা যায় না, আবার ঠিক হতেও পারে কোনো কোনোটা। অনেক বই লেখা হয়েছে এ নিয়ে, চলচ্চিত্র হচ্ছে, রহস্য অনুসন্ধানীরা হোলি গ্রেইল খুঁজে বেরাচ্ছে!
তুমি লুকিয়ে রাখো নি তো ডাউ?
তোমার মতো ইহুদি গোয়েন্দা রয়েছে যেখানে আমার সাধ্য কি?
ঝগড়া করে না, বাচ্চারা।
হো হো হো।
অনেক ধন্যবাদ কেরোল কিছুটা ধারণা পেলাম।
যদি ইন্টারেস্টেড হও ড্যান ব্রাউনের দ্য ভিঞ্চি কৌড বইটা পড়তে পারো।
কি আছে ওখানে?
হোলি গ্রেইলটা কোনো পাত্র নয়, বরং মেরি ম্যাগডালেনের (যেশাসের স্ত্রী?) গর্ভ! বেশ কিছু ঐতিহাসিক তথ্য তুলে ধরে বলা হয়েছে যীশু ছিলেন অনেক উচ্চ-ধারণাসম্পন্ন একজন সাধারণ মানুষ। যীশুর শিক্ষা, তাঁর জীবন ও প্রজন্ম সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য ও যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। স্কটল্যান্ডের রোসলিন চ্যাপেলের নিচে হোলি গ্রেইল সমাধিস্ত রয়েছে। সমপ্রতি আবার বলা হচ্ছে ফ্রান্সের লু্যভর মিউজিয়ামের কাছে নির্মিত ইনভার্টেড পিরামিডের নিচে কোথাও লুকানো আছে হোলি গ্রেইল।
পড়তে হবে তো বইটা।
হোলি গ্রেইল নিয়ে অনেক রকম কথা প্রচলিত আছে।
ঠিক আছে, থাক এখন।
বজ্জাত রল্ফটা জিজ্ঞেস করে–
আচ্ছা কেরোল, ডেয়ুডের সঙ্গে তোমার ইয়েটা গড়ে উঠলো কীভাবে?
এ রকম একটা প্রশ্ন কোনো ভদ্রলোকে করে?
কিছুটা উষ্মা প্রকাশ করি।
আমি হয়তো ভদ্রলোক না।
তোমরা দু’জনেই অতি-ভদ্রলোক, থামো এবার… এটার জবাব দিতে কোনো অসুবিধাই নেই আমার। শুরুটা ছিল নিতান্তই কৌতূহল।
একটু অবাক হই, জিজ্ঞেস করি–
কৌতূহল?
তাহলে আমার শৈশবের একটা কথা বলি?
বলো, বলো। উৎসাহ দেয় রল্ফ, খুব খুশিতে আজ সে। তৃতীয় পেগ নেয়ার আগে সাধারণত ভাবে কিছুক্ষণ, আজ দ্বিতীয়টা শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঢেলে নিয়েছে।
জিজ্ঞেস করি–
ঠিক আছো রল্ফ?
ভেবো না, তুমি ঠিক আছো তো?
আমি না থাকলেও তুমি আছো না, ঠিক রাখার জন্য।
কেরোলই যথেষ্ট।
ও কি বলতে যাচ্ছে শুনবে, না প্যাচাল চালাবে?
আমি প্যাচাল চালাই?
টেবিলের উপর টোকা দেয় কেরোল–
অর্ডার, অর্ডার।
হেসে উঠি দু’জনেই।
শোনো, সেবার হাইস্কুলে উঠেছি মাত্র, আমাদের প্রতিবেশী হিসেবে আসে এক মুসলিম পরিবার। বাবা-মায়ের কাছ থেকে তেমন কিছুই জানতে পারি না, ওদের ফিসফাস শুনি শুধু। বিকেলে যখন খেলতে বেরোই, অপেক্ষা করে থাকি লুকিয়ে ওদের দেখার জন্য, সামনে যেতে সাহস পাই না। শুনেছি ওরা নাকি ছুরি দিয়ে প্রাণী কেটে হত্যা করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করে ওগুলো নিজেরাই খেয়ে ফেলে। আমরা বলাবলি করি আমাদের জঙ্গলের খরগোশগুলো ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলিদান করে খেয়ে ফেলবে না তো ওরা, কিংবা আমাদের পোষা প্রাণীগুলো। আমাদের দোকানগুলোয় কেনাকাটা করতে যায় ওরাও, কখনও মাংস কিনে না, এতে আমাদের সন্দেহটা আরো বেড়ে যায়। মাঝে মাঝে আমাদের দেখে হাসে, কালো কালো চোখ দিয়ে সরাসরি তাকায়, আমরাও বোকার মতো হেসে ফেলি কখনো কখনো, আর পালিয়ে যাই। আমাদের এক বন্ধু দেখেছে ওদের ছেলেরা ঘরের ভেতর মেয়েদের মতো গাউন পড়ে থাকে। কেমন এক অদ্ভুত, গা-গুলানো গন্ধ নাকি ওদের ঘরের ভেতর! কুকুর বা বেড়াল পোষে না ওরা।
হাসতে থাকে রল্ফ।
এসব ধারণা কি এখনো আছে তোমার?
আরে না।
আমার দিকে তাকিয়ে বলে_
ডাউকে আমার অন্য রকম মনেই হয় নি।
কোন অর্থে?
এটাও থাক।
তাহলে গান হোক।
কে গাইবে?
টেগোর।
টেগোরের নিজের গাওয়া ‘তবু মনে রেখো…’ গানের রেকর্ডটা বাজাই।
এতো নিস্তব্ধ হয়ে যায় সবকিছু, কারো কথা বলতে ইচ্ছে হয় না, সুরের এই যাদুর রেশ ধরে রেখে প্রায় ঘুমিয়ে পড়ি আচ্ছন্নতার ভেতর। শেষ রাতের দিকে আড্ডা ভাঙলে ঘরে ফিরে যায় রল্ফ। ক্লান্ত হয়ে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ি। বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙ্গে। সকালটা মঙ্গলময় হয়ে ওঠে! গ্রাম সম্পর্কে এক চাচা এসেছেন বিলেতে সেনাবাহিনীর একটা ট্রেইনিং কৌর্সে, যাওয়ার আগে বেড়াতে আসেন আমার এখানে, কেরোল ও আমি মিলে বেশ যত্ন-আত্তি করি।
এর মাসখানেক পর চাচার চিঠি পেয়ে দুঃশ্চিন্তায় পড়ে যাই, বাবার অসুখ, সঙ্গে সঙ্গে টিকিট কাটি, বাড়িতে পৌঁছে দেখি বাবার শরীর ভালো, মন খারাপ। বুঝতে পারি, ঐ চাচা কিছু লাগিয়েছে নিশ্চয়। বাবার পরিষ্কার কথা: দেশে ফিরে আসতে না চাও, এসো না, কিন্তু বিয়ে করে বউ নিয়ে যাও, আর বিলেতেই যদি বিয়ে করতে চাও, তাহলে বিয়ে করে বউ নিয়ে আসো এখানে, সামাজিক একটা অনুষ্ঠান করে বিষয়টা মিটিয়ে ফেলি। ঐ চাচামিয়া বোধ হয় কেরোলের সঙ্গে বসবাসের কথা রং চড়িয়ে বলে বেড়াচ্ছে, বাবার আত্মসম্মানে আঘাত করেছে তা। খুবই স্বাভাবিক।
বাবাকে আস্বস্ত করে তাড়াতাড়ি ফিরে আসি, কেরোলকে বিয়ের কথা জানাই, কোনো আপত্তি নেই, ওর মায়ের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়। ভালোভাবে বুঝিয়ে বলি ওকে, ধর্ম বিষয়ে আমার অবস্থান সে তো জানেই, কিন্তু আনুষ্ঠানিকতা যেহেতু ধর্মগুরুদের দিয়েই করাতে হবে, নামমাত্র হলেও ওকে মুসলমানদের ধর্মটাকে গ্রহণ করতে হবে, বিয়েটা সেভাবেই হবে, ওতেও কোনো আপত্তি নেই ওদের কারো। গ্রীষ্মের ছুটিতে একটা তারিখ ঠিক করি। সবকিছু সুন্দরভাবে এগিয়ে যায়।
আকাশে উড়তে থাকা একটা পাখি যেমন অকস্মাৎ গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, আমার অবস্থা হয়েছে ঠিক তাই। খুব চেষ্টা করেও বিষণ্নতা ঢেকে রাখতে পারে না কেরোল, বলে_
তোমাকে একটা কথা ক’দিন থেকেই বলবো ভাবছিলাম ডাউ, শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, কিছু পরীক্ষা-টরীক্ষা করলো ডাক্তারেরা, আজ রিপোর্ট দিয়েছে, ক্যামো দিতে হবে কয়েকটা, কিছু ভেবো না তুমি, সব ঠিক হয়ে যাবে।
ওর হাত ধরে বসে পড়ি, অনেক অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারি না, এরকম হলো কেন!
প্রথম ক্যামো দেয়ার পরই চামড়া পুরো কালো হয়ে যায়, চুল ঝরে যায় সব। সারাক্ষণ হাসপাতালের কাছেই ঘোরাফেরা করি, ভেতরে তো ঢুকতে দেয় না, ওদের কেন্টিনে বসে থাকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বই পড়তে ইচ্ছে হয় না, টিভি দেখতে ইচ্ছে হয় না, এত প্রিয় আমার রবীন্দ্রসংগীত, তাও শোনা হয় না। অপ্রকৃতিস্থ, অসুস্থ একটা জীবনের ভেতর ছিটকে পড়ি, কলেজ থেকে ছুটি নিয়েছি। খারাপের দিকে যেতে থাকে কেরোলের অবস্থা, অপারেশন করে বুকের একটা দিক ফেলে দিতে হয়, কেরোলের কষ্ট আর সহ্য হয় না, ওকে বলি–
কিছুই চাই না তোমার, শুধু শরীরের ভেতর মানুষটা টিকে থাকো, ওতেই চলবে আমার, তাও যদি না পারো, অশরীরী হয়েও বেঁচে থাকো আমার বুকের ভেতর, তবু বেঁচে থাকো। বুঝতে পারি শরীরের থেকেও মনের কষ্টই হচ্ছে ওর বেশি।
শেষ পর্যন্ত সকল কষ্টেরই অবসান হয়। প্রায় আট মাস পর ওর মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয় ওর কফিন, শেষকৃত্যের আগেই বিলেতের পাট চুকিয়ে দেশে ফিরে আসি।
অক্সফোর্ডের শেষ ক’টা দিন এক অবর্ণনীয় অবস্থার ভেতর কাটিয়েছি, ভালোলাগা কোনো কিছুই আর ভালো লাগে নি, জীবনের প্রতি সব ধরনের আকর্ষণ ও মোহ হারিয়ে ফেলি, অর্থহীন মনে হয় সব কিছু। স্পেইস সাইন্স নিয়ে পড়াশোনা শুরু করি। বিশ্বজগতের সময়ের হিসেবে পৃথিবীর জন্ম ও মৃতু্যর সময়টাই তো একটা বুদবুদের জন্ম-মৃতু্যর সমান, আর একটা মানুষের জীবন মুহূর্ত দিয়েও পরিমাপ করা যায় না, এতো কিছু কেন এ জীবনে? পৃথিবীর এই অনিত্যতার ভেতর নিত্যদিনের কোনো কিছুই যেন আর নির্দিষ্ট থাকে না। কোনো কোনো রাতে ঘুম হয় না, আবার কখনো দেখি দুপুর থেকেই ঘুমোনো শুরু করেছি। কখন কি খাই তাও মনে থাকে না, ডিমেনশিয়া রোগীর মতো হয়ে পড়ি অনেকটা। পুরোপুরি এলোমেলো হয়ে যায় জীবন!
আমার এই ভগ্নাবস্থা দেখে মুষড়ে পড়ে বাবা, প্রায় দু’মাস গ্রামের বাড়িতে কাটিয়ে দেই, কোনো কিছুই ভালো লাগে না, জীবনের সকল অর্থ যেনো হারিয়ে ফেলি। বিলেতে ফিরে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই, দেশের ভেতরই ঘুরতে থাকি, পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করি, জীবনে কিছুটা গতি আনার চেষ্টা করি, যুদ্ধের ন’মাসে রাজাকারেরা কী অবস্থা করেছে দেশটার বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় নি, সর্বত্রই নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ, চেনা-জানা আত্মীয়-স্বজন অনেকেই নেই, অনেকের প্রায় পুরো পরিবারই শেষ করে ফেলেছে, কী নিষ্ঠুরতা! এর মধ্যে আবার নতুন করে শুরু হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা নামধারী ছদ্মশয়তানদের লুটতরাজ, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশের ভেঙ্গে পড়া অর্থনীতি, এমন একটা অরাজক অবস্থা দেশ-জুড়ে, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতির পক্ষেও এমন একটা দেশ স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ঠিক করে ফেলা পুরোপুরি অসম্ভব, অন্তর দিয়ে চেষ্টা করছেন বঙ্গবন্ধু, অসৎ রাজনীতিবিদরা প্রকৃত দেশপ্রেমীদের দূরে সরিয়ে দিচ্ছে বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে, মানুষের প্রত্যাশা ধূসর হতে শুরু করেছে, খুব দ্রুত নিজেদের অবস্থান ঠিক করে নিচ্ছে বিরুদ্ধবাদীরা, এতো দিন যারা স্রোতে গা ভাসিয়ে ছিল, সুযোগ বুঝে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে শুরু করেছে। এসব দেখেশুনে মন আরো ভেঙ্গে পড়ে।
শেষ পর্যন্ত গ্রামের পাট চুকিয়ে ঢাকায় চলে আসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির চেষ্টা করি, প্রোফেসর হিসেবে যারা আছে ওদের সঙ্গে কথা বলতে যেয়ে বুঝতে পারি আমার পিএইচডি ডিগ্রি এদেশে কাজে লাগানো যাবে না, পদার্থবিদ্যায় কোনো গবেষণা করা দূরে থাক, বিলেতে এ লেভেলেও এসব জিনিস পড়ানো হয় না, নতুন জ্ঞান দূরে থাক পুরোনো বিদ্যাই নেই এদের, বুঝতে পারি না, এসব বিশ্ববিদ্যালয় কেন! পদার্থবিদ্যায় মাস্টার্স করার পর যদি ব্যাংকের কেরানি বা পুলিস পরিদর্শকের চাকরিতে যেতে হয় তাহলে রাষ্ট্র কেন এই অপচয় করছে, এমন চাকরির জন্য এ লেভেল পড়াশোনারও দরকার নেই, ও লেভেলই যথেষ্ট। ওদের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারি তথাকথিত প্রাচ্যের অঙ্ফোর্ডে চাকরি হবে না আমার। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন প্রকৃত পদার্থবিজ্ঞানীর সন্ধান পাই, তরুণ ও খুব আন্তরিক ভদ্রলোক, ওর সঙ্গে দেখা করি, ওখানে ঢুকতে পারলে সে খুশি হবে, সব দিক দিয়ে সহায়তা দেন আমাকে, ওখানেও হয় না আমার, পৈতৃক বাড়ি চট্টগ্রামে হলে হতো নিশ্চয়, এরা এতো বেশি আঞ্চলিকতা দোষে দুষ্ট, জানা ছিল না।
আণবিক শক্তি কমিশন থেকে একটা অফার পাই, কিন্তু আমার স্বভাব যা দাঁড়িয়েছে, শিক্ষকতার বাইরে ঐ দশটা পাঁচটার জ্বীহুজুর চাকরি আমাকে দিয়ে সম্ভব হবে না। ঘুরে ফিরে একটা বছর কাটিয়ে দেই।
বাবা-মা উঠে পড়ে লেগেছে বিয়ে করানোর জন্য। বুঝতে পারি, এদেশটাকে হারিয়ে ফেলেছি আমার কাছ থেকে, এক বিগত আত্মা এখন আমি, কিছু করার নেই। জীবন থেকে প্রায় একটা বছর খুঁইয়ে লন্ডনের বিমানে উঠি, অনিশ্চয়তার পথে আবার ভাসিয়ে দেই জীবনের আগামী দিনগুলো।
৯
বিমান বন্দরে স্বাগত জানাতে এসেছে রল্ফ ও আবীর। এবারের বিলেতে আসায় প্রাণের কোনো উন্মাদনা নেই, উত্তেজনা তৈরি হয় না কোনো, সবই পুরোনো, চেনা বিশ্ব, বাতাসে কেবল অদেখা দীর্ঘশ্বাস, মনের ভেতর কোনো আনন্দ নেই, শিহরণ নেই, গতি হারিয়ে ফেলা নদীর মতো বয়ে চলা নিস্তরঙ্গ জীবন! রল্ফ বলে, ওর ফ্ল্যাটে একটা রুম একেবারে খালি পড়ে আছে, বইপত্র ও টুকিটাকি জঞ্জাল পরিষ্কার করে ওখানে থাকতে পারি ইচ্ছে হলে। আবীরদের যে-কোনো একটা রেস্টুরেন্টের একটা স্টাফ রুমেও থাকতে পারি আপাতত। কি করবো বুঝতে পারি না, রল্ফ বলে, আবীরের সঙ্গেই যাও, তোমার ইচ্ছে হলে যে-কোনো সময় আমার এখানে চলে আসতে পারো।
উইল্টশায়ার ও অক্সফোর্ড কাউন্টির সীমানায় চমৎকার একটা গ্রাম শ্রিভেনহ্যাম। আবীরদের একটা রেস্টুরেন্ট আছে ওখানে, উপরে অনেক ক’টা স্টাফ রুম, প্রায় সারা বছরই এক দু’টা খালি পড়ে থাকে, ওখানে নিয়ে আসে আবীর, রল্ফ পৌঁছে দেয় গাড়ি করে, রাতের খাবার ওখানেই সেরে নেই রল্ফ সহ। আমাকে রুমে গুছিয়ে রেখে ফিরে যায় আবীর, ঘুমিয়ে পড়ি চটজলদি, আজকাল খুব ভালো ঘুম হয়, কোনো কোনো দিন দশ বারো ঘণ্টা, অলসতার ভেতর কাটাতে ভালো লাগে। এতো বছর বিলেতে কাটিয়েও আমার বাঙালি হোটেলকর্মী ভাইদের সঙ্গে মেশা হয় নি, এখানে এসে ওদের জীবনযাত্রা দেখে মনে হয় বাংলাদেশেই আছি, রুমের ভেতর গুমোট গন্ধে ঢোকা যায় না, মেঝে জুড়ে ছড়ানো ছিটানো টুথপিক ও অন্যান্য টুকিটাকি, টেবিলে স্তূপ করে রাখা জঞ্জাল, প্রত্যেকের খাটের নিচে একটা করে স্যুটকেইস, প্রত্যেকের মাথার কাছে, দেয়ালে রশি টানিয়ে ঝোলানো কাপড়-চোপড়, ঘুমোতে আসে শেষরাতে, এগারোটা পর্যন্ত ঘুমোয়, মাঝরাতে হোটেলের কাজ শেষে আড্ডায় বসে, টিভি দেখে, তাস খেলে অনেকে, অনেকটা বন্দিশালায় কাটানো জীবনের মতো।
দু’হপ্তার মধ্যে আর একটা বিশাল ঘটনা সামান্য এ জীবনের অনেক হিসেব-নিকেশ পাল্টে দেয়, কর্মজীবন নির্দিষ্ট হয়ে যায় এটাতেই। অক্সফোর্ডের ক্রেইনফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক-শিক্ষক হিসেবে চাকরি পেয়ে যাই, সবাই খুব খুশি, একদিনও দেরি না করে ঢুকে পড়ি। সুইনডনে ছোট্ট একটা বাসা ভাড়া নিয়ে দেয় আবীর, শ্রিভেনহ্যামের অস্থায়ী আবাস ছেড়ে উঠে আসি নতুন বাসায়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রকল্পটা এতো ভালো লাগে আমার, মন-প্রাণ ঢেলে দেই, তিন বছর লাগে রেডিওলোজির সাহায্য নিয়ে একটা যন্ত্র তৈরি করতে যা বিশুদ্ধ পানির প্রবাহ নিশ্চিত করবে, পানির পাইপ-লাইনের দুটো প্রান্তের মাঝামাঝি বসানো যন্ত্রটায় থাকবে একটা ডিটেক্টর, পানিতে অগ্রহণযোগ্য কোনো উপাদান যন্ত্রটার আওতায় আসা মাত্র বিশুদ্ধ পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে অন্য একটা ভালব খুলে যাবে, যেখান দিয়ে পানি অন্য আধারে চলে যাবে আবার বিশুদ্ধ করার জন্য। বিশুদ্ধ পানি আসা আবার শুরু হলে এটা বন্ধ হয়ে আগেরটা চালু হয়ে যাবে, এভাবে একশোভাগ বিশুদ্ধ পানির প্রবাহ নিশ্চিত থাকবে। গৃহস্থালি বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়ও এটা কাজে লাগবে, ওখান থেকে পচনশীল, অপচনশীল, ধাতু, কাপড়, কাগজ প্রভৃতি বস্তু পৃথক করে ফেলতে পারবে যন্ত্রটা। এটা একটা বড় ধরনের কাজ আমার, স্বীকৃতিও এনে দিয়েছে আমাকে। জীবনের তিক্ত দিকগুলো থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখি কাজে ডুবে থেকে।
রল্ফের কাছ থেকে আর একটা জ্ঞান অর্জন করেছি, অসংখ্য ছোট দৈর্ঘের প্রেম করে সে, কোনো কোনোটা এমনকি এক হপ্তার! জীবনের চাহিদা তো মেটাতেই হয়, আমিও অভ্যস্ত হয়ে পড়ি ছোট দৈর্ঘের প্রেমে। জীবনের কেরোলপূর্ব অবস্থায় ফিরে যাই অনেকটা। চাকরি থেকে যা উপার্জন করি, আমার জন্য অঢেল, দেশে যাই প্রতি বছর, বাবাকে সুখী রাখতে চেষ্টা করি। প্রেমিকাদের নিয়ে হলিডেতে যাই বিভিন্ন দেশে। সুইনডনের ছোট্ট বাসাটা ছেড়ে দিয়ে হাইওয়ার্থে একটা ডিটাচড বাড়ি কিনেছি। বিশাল, সামনে অনেক বড় বাগান, পেছনে প্রায় ফুটবল খেলার মাঠ, একটা পাহাড়ের চূড়ার সব-শেষ বাড়ি, অনেকটা দূরে অন্য পাহাড়, ফসল আবাদ হয় সেখানে। এতো বড়ো বাড়ি, ফাঁকা লাগে কখনো কখনো, ইউরোপের ইনডিভিজুয়ালিস্টিক জীবনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছি, খুব একটা অসুবিধা হয় না। প্রেমিকাদের কখনো বাসায় আনি না, উইকেন্ডে কাছাকাছি কোথাও ট্যুরে যাই, হলিডেগুলোয় একটু দূরে। একটা হিন্দি সিনেমা দেখেছিলাম, ওখানে একটা ডায়লোগ ছিল, ‘মেরে ঘর, মেরে মন্দির’, একটা চলচ্চিত্রও ছিল এ নামে। আমারও নিজের আবাসটাকে কালিমাহীন রাখতে চেষ্টা করি, আত্মার মতো।
আবীর মাঝে মাঝে আসে উইকেন্ডে, আড্ডার জীবন কিছুটা আবার ফিরে পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে মোটামুটি চলে। আবীরের জীবনটাও এলোমেলো হয়ে যেতে শুরু করেছে, ওর বাবা-মা এতো বেশি মেয়ে দেখেছে ওর জন্য, অথচ সত্যি ম্যাচিং হয় এমনটাই দেখছে না বা খুঁজে পাচ্ছে না, আমারই পছন্দ হয় না, কি দোষ দেবো আবীরকে। ওর বাবা একদিন ডেকে বলে, ওকে নিয়ে দেশ থেকে বেরিয়ে আসো ক’দিনের জন্য, যে মেয়েই পছন্দ করুক, বিয়ে ঠিক করে দেবো আমি। ভাবি, প্রস্তাবটা মন্দ না। ওদের গ্রামের বাড়ি যাই, বিশ্বনাথের দেওকলস গ্রামে। সিলেটের মুরারী চাঁদ কলেজে নতুন চাকরিতে ঢুকেছে, এমন এক মেয়ের সন্ধান পেয়ে ছুটে যাই, কথা-টথা বলে আমারই পছন্দ হয়ে যায়। বলি–
আমারই তো ইচ্ছে হচ্ছে।
লাফিয়ে ওঠে সে।
তাই সই, তোর জন্যই কথা বলি।
দূর যাহ্, ঠাট্টা করলাম, আর সিরিয়াসলি নিয়ে নিলি, দিলি লাফ।
সত্যি বলছিস?
হ্যাঁ, সত্যি আবীর, তোর বাবাকে বল।
তুই বল।
পরের হপ্তায় ওর বাবা এসে হাজির, দু’হপ্তার মধ্যে ধূমধাম করে বিয়ে হয়ে যায় ওদের। মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্য ওদের কক্সবাজার পাঠিয়ে ওর বাবার সঙ্গে আমিও ফিরে আসি ইংল্যান্ডে।
ওর স্ত্রীর ইংল্যান্ডে আসার জন্য কাগজপত্র তৈরি প্রভৃতি সারতে আরো তিন মাস থেকে যায় আবীর, তারপরও ওকে আনাতে প্রায় এক বছর অপেক্ষা করতে হয়। ছেলেকে বিয়ে করিয়ে আবীরের বাবার খুশি দেখে অভিভূত হই, বুকের ভেতর বাবার জন্য কাঁটার খোঁচা অনুভব করি, তাঁকে খুশি করতে পারলাম না, স্বার্থপরের মতো নিজের জীবনটাই যাপন করে চলেছি, মুখে কিছু না বললেও বুঝতে পারি ভেতরে ভেতরে খুব কষ্ট পাচ্ছেন। কিছুদিনের জন্য হলেও বিলেতে নিয়ে আসার অনেক চেষ্টা করেছি, কোনোভাবেই রাজি করাতে পারি নি, মা তো মরে গেলেও বিমানে চড়বে না। আগামী বছর যেয়ে চেষ্টা করবো হজ্জ্ব করতে রাজি করিয়ে জোর করে হলেও ইংল্যান্ডে নিয়ে আসবো।
চাকরিটা করে বেশ আনন্দ পাচ্ছি, ক্রিয়েটিভ অনেক কিছু থাকার কারণে সম্ভবত। একটা প্রমোশনও পেয়েছি, বেশ ক’জন চমৎকার সহকর্মীও পেয়েছি।
বিলেতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেখে এটা বুঝতে পেরেছি, নব্যধনীদের অথবা উপরে উঠতে মরিয়া বিত্তবানদের বাজে কাজে অবসর কাটানোর জন্য এগুলো গড়ে ওঠে নি। জনগণের সম্পদ এসব, এখানে যারা শিক্ষা নেবে বা দেবে, তারা নৈতিক জীবন যাপন করবে। কারিগর, চিকিৎসক, গবেষক, ব্যবসায়ী, সাহিত্যিক হবে, জনগণের অবদানের বিনিময়ে যারা উন্নত সেবা দেবে ঐ জনগণকে, নিজেদের ভবিষ্যতও সুন্দর করে গড়ে নেবে। গলায় টাই ঝোলানো ভৃত্যকুলের জন্য রাষ্ট্রীয় সম্পদ অপচয় করে না এরা, ভৃত্যদের যোগ্যতা আদেশ পাঠ ও পরিপালনের বেশি কখনোই নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী কেউ আমলা-জাতীয় সরকারী ভৃত্যের কোনো পদের জন্য আবেদন জানালে ওভার-কোয়ালিফাইড বলে বাতিল করে দেয়, প্রকৃত মেধাবীরাই কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে। নতুন যে বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠছে, বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ, মানববিদ্যার অগ্রগতি, প্রভৃতির সবই পাশ্চাত্যের এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান।
এক তরুণ গবেষক সমপ্রতি যোগ দিয়েছে আমাদের বিভাগে, সহকারী হিসেবে ওকে পেয়ে বেশ ভালোই লাগছে। জার্মান-স্কটিশ, নীল ম্যাককিন, লম্বা ঢ্যাঙা, লালচে চুল, ভাইকিংদের উত্তরপুরুষ সম্ভবত। বিকেল হলেই বেরিয়ে যাবে বাস্কেট বল নিয়ে, রোম্যান্টিক চেহারা, অথচ অস্বাভাবিক রকম লাজুক আচরণ করে ওর সহকর্মী ও সহপাঠিনীদের সঙ্গে। সময়টা এখন অবাধ মেলামেশার স্বর্ণযুগ, প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকের সঙ্গে একটু হলেও মিশতে চায়, এমন সুসময়ে নিজেকে বঞ্চিত করার কোনো অর্থ হয় না।
বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে ওর একান্ত জগত, আমাদের বিভাগীয় প্রধান ড. চেস্টারম্যান ওর আদর্শ, আরবদের সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে কিছু সেকেন্ডহ্যান্ড তথ্য দিয়ে ওকে অভিভূত করে ফেলেছিল চেস্টারম্যান। ওর ধারণা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের সংযোগ ঘটিয়ে মধ্যযুগে আরবরা রসায়ন ও জীববিদ্যায়, গণিত ও পদার্থবিদ্যায় অনেক জ্ঞানী হয়ে ওঠেছিল, গবেষণা করে এখন যা কিছু আবিষ্কার করছি আমরা, ওদের যদি থামিয়ে দেয়া না হতো, তখনই এসব করে ফেলতে পারতো ওরা, আরবদের নতুন ধর্মটা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানচর্চার জন্য উদার, অথচ ওদের শাসককুল ছিল প্রকৃত অর্থেই বদমাশ, জ্ঞানের ও দর্শনের চর্চায় ওরা বাধ সাধে যেনো সাধারণ মানুষ প্রকৃত শিক্ষিত হয়ে উঠে ভ্রান্ত ও দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিবিদদের বিপক্ষে চলে যেতে না পারে, জীবনরক্ষার্থে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের পালিয়ে বেড়াতে হয় এমনকি, ধর্মকে ওরা ব্যবহার করে নিরক্ষর জনগণকে দারিদ্র ও অশিক্ষার ভেতর আটকে রেখে নিজেদের ভোগ বিলাসিতা বজায় রাখার কাজে, ওটায় এতোটাই সফল হয় ওরা যে এখনো তা চালিয়ে যেতে পারছে চরম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে, অথচ ওদের ধর্মটা ছিল সে-সময়ের জন্য উদারতম। অন্য ধর্মাবলম্বীরা সময়ের সঙ্গে নিজেদের শিথিল করেছে, যুগোপযোগী করে নিয়েছে, অথচ ওরা এখনো ঐ কট্টরই রয়ে গেছে। গবেষণা করতে কখনো দেখা যায় না চেস্টারম্যানকে, অবসর সময়ে এ ধরনের ছোট ছোট ভাষণ দিয়ে, ও কুকুর পুষে আনন্দ পায়। সবার কাছে প্রিয় হওয়ার মতো কি যেন একটা ছিল ওর ভেতর, ছোট্ট একটা ঘরোয়া পার্টিতে আমন্ত্রণ করে সে আমাদের ক’জনকে।
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিভাগে অন্তত একজন পাগলাটে গবেষক রয়েছেন, এরা বিভাগীয় সম্পদ, ছাত্রদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করায় ওস্তাদ এরা, ছাত্রদের দু’চারজনকে বিপর্যস্ত করে এক ধরনের আনন্দ পায় ওরা, যাদের কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যায় এমনকি। আমাদের বিভাগেও যথারীতি এমন একজন রয়েছে, বিভাগীয় প্রধান নিজেই। সুনীতি বলে কোনো কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন তিনি, এগুলোকে বলেন আপাত-অনুকূল স্বার্থান্বেষী নীতি, ভবিষ্যতে যা বাতিল হবে, সত্য হচ্ছে ক্রম-প্রসারমান, ধ্রুব সত্য বলে কিছু নেই, গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র, কোনোটাতেই আস্থা নেই, ঈশ্বর অথবা শয়তান, কারো অস্তিত্বেই বিশ্বাস বা অবিশ্বাস নেই। সবকিছুকে একই রঙের ভিন্নরূপে দেখেন, শাসক ও শাসিতের সুবিধে অনুসারে একটা মধ্যাবস্থা। আস্তিক ও নাস্তিকের মধ্যে খুব সামান্যই পার্থক্য রয়েছে বলে মনে করেন, যদিও ইহুদি বলে জানে ওকে সবাই, ওর আচরণে প্রেসবাইটেরিয়ানদের সঙ্গে মিল বেশি। কেন যে নীল ওর এতোটা আস্থা অর্জন করেছে মাঝে মাঝে ভেবে পাই না।
আজকের সন্ধ্যায় ওর মেজাজ বেশ প্রসন্ন, প্রতিভাবান কাউকে সে মনে করে হয় ইহুদি, নয় তো আরব, এই অদ্ভুত ধারণার পেছনে শত শত যুক্তি দাঁড় করাতে পারে সে, একারণে কেউই নিজেকে প্রতিভাবান প্রমাণ করতে চায় না ওর সামনে, ফলে সব সময় আসর থাকে ওর দখলে, স্বল্প-দৈর্ঘের বিভিন্ন রশ্মি নিয়ে গবেষণা করতো জার্মানিতে, ওখান থেকে পালিয়ে আসার পর ফিরে যায় নি আর, বস্তুত যাওয়ার মতো কেউ ছিল না। গবেষণাগারে যাওয়া, নিজের ও কুকুরের জন্য খাবার-দাবার কেনার জন্য হপ্তায় একবার সপিং সেন্টারে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো কারণে ঘরের বাইরে বেরোতো না সাধারণত। বিভিন্ন উদ্ভট আচরণের জন্য ছাত্রদের ভেতর অনেক গুজব ছিল ওকে নিয়ে, কেউ কেউ ওকে সমকামী বলতেও ছাড়তো না। আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘের চেয়েও ছোটো তরঙ্গ নাকি প্রায় আবিষ্কারই করে ফেলেছে সে! প্রচলিত নিয়ম অনুসারে ছাত্রদের সঙ্গে সহকর্মীদের বিষয়ে আলোচনা করে না শিক্ষকেরা, নীলের সঙ্গে তাই ওর বিষয়ে কোনো কথা বলি না। এটা বুঝতে পারি, কোনো প্রসঙ্গে নীলের সঙ্গে এভাবে কথা পেঁচিয়ে তোলে সে, যেনো আমার প্রসঙ্গ এসে যায়, এভাবে আমার বিষয়ে টুকটাক জানতে চায় চেস্টারম্যান, কথার পিঠে কথা নিয়ে আসার আশ্চর্য ক্ষমতা ওর, কোনো কারণ পাই না ওর ঔৎসুক্যের, হয়তো ভেবেছে যেহেতু মুসলমান আমি, আরবদের মিশ্রণ ঘটে থাকতে পারে আমার ভেতর, তায় আবার নামের নাকে একটা শেখ, বসিয়া আছেন! ওর অনুমানটা খুব মিথ্যেও না, উন্নত জীবনের লোভে ইয়েমেনের একদল সুযোগসন্ধানী এসেছিল আমাদের অঞ্চলে, যারা ফিরে যায় নি আর কখনো।
আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে চেস্টারম্যানের বন্ধু, বিখ্যাত এক কবি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, নিয়মিত কবিতা পাঠের জন্যই হয়তো ওর গলার স্বর সব সময় উঁচুতে থাকে, চেস্টারম্যানকে খুঁচিয়ে উত্তেজিত করে তোলা ও আসর ভণ্ডুল করে দেয়ার কৃতিত্ব নেয়ার জন্য ওর জুড়ি দ্বিতীয় কেউ নেই, সবার ইচ্ছে সব শেষে কথা বলুক সে, যখন সবাই সত্যিই ঘরে ফিরে যেতে চায়। অথচ কি এক প্রসঙ্গ এসে যায় হঠাৎ, চেঁচিয়ে বলে_
আমরা যারা স্বপ্ন ও সৌন্দর্য ভালোবাসি, এটা বিশ্বাস করি ও নির্মাণ করি, তাদের অবহেলা করার যৌক্তিক কোনো কারণ নেই তোমার, চেস্টার, বিজ্ঞানের সব আবিষ্কার ও অগ্রগতি হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করি আমরা, বিশুদ্ধ সংখ্যা বা গণিত দিয়ে যা প্রমাণিত নয় তার যদি কোনো মূল্যই না থাকে, তাহলে তোমার স্ত্রীকে বলোনা, ঠোঁটে লিপস্টিক না লাগাতে, কেশ-সজ্জা না করতে, প্রসাধন ব্যবহার না করতে . . .
ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে চেস্টার–
চুলোয় যাক, সৌন্দর্যের কোনো মূল্য নেই এমন ধারণা কস্মিনকালেও আমার ছিল না, নেই, এবং থাকবেও না।
বিষয়টা যেন এগিয়ে যেতে না পারে, এবং এটা থেকে পরিত্রাণ পেতে দারুণ এক কাজ করে আমাদের তরুণ অতিথি, উঠে যেয়ে চেস্টারের স্ত্রীকে জানায়_
আপনার স্বামীর যদি আপত্তি না থাকে তাহলে চলুন এক পাক নাচি।
নিশ্চয়, বলেই মিউজিকের ভলিউমটা বাড়িয়ে দিয়ে সত্যিই নাচতে শুরু করে ওরা। বাজনাটা ছিল মধ্যলয়ের, একে একে সবাই জোড় বেঁধে নাচতে শুরু করে, জোড় না থাকায় বসে বসে দেখি। পরিবেশটা আবার আনন্দঘন হয়ে ওঠে। একটা চমৎকার সন্ধ্যা উপভোগ করে সবাই, মিসেস চেস্টারম্যান ঘরে-বানানো তিন স্তরের চকোলেট কেইক পরিবেশন করে পার্টির শেষে এসে।
বাইরে যথেষ্ট ঠাণ্ডা হলেও হেঁটে ঘরে ফেরার ইচ্ছে হয়, সঙ্গী জুটে যায় নীল, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার অনেকগুলো ছোট বড় ভবন ও বাগানের পাশ দিয়ে হেঁটে যাই, শরীরের ভেতর থেকে শীতের অনুভূতি চলে যায় একটু পরে, একটা ভবনের কাছাকাছি যেতে বাইরের বাতিটা নিভে যায়, একটু আশ্চর্য হই, বাল্ব ফিউজ হয়েছে না রাতজাগা কোনো প্রাণী নিজেকে আড়াল করার জন্য বাতিটা নিভিয়ে দিয়েছে! কয়েক মিনিট পর বিদায় জানিয়ে ওর বাসার দিকে ঘুরে যায় নীল, বেশ বড় একটা মাঠের পাশ দিয়ে পেরোতে হবে রাস্তাটা। নিশ্চুপ শীতের রাতের মলিন আলোয় দীর্ঘ শরীর, জগত-সংসার বিষয়ে নির্লিপ্ত, আত্মসমর্পিত, অদ্ভুত আচরণ এক মানুষের আবির্ভাব ঘটে। আর্যদের উঁচু নাক ও গোল কপালের দুপাশে উজ্জ্বল দুটো চোখ মেঘমুক্ত আকাশের স্নিগ্ধ তারার মতো, পৃথিবী ও পরিপার্শ্ব সম্পর্কে অচেতন, আত্মমগ্ন, হয়তো নিজেও জানে না কোথায় হেঁটে যাচ্ছে অথবা কেন, হাত দুটো ওভারকোটের পকেটে ঢোকানো, কাছাকাছি আসতেই একটা হাত বাড়িয়ে দেয় একটুও অপ্রতিভ না হয়ে, যেনো এখানেই থাকার কথা আমার, পূর্ব-নির্দিষ্ট!
কেমন আছো ডাউ?
ড. রল্ফ!
চিনতে পারছো না?
কষ্ট হচ্ছে।
হবারই কথা। সেই বিকেল থেকে ফোন করে চলেছি তোমাকে, রিং বাজছে, ধরছো না কেন?
বাইরে থেকে ঘরের ভেতর ফোন ধরার কৌশলটা এখনো শেখা হয় নি তোমার কাছ থেকে, আশা করি শীঘ্রই শিখে নেবো এটা…। তোমার মতো অলৌকিক ক্ষমতা এখনো অর্জন করতে পারি নি রল্ফ, দুঃখিত এজন্য।
ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোমার এখানে আজ রাতটা কাটানো যায় ডাউ?
আমি খুব ক্লান্ত রল্ফ, এখন যেয়েই ঘুমিয়ে পড়বো, সুবিধে হবে না তোমার।
তোমার লিভিং রুমের সোফায় ঘুমোতে পারবো আমি।
ব্রিটিশেরা তোমার মাপে সোফা বানায় না তো, পা নয়তো মাথা, কোনো একটা ঝুলিয়ে রাখতে হবে তোমাকে।
দেখা যাবে ওটা, চলো এগোই তাহলে।
অগত্যা বলি–
চলো।
দুঃখিত ডাউ, তোমার অনুমতি না নিয়ে এসে পড়ার জন্য।
এতো ভদ্রতা দেখাতে হবে না, অনেকদিন আগে থেকেই অভ্যস্ত হয়ে গেছো এতে।
একটু চুপ করে থাকে রল্ফ, ছোট্ট একটা চাপড় দেই পিঠে।
কিছু মনে করো না।
না না ডাউ। একটু থেমে বলে, হয়তো জানো, ইংল্যান্ডে একমাত্র তোমার সঙ্গেই এমনটা করি আমি।
জানি জানি।
আর অধিকার তুমিই দিয়েছো।
রাখো তো ওসব রল্ফ।
একটা উৎকট ঝামেলা মনে হচ্ছে, সত্যিই যেয়ে ঘুমানোর ইচ্ছে এখন, ঘরে ঢুকে উপর থেকে বিছানাপত্র এনে দেই ওকে। বলি, শুয়ে পড়ো।
ফ্রেশ হয়ে উপরে উঠে শুয়ে পড়ি। ঘুমোবো, দীর্ঘ ও নির্বিঘ্ন একটা ঘুম চাই এখন, বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে না, আমার ঘুমের প্রাকৃতিক অষুধ, পাশ্চাত্যের উচ্চাঙ্গ সংগীতের ছয়টা রেকর্ড চেঞ্জারে চাপিয়ে দেই, খুব লো ভলিউমে, ঐ সব সংগীতের অনেকগুলোরই বৈশিষ্ট্য এমন যে মাঝে মাঝে জোরে বেজে উঠে ধীরে ধীরে এতো ক্ষীণ হয়ে যায় যে মনে হয় অনেক অনেক দূরে কোথাও বাজছে, ঘুমোনোর জন্য এর চেয়ে ভালো আর কিছু এখনো আবিষ্কার করতে পারি নি। এতেও কাজ হয় না এখন! রল্ফের মতো এমন একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, যাকে ভগবান গড়েছেন নিজ হাতে অনেক যত্ন করে, তাকে নিচে রেখে ঘুমোনো অসম্ভব! ধুত্তোর, বলে নিচে নেমে অবাক হই, চুপচাপ সোফায় বসে আছে, বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা ভাবছি, ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছি। বলে–
ঘুমাই নি।
তাই বলো। আলো জ্বালবো?
জ্বালো।
একটু দুঃখবোধ হয় ওর জন্য, আরেকটু ভালো হওয়া উচিত ছিল আমার, বেচারা!
ঘরে পরার পোশাক দেই রল্ফ, একটু স্বচ্ছন্দ হও?
দিতে পারো।
কাপড় পাল্টে হাতমুখ ধুয়ে আসো, কিছু একটা তৈরি করি তোমার জন্য, কি খাবে বলো?
যে-কোনো কিছু, যা খুশি তোমার।
জেইমির চিকেন সালাদ দিয়ে একটা স্যান্ডউইচ বানিয়ে দেই, একটা হ্যাডক ফিলে ও কয়েকটা পটেটো ওয়েজেসও ভেজে দেই।
খাবার দেখে খুশি হয়ে ওঠে।
বাহ্!
ওর খাওয়া দেখে বুঝি ক্ষুধার্ত ছিল, আমি ঘুমিয়ে পড়লে নিশ্চয় অন্যায় হতো, ভাগ্যিস ঘুমাই নি! একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি_
ভাবলে কি করে যে ঘরে পাবে আমাকে, এতোটা পথ পেরিয়ে এসেছো।
আগেও বলেছি তোমাকে ডাউ, মনের টানে চলি সব সময়, সাধারণত মনের বিপক্ষে যাই না আমি, মন যা বলে তাই করি। একশ’ভাগ ক্ষেত্রেই যে মনের ইচ্ছেটা ঠিক হয়ে যায়, তা না, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনের ইচ্ছেটাই জয়ী হয়, দু’একবার বিপরীত হলেও মনে কিছু করি না, ওটাই প্রকৃতির নিয়ম। শত ভাগ সঠিক বা অভ্রান্ত বলে কিছু নেই পৃথিবীর কোথাও। মন তো মানুষেরই, আর মানুষ প্রকৃতিরই অংশ, এটা মেনে নিতে কষ্ট হয় না আমার, মন বলেছে, ঘরে পাবো তোমাকে আজ, একটু দেরিতে হলেও পেয়েছি। মন বলেছে, ঐ পথ ধরে ফিরে আসবে তুমি, তাই এসেছো, মন বলেছে, তুমি এখন ঘুমাবে না, ঘুমোও নি . . .
রল্ফ, তোমার ভেতর তো দেখি প্রোফেসি রয়েছে! বলো দেখি আরো কি কি বলে তোমার মন, আমার কাজে লাগবে।
ওর সেই নিঃশব্দ হাসিতে ভরিয়ে দেয় আমার মনের সবটুকু। জিজ্ঞেস করি_
আমার মন যে কিছু বলে না রল্ফ?
কোথাও একটা কাঁটার খোঁচা খাই। দু’কাপ স্ট্রং কফি বানিয়ে নিয়ে আসি, ওরেওর মিক্সড বিস্কুটের একটা টিন খুলি, এই বিস্কুটগুলো কেন যে এতো ভালো লাগে আমার, থামতে পারি না!
সবার মনই কিছু না কিছু বলতে চায় ডাউ।
যাদের মনের বলা কথায় অধিকাংশ বাস্তবের সঙ্গে মিলে যায় তাদের অতিলৌকিক কোনো ক্ষমতা আছে বলে ধরে নেয়া হয়।
এখানেই ভ্রান্ত হই আমরা, অথবা ভ্রান্তির ভেতর পড়ে যাই নিজেরা। তুমি তো আবার নীৎসে প্রসঙ্গ তুলতে দেবে না, এই ভ্রান্তি সম্পর্কে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছিলেন তিনি।
না, নীৎসের প্রতি কোনো বিদ্বেষ নেই আমার, তবে শেষ পর্যন্ত আঙ্গুলটা এসে তার চোখেই গুঁতো দেয়।
অস্বীকার করছি না, শেষ পর্যন্ত ভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে বেরোতে পারেন নি তিনিও। কথা হচ্ছিল মনের কথা নিয়ে, যখন বিজ্ঞান, আরো সংকীর্ণ হয়ে বললে, মনোবিদ্যা, যেটাকে বিজ্ঞানের একটা অংশ বলে মনে করি, এতোটা অগ্রগতি অর্জন করে নি, দেড়-দুই-আড়াই হাজার বছর আগে, যে সব মহান ব্যক্তিদের মনের কথাগুলো অধিকাংশ বাস্তব বা প্রায়-বাস্তব রূপ লাভ করে, সাধারণভাবে চিন্তা করতে অক্ষম আমজনতা ওদের ঐ ক্ষমতাকে অলৌকিক ভেবে নেয়, ওদের মনের যে-সব কথা ঠিক হতো না, বা ফলে যেতো না সেগুলো দক্ষভাবে চেপে যেতো ওদের গুণগ্রাহীরা, তাবেদাররা, বা উপকারভোগীরা। ঐ সব মানুষদের শিখণ্ডী বানিয়ে ওদের উপর প্রোফেসি আরোপ করে নিজেদের মনের অনেক কথাও ওদের বলে চালিয়ে দিতো, প্রায় প্রতি প্রজন্মে বিভিন্ন গোত্রে এরকম এক-আধজন অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব হতো, ওদের অনেকে সাধু, অথবা ভণ্ড, অথবা এ দুটোর মিশেল।
এভাবে বলো না।
শুধু তোমার সঙ্গেই বলছি এসব।
কাউকেই এতো বেশি বিশ্বাস করো না।
তা হলে তো নিজেকেই অবিশ্বাস করতে হয়।
ওদের উদ্দেশ্য কিন্তু অসৎ ছিল না।
তা বলি নি, কিন্তু একটা ভ্রান্তির বেড়াজাল তৈরি করেছিল ওসব, মানুষের স্বাধীন চিন্তাশক্তির জন্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
এতো অসংখ্য ছিল ওরা, কেউ কেউ বিভ্রান্তি ছড়াতেও পারে।
হ্যাঁ, হিন্দু শাস্ত্রে বলে তেত্রিশ কোটি দেবতা, তোমাদের শাস্ত্রে বোধ হয় কয়েক লক্ষ পয়গম্বর।
শাস্ত্র বিশারদও হয়ে ওঠেছো দেখছি, কি নও তুমি!
দেখো, ধর্ম ও রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে সব চেয়ে বেশি অনাগ্রহ আমার, অথচ কথা বলতে গেলেই ওদুটো এসে পড়ে।
তার মানে ওদুটো বাদ দিয়ে জীবন হতে পারে না, এজন্যই তো বলি শিল্প সাহিত্য নিয়ে কথা বলো।
ওখানে ওদুটো নেই?
বেকায়দায় ফেললে রল্ফ।
থাক, তাহলে কি আমার বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো?
খবরদার, মুখ খুলেছো তো টুটি চেপে ধরবো।
এতো কষ্ট করে এলাম!
না, এজন্য আসো নি তুমি। আমার মনও মাঝে মাঝে কথা বলে, সেগুলো ঠিক ঠিক হয়ে যায়।
হেসে বলে, বিশ্বাস করো।
অনেক বার করেছি।
কেন যেনো মনে হচ্ছে ডাউ, তোমার কাছে এসব বলার জন্য খুব বেশি সময় আমার হাতে নেই।
তোমার মন বলছে একথাটা?
হ্যাঁ।
সত্যি?
হ্যাঁ, সত্যি।
কিছুটা বিষণ্ন মনে হয় ওকে, এই প্রথম ওর চোখে অন্য এক আলো দেখি, নিষ্প্রভ, শীতের কুয়াশামাখা ধূসর! বলি_
ঠিক আছে রল্ফ, সব সময় যেখানে এসে থেমে যাও, তার পর থেকে যদি বলতে চাও, বা পারো, সেখান থেকে শুরু করতে পারো, আগের কথাগুলো অন্যভাবে বলে বোকা বানানোর চেষ্টা করো না আমাকে।
ঠিক আছে, সোফায় হেলান দিতে পারি একটু, ক্লান্ত বোধ করছি।
নিশ্চয়, শুয়ে পড়তে পারো, বালিশটা নাও, শুয়ে শুয়ে বলো।
তাই ভালো, কিছু একটা পান করতে পারি, ওয়াইন জাতীয়।
সেলার থেকে নিয়ে নাও যা খুশি, টয়লেট থেকে আসছি আমি।
হিটার অন থাকায় বেশ গরম হয়ে উঠেছে ঘর, টয়লেট থেকে ঘুরে এসে দেখি মৃদু নাক ডাকছে রল্ফ! অবাক হই, এমন হুট করে ঘুমিয়ে পড়ার কথা তো না, কিছুক্ষণ বসে থাকি, আরো ভারি হতে থাকে ওর শ্বাস-প্রশ্বাস, উপরে উঠে যেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি, যা চাইছিলাম ক’ঘণ্টা ধরে।
ঘুম থেকে উঠে দেখি অন্য আকাশ, অন্য আলো, এতো ঝকঝকে, ঘরের ভেতর থেকে গ্রীষ্ম বলে ভুল হয়, রল্ফকে বলি, আজ আমার যাত্রা নাস্তি, ঘরের বাইরে পা রাখা যাবে না, গান শুনবো শুধু, আর খাবো-দাবো, ফুর্তি করবো।
নাচবে না?
সঙ্গী নেই।
দুঃখের বিষয়! তা আমার যে আবার যাত্রা শুভ।
মাঝামাঝি কিছু একটা হবে, ময়ূরী পছন্দ করো তুমি?
স্যাঙ্কচুয়ারিতে দেখেছি, খুব সুন্দর, তোমাদের একটা কবিতা পাঠের আমন্ত্রণে যেতে হয়েছিল, জীবনে ঐ একবারই, একটা শব্দ বুঝতে না পেরে ওটার মানে জানতে চেয়েছিলাম, মনময়ূরী, কোনোভাবে মিলাতে পারি নি মনের সঙ্গে ময়ূরীর সম্পর্ক, ওর অনুবাদটাও সম্ভবত ভালো ছিল না।
এটা কোনো বিষয় না, ভাষার এ রহস্যটা সব ভাষায়ই আছে, আমার কাছে ঐ শব্দটা ভীষণ দ্যোতনা সৃষ্টি করে, বর্ষার সঙ্গে মনের সম্পর্ক, ঐ ঋতুতে ময়ূরী কেন পেখম মেলে, প্রকৃতির এসব অনুষঙ্গ তোমাদের নেই, এটা না বোঝাই স্বাভাবিক তোমাদের, পাশের গ্রামে একটা ময়ূরীর খামার আছে, বিকেলে যেতে পারো।
এক সঙ্গে অনেকগুলো ময়ূর দেখে অভিভূত রল্ফ, বেশ বড় লেজের পূর্ণ-বয়স্ক একটা ময়ূরী দেখে বিস্ময়-চোখে, ওটার ছবি দেখাই। এরকম পেখম মেলে ওরা বর্ষা এলে, ওদের প্রজননকাল, মৌসুমী বর্ষায় বাংলাদেশের মানুষের মনও নেচে ওঠে, ওরা যখন পেখম মেলে, এমনভাবে কাঁপে ওটা, মনে হয় ময়ূরীটা নাচছে যেনো, চমৎকার ছন্দ আছে ওখানে, ভারতীয় নাচের মুদ্রায়ও এটা ব্যবহার করা হয়, রোম্যান্টিকতায় তোমার মনও নেচে ওঠে ওভাবে।
একটু একটু বুঝতে শুরু করেছি।
হালকা ফুরফুরে মন নিয়ে পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, এক সঙ্গে বেশ ক’টা ভালো সংবাদ, আমার একটা আর্টিক্যাল জার্মানিতে অনুবাদ করার জন্য অনুমতি চেয়ে পত্র পেয়েছি, আমেরিকার একটা বিখ্যাত জার্নালে বড় একটা আর্টিক্যাল বেরিয়েছে, নতুন একটা গবেষণার জন্য বড় একটা ফান্ড ও আরো এক জন সহকারী পেয়েছি।
ঘরে ফিরেই রল্ফের ফোন!
অভিনন্দন।
জানলে কি করে?
শুধু আমার পেছনেই স্পাই নেই।
তোমার টিকটিকির লেজ কেটে দেবো আমি।
ও বেটা জার্মান, লেজ ছাড়াও দৌড়াতে পারে।
নীলের সঙ্গে কথা হলো কখন?
দুপুরেই ফোন করেছিল, খুব খুশি ও, একটা পার্টি দাও।
আমি পার্টি দিলে তো আবার মাতাল হয়ে যাও তুমি।
এবার হবো না।
দেবো তা হলে।
আমার মনের বিষয়টা তো বলেছি তোমাকে, এবার আমার মন বলছে একজন বড় বিজ্ঞানী হয়ে উঠবে তুমি।
বিজ্ঞানী হতে চাই না সেভাবে, হয়তো।
কেন?
হতে চেয়েছিলাম, কবি, গৃহী, কোনোটাই হই নি।
গৃহী না হতে পারার বিষয়টা জানি, দুঃখজনক, এখনও তো অনেক সময় আছে। কবি না হতে পারার বিষয়টা তো জানি না।
ছাত্রজীবনের শুরুতে কবিতা লেখা শুরু করেছিলাম, বলতে পারো এটা বাঙালির স্বভাব, কিন্তু আমার কবিতাগুলো মনে হয় ছিল অসাধারণ, কবিতার খাতাটা সঙ্গে আনতে যেয়েও আনি নি। ভাবতেও পারি নি এভাবে বিলীন হয়ে যাবে ওটা।
কি হয়েছিল?
আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বলি।
আবার লেখা শুরু করো, অসুবিধা কোথায়, যদি কবিতা-বোধ থাকে তোমার ভেতর।
ঐ লেখাগুলোয় আমার কবিতার বীজ রুয়েছিলাম, এতোদিনে ওগুলো গাছ হয়ে জন্মাতো, মুকুলিত হতো, রং ছড়ানো ভোরের আকাশে, সন্ধ্যার গোধূলি আলোয়, হয়তো বা।
আবার রোপণ করো।
হয় না, হবে না। বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করা যায়, কবিতা না এলে মাথা কুটে মরলেও কিছু হয় না।
ওটা বুঝি না আমি।
না বোঝাই ভালো।
যাহোক, পার্টি হচ্ছে কবে?
আমাদের দেশে একটা কথা বলে, রাঙা শুক্রবার।
মানে কি?
রঙিন যে শুক্রবার।
তাও বুঝি নি।
যে শুক্রবার কখনো আসে না।
দরকার নেই, শনিবারে হবে।
তাহলে হোস্ট তুমি।
হতে হলে হবো, কো-হোস্ট।
বাহ্!
রল্ফের চাপে পড়ে বিলেতের বিখ্যাত এক রেস্টুরেন্ট ‘জুয়েল ইন দ্য ক্রাউন’এ একটা পার্টি দেই, আমার জন্মদিনে। ইতোমধ্যে আমার আর একটা আর্টিক্যালের ফরাসী অনুবাদ বের হয়েছে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে বক্তৃতা দেয়ার আমন্ত্রণ পাই নিয়মিত। ব্যক্তি জীবন, অথবা আরো নির্দিষ্ট করে বললে, পারিবারিক জীবনটা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলেও কর্মজীবনে উন্নতি ঘটতে থাকে, শনৈ শনৈ!
চেরওয়েল ও আইসিস, উভয় নদী দিয়ে এতো জল সমুদ্রে গড়িয়ে গেছে কখন বুঝতেই পারি নি! জুলফিতে পাক ধরেছে, বান্ধবীরা ঠাট্টা করে। পৃথিবীর অনেক জায়গাই ঘুরে দেখা হয়েছে, সিদ্ধান্ত নেই সাব্বাটিক্যাল লিভ নিয়ে দীর্ঘ সময় কাটাবো দেশে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি পেয়ে যাই।
দেশে ফিরে অনেক বেশি সময় কাটাতে চাই বন্ধুদের সঙ্গে, এ দেখি ভিন্ন এক জগত, এতো বদলে গেছে সব! বন্ধুরা সব পরিবার-পরিজন চাকরি-বাকরি নিয়ে এতো ব্যস্ত, দম ফেলারও ফুসরত নেই কারো! কেন এই জীবন? কেউ ছুটি নিতে পারে না, অফিস চলবে কি করে? ব্যবসায়ী কোথাও যেতে পারে না, ব্যবসা লাটে উঠবে! প্রত্যেকেই অপরিহার্য করে তুলেছে নিজেদের। ঢাকা ছেড়ে গ্রাম-গঞ্জের বন্ধুদের সঙ্গে কাটানোর পরিকল্পনা করি, শান্তি পাই না, মানসিক ব্যবধান এতো বেড়ে গেছে, পুরোনো দিনের জাবর কাটা ছাড়া নতুন প্রসঙ্গ খুঁজে পাই না। কক্সবাজারের এক পুরোনো ইয়ারের সন্ধান করি অবশেষে। বাংলাদেশের অনেক কিছুর মতো সেও উধাও হয়ে গেছে।
সামাজিক শৃঙ্খলা, রাজনৈতিক শৃঙ্খলা, প্রভৃতি সবই ঠিক থাকে যদি অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় থাকে। স্বার্থান্বেষী চক্র অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিনকে বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দেশটাকে তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিণত করেছে। যে সকল মানুষের কাছে নুনের পয়সাও ছিল না, পান্তার বদলে পোলাও কেনার সামর্থ রাতারাতি এসে গেছে ওদের, জীবন যাপনের স্বাভাবিক হিসাব নিকাশ গুলিয়ে ফেলে ওরা। ঘাপটি মেরে থাকা রাজাকারের দোসররা মুখোশের আড়াল থেকে সুযোগ বুঝে বেরিয়ে আসে। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা জেনারেল, কর্ণেল তাহের হত্যার মাধ্যমে অতিজঘন্য রাজনীতির সূত্রপাত করেন। ভুঁইফোড় নব্যধনী, সুযোগ-সন্ধানী সামরিক ও বেসামরিক আমলা গোষ্ঠী, স্বার্থান্বেষী আওয়ামী গোষ্ঠী, পুনর্বাসিত রাজাকার, মাথাপচা ভণ্ড বামপন্থী, আস্তাকুড়ঘাটা বুদ্ধিজীবী নামধারী ঘোড়েল, প্রভৃতি, ও এক শ্রেণির পা-চাটা জনতার মিশ্রণে এক অভাবনীয় দল গড়ে তোলেন, যাদের না ছিল কোনো আদর্শ বা দেশপ্রেম! যে-রকম নৃশংসতায় বিরোধী কাঁটাগুলো পথ থেকে অপসারণ করেছিলেন তিনি, একই রকম হিংস্রতার সঙ্গে তাকেও সরানো হয়। পরবর্তী একনায়ক জেনারেল তার অসমাপ্ত কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করা শুরু করেছেন। এই কালো রাজনীতির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া দেশের জন্য অত্যন্ত কঠিন হবে। এতো অপরিকল্পিতভাবে একটা জাতি এগোয় কীভাবে, আরবরা যেমন এক সময় অন্ধকার যুগের বলে ওদের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য সব নিশ্চিহ্ন করা শুরু করেছিল, তেমনি পুরানো সব কিছু ভেঙ্গে ফেলে যেখানে যা খুশি গড়ে উঠছে, এমনকি শত শত বছরের পুরোনো গাছপালাও কেটে ফেলা হয়েছে। সভ্য দেশে হাইওয়ের কাছ থেকে বাজার, লোকালয় প্রভৃতি জনবহুল স্থান দূরে রাখা হয়, এখানে রাস্তার উপর বাজার বসানো হচ্ছে, গাড়ি-ঘোড়া আটকে থাকছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির এই বৈপরীত্য অবাক হওয়ার মতো, পেছনে হাঁটার প্রতিযোগিতা যেনো চলছে এখানে! সাধারণ মানুষের স্বপ্ন ধুলায় গড়িয়ে পড়েছে, মুষ্টিমেয় সুযোগসন্ধানীরা অর্থের পাহাড় গড়ে তুলছে। এসব দেখেশুনে ছুটি শেষ হওয়ার আগেই বিলেত ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়।
গত দু’বছর ধরে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেছে নিউইয়র্কের সেজানের সঙ্গে, ওকে ফোন করি, কাউকে না জানাতে বলে সে আমাকে। ভালোই হয়েছে, সময়টা কক্সবাজারে কাটিয়ে দেবো। অখণ্ড অবসর পেয়ে স্মৃতিগুলো উথলে ওঠে মাঝে মাঝে। কক্সবাজার যাই। হায়, এই সেই হাকসোবাজার! আদিবাসী রাখ্যাইনদের সুন্দর, ঝকঝকে ছোট্ট শহর বদলে এখন এতো কুৎসিত! নোংরা রাস্তাঘাট, চারদিকে আবর্জনার স্তূপ, মধুমাসের নীলমাছির মতো রঙিন মানুষের ঝাঁক, রিক্সায় অচল রাস্তা, পর্যটকদের ট্যাক্সিগুলোর অকারণ হর্ণ, এসব পেরিয়ে হোটেল সীসাইডের দুয়ারে পৌঁছি। সঙ্গে সেজান, আমি ডাকি সজনি, বছর তিনেক ধরে স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি, ডিভোর্স হয়ে যাবে শীঘ্র। নিউইয়র্কে প্রায়ই আমার হোটেল-রুমে আসে রাত কাটাতে, হলিডেতেও যায় মাঝে মাঝে, এবারই প্রথম দেশে আসে আমার সঙ্গে, আমি যেমন কাউকে জানাই নি, সেও না। নিউইয়র্কের ব্যার্ড কলেজে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশানস পড়ায় সেজান, জন্মসূত্রে আমেরিকান, দেশ থেকে পাত্র পছন্দ করে বিয়ে দিয়েছিল বাবা-মা, পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, আমেরিকায় যেয়ে চোখ-টোখ ফুটে সাদা মেয়েদের চাটা হয়েছে এখন, স্ত্রীর কোনো মূল্য নেই ওর কাছে, নব্যধনীদের যা হয়। ওর বাবা নাকি জেনারেলের দলের এক পাতি-মন্ত্রী, বাংলাদেশের মানুষেরা ওদের রায়ত, যা খুশি করা যায় এদের নিয়ে!
হোটেলের পাঁচতলায় সমুদ্রমুখী একটা রুম বেছে নেই, রেজিস্টারে তথ্য লিখতে যেয়ে কিছুটা বিড়ম্বনায় পড়ি, পৃথিবীর এতো দেশের এতো এতো হোটেলে থেকে এলাম কোথাও সঙ্গিনীর সঙ্গে ‘সম্পর্ক’ লিখতে হয় নি, এখানে এটা লিখতে যেয়ে মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত হই, কাউন্টারের লোকটার সন্দেহ সৃষ্টি না করার জন্য চট করে লিখে ফেলি ‘স্ত্রী’, সজনি এটা লক্ষ্য করে, কনুই দিয়ে পাঁজরে গুঁতো দেয়, বেশ শক্ত, প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করি না, রুমে ঢুকেই হেসে লুটিয়ে পড়ে।
এই যে ভাই, মিথ্যে পরিচয় দিচ্ছেন কেন?
উপায় তো ছিল না, এখানে ‘পার্টনার’ লিখলে সোজা পুলিশের তেরো খোপ।
রুম সার্ভিস ডেকে খাবার আনিয়ে নেই, ডাইনিংএ যেতে ইচ্ছে করে না, ঝুলবারান্দায় টেবিল পেতে খেতে বসি, চোখ জুড়িয়ে দেয় সামনের সমুদ্র, পেছনের নোংরা শহর মুছে গেছে স্মৃতি হতে, এমন সমৃদ্ধ একটা সৈকত থাকতে এদেশে পর্যটন শিল্পটাই গড়ে উঠতে পারছে না। রুমে টেলিফোন বেজে ওঠায় চমকে উঠি, কথা তো ছিল না! কে হতে পারে?
হ্যালো?
স্যার, আপনার গেস্ট এসেছে, কথা বলতে চান, দেবো?
কে?
সোয়েচিন।
সোয়েচিন! ও হ্যাঁ, দিন।
হ্যালো সোয়েচিন?
হ্যাঁ, সোয়েচিন, তুমি কেমন আছো?
আমি ভালো, তুমি?
আমিও ভালো।
জানলে কি করে আমি এখানে?
বলবো, তোমার ওখানে আসবো?
আসবে?
হ্যাঁ, আসছি তাহলে।
না হয় এক কাজ করো, তুমি ওয়েটিঙে বসো, আমি বেরিয়ে আসছি, এক সঙ্গে বেড়াতে যাবো কোথাও।
তাও হয়, আসো, ঠিক আছে।
ফোন রেখে ফিরে আসি খাবার টেবিলে। সেজান বুঝতে পারে ফেঁসে গেছি, চোখে ওর দুষ্টু হাসির ঝিলিক। কি করি, প্রাণের এমন বন্ধুকে নিয়ে এখন! সোয়ে সত্যিই আমার অন্তরের দোসর, আমার অনেক লেখার প্রথম পাঠক, আমার অনেক কবিতার চরণ ওর মুখস্ত, যা আমারও নেই। একজন উঁচুমানের পাঠক, ওর সিনেমা সংগ্রহ ছোটোখাটো একটা আর্কাইভ হয়ে যায়, এমন চলচ্চিত্র বোদ্ধা আমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ নেই, এমনকি যারা ছবি বানায়, ওরাও, অথচ সে কিছুই লেখে না, কিছুই বানায় না, কখনো কখনো গানে বুঁদ হয়ে থাকে, দেশের আনাচে কানাচে, এমনকি পশ্চিমবঙ্গেরও কোথায় কোথায় চলে যায় গ্রামীণ সব গান সংগ্রহের জন্য, সরাসরি এসব রেকর্ড করে নিয়ে আসে, উঁচুমানের শিল্পরসিক, কক্সবাজার ছেড়ে কোথাও যাবে না, নাম আসলে সোয়েব চৌধুরি। কক্সবাজারে আমাদের বন্ধুদের অধিকাংশই রাখ্যাইন, পান-ভোজনের নিষেধ-জালের বাইরে থাকার কারণেই হয়তো। সোয়েচিনকে দেখায়ও অনেকটা রাখ্যাইনদের মতো, ছোট নাক, ফর্সা, বেঁটে। ওকে যখন সোয়েচিন বানিয়ে ফেলি, প্রতিবাদ করে নি, বন্ধুদের মধ্যে এটা চালু হয়ে যায়, আমাকে গুম হয়ে থাকতে দেখে সেজান বলে_
ভাবাভাবির কিছু নেই, আমি এখন ঘুমোবো, নির্দ্বিধায় যেতে পারো তুমি।
তাই?
হ্যাঁ, সত্যিই ঘুম পেয়েছে, ক্লান্তিও লাগছে।
ঠিক আছে, ফিরতে দেরি করবো না।
না না, তা কেন! বরং রাতে না ফিরলেও পারো।
ও বুঝতে পেরেছে, আমার কক্সবাজার জীবনের গল্প বলেছি ওকে এক সন্ধ্যায়, কক্সবাজারের রাত মানে মাতাল, মদির, অধীর, চঞ্চল! পার্টনারের এই সুবিধে, কোনো দায় নেই তেমন, যা পুরোপুরি রয়েছে একজন স্ত্রীর কাছে। পাশ্চাত্যের মানুষেরা এটা বুঝেই সহজ সম্পর্কটা গড়ে নিয়েছে। বিশ্বের অপরাপর অংশের মানুষেরাও বুঝে নেবে ধীরে ধীরে, যাদের সামাজিক বিকাশ যত আগে হবে!
সোয়েকে দেখে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে এতোটা একই রকম রয়ে গেছে, শুধু নাকের দু’পাশের দাগদুটো নতুন মনে হয়, ছোটো ছোটো চুলে এক দু’টা সাদা দাগ! দু’জনে দু’জনকে কয়েক পলক দেখে পরস্পরে জড়িয়ে ধরি।
কেমন আছিস রে শোয়ে?
বরাবরের মতোই। তুই?
আমিও।
তা কেন?
কোনো কারণ নেই।
এরকম বলছিস কেন? বড় বিজ্ঞানী হতে চলেছিস, স্বপ্নের দেশে স্বপ্নের মতো জীবন, স্বপ্নের রাজপুত্র!
অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা ছাড়া।
বিয়ে করিস নি?
হয়ে ওঠে নি।
বলিস কি! বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।
তোর কি খবর?
বাস করি প্রেতরাজ্যে, নিজেই এক প্রেত, বিয়ে করেছি পেত্নী।
দেখাবি না পেত্নী?
তোকেও তো প্রেত হতে হবে তাহলে।
হলাম না হয়।
বাদ দে ওসব।
সত্যিই বউ দেখাবি না?
আমারও হয় নি রে।
অবাক কাণ্ড তো!
রিক্সায় চড়ি, কলাতলী সৈকতে প্রতিদিন একটা বৈকালিক বাজার বসে, স্থানীয় জেলেরা তাজা মাছ, শাক সবজি ও ফলমূল বিক্রি করে খোলা আকাশের নিচে। মাইকের শব্দে কান ঝালাপালা, গান বাজিয়ে যাচ্ছে কেউ, সেই সঙ্গে কারো মৃত্যু সংবাদ! এই সংস্কৃতি কারা গড়ে তুলছে, অথবা কীভাবে গড়ে উঠছে বুঝতে পারি না। স্বাস্থ্যকর স্থান বলে পরিচিত এখানে এই শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ, পরিবেশ-দূষণ, এসবের কোনো প্রতিকার নেই কেনো! এসব তো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, অথবা পূণ্যভূমি আরবের বাদশাহ, বা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এসে করে দেবে না, স্থানীয় জনগণকেই এসব ঠিক করতে হবে, নিজেদের যোগ্য নেতৃত্ব ঠিক করতে হবে, মানুষকে সচেতন করতে হবে, জাগাতে হবে, লোকাল ও কমিউনিটি কন্সেপ্ট গড়ে তোলার জন্য কেউ নেই কক্সবাজারে! মনে মনে ভাবি, এখানটারই বা দোষ দেই কেন? এ কন্সেপ্টটা তো দেশের কোথাও গড়ে ওঠে নি। সভ্য দেশগুলো এগিয়ে যেতে পেরেছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে, লোকাল ডেভেলপমেন্ট ব্যবস্থা গড়ে তুলে, আর আমরা আরো কেন্দ্রীভূত করছি ক্ষমতা! আরো আরো ক্ষমতা চাই, কেবল আমার হাতে, ঐশ্বরিক ক্ষমতা চাই। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে চেয়ে জেলা গভর্নর সিস্টেমটা যে চালু করতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু, তা যদি বাস্তবায়ন করা যেতো, দেশের অবস্থা হয়তো অন্য রকম হতো আজ। বিকেন্দ্রীকরণের বিকল্প তো কিছু নেই এখনো, আজ হোক, কাল হোক, এটা করতেই হবে। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়েও স্বৈরশাসকের মতো আচরণ করছে অনেকে, এসবের অবসান কি কখনো হবে!
আমাকে ভাবনায় ডুবে থাকতে দেখে শোয়েও চুপচাপ হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করি–
ওখানে কি বাজার করবি?
হ্যাঁ, মাছ ভাজা খাওয়াবো তোকে।
ফরেস্ট অফিসের উল্টোদিকে বাঁশের বেড়া দেয়া টিনের ছাউনি ঐ হোটেলটা আছে না?
আছে আছে, হোটেল নিরিবিলি।
হ্যাঁ নিরিবিলি, নিরিবিলি।
ওখানের চিংড়ি শুঁটকি ভর্তা খেতে ইচ্ছে করছে, লইট্টা মাছের লাল ঝোল, ছুরি শুঁটকি ও সিমের বিচির ঝোল, মগজ ভুনা, আমার জিভে জল জমে গেছে রে, এতো মজা করে রাঁধে কীভাবে ওরা?
হঠাৎ দু’একদিন অন্যরকম স্বাদ সব সময়ই ভালো লাগে, তাছাড়া পরিবেশ পরিস্থিতি, অনুকূল মানসিক অবস্থা, সব মিলিয়ে একটা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে, এর উপর, ওদের রান্না তো অবশ্যই ভালো।
সোয়েচিনের বাসায় এসে মনটা ভরে যায়, সরাসরি দোতলায় উঠে যাই, নিচের তলায় থাকে ওর এক বোন। বিধবা, দুটো বাচ্চা নিয়ে থাকে, উপর তলাটা ওরাই দেখেশুনে রাখে, ঘরের ভেতর ঢুকে মনেই হয় না বাইরে এতো ঘিনঘিনে, নোংরা কুৎসিত এক পৃথিবী রয়েছে। সব সময়ই রুচি বজায় রেখে জীবন যাপন করে সোয়ে, ধরে রেখেছে এখানেও, অনেক ব্যাচেলার বন্ধুর রুমে ঢুকলে দেখা যায় অগোছালো কাকে বলে। আমারও স্বভাব বলে, অগোছালো হওয়ার কথা। নটরড্যাম কলেজ হোস্টেলে থাকার কারণে পরিপাটি থাকার অভ্যাসটা গড়ে উঠেছিল, রয়ে গেছে এখনো।
দোতলার রান্নাঘরটা নাকি কালেভদ্রে ব্যবহার করা হয়, আজ কিছু সময়ের জন্য হবে, বুয়াকে বলে মাছটা কুটে দিতে, এক ব্যাগ ঘিমা শাক এনেছে, ওটা নাকি খাওয়াবে আমাকে, আমি তো অবাক, হুইস্কির সঙ্গে ঘিমা শাক! ও বলে, দেখতে দোষ কি? সাইড ব্যাগ থেকে বুশমিলস আইরিস হুইস্কির বোতলটা বের করে ওর হাতে দেই। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলে, দারুণ জিনিস তো, ঘিমা শাকের জন্যই তৈরি, হেসে উঠি আমি, প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের একটা রেকর্ড চাপিয়ে বলে ফ্রেশ হয়ে নে দাউদ, রাখ্যাইনদের লুঙ্গি আছে, একেবারে নতুন, মাড় না দেয়া, দেখ পরে কত আরাম। একটা লুঙ্গি ও ফতুয়া পরি, সত্যি আরাম, একটা গুমোর ফাঁস করে দেয় সে, রাখ্যাইন কাপড়ের চাহিদা আজকাল এতো বেড়েছে যে ওরা তাঁত চালিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না, নতুন আসা বাঙালিদের চাপে অনেক রাখ্যাইন বার্মায় পাড়ি দিয়েছে, এসব কাপড়ের অনেকটাই নাকি এখন আসে কুমিল্লার কুটির শিল্প হতে।
চুলো ধরিয়ে মাছ ভাজা শুরু করে সোয়ে, মাছ ভাজার গন্ধ বরাবরই প্রিয় আমার, খাওয়া শুরু করি, মাছটার কাঁটার রং সবুজ! জীবনেও সবুজ কাঁটার মাছ দেখি নি, মাছটা দেখতেও অন্য রকম, অনেকটা গজার মাছের মতো, আরো লম্বা ও চিকন, সাদা চকচকে আঁশ, খেতে ভালোই। বড় একটা পাতিলে ঘিমা শাক সেদ্ধ বসায়, ছোট্ট এক টুকরো নাপ্পি দেয় ওখানে, জিজ্ঞেস করি, এতো শাক কে খাবে? বলে, দেখাই যাক না। তাজা শাকের ভাঁপ থেকে ছড়ানো গন্ধও যেনো সবুজ। সোয়ে জিজ্ঞেস করে_
নাইখ্যংছড়ির বনযোগীদের ঘরে বানানো একটা মদ আছে, দেখবি নাকি একটু চেখে?
বোতল খুলতেই মৌলির তীব্র গন্ধে গা গুলিয়ে ওঠে, বলি_
মাপ চাই, আজকাল এসব পারবো না রে সোয়ে, বয়স হয়েছে না!
ঠিক আছে বলে বুশমিলের বোতল খুলে দু’জনের জন্য দুটো গ্লাসে ঢালে।
চীয়ার্স! তোর ভবিষ্যৎ সঙ্গিনীর জন্য।
চীয়ার্স।
এলকোহোল জাতীয় সবকিছুকেই আমরা মদ বলি কেন রে সোয়ে?
কেতাব থেকে এসেছে বোধ হয়, নেশা জাতীয় পানীয়কে মদ্য বলা হয়েছে ওখানে।
অথচ মদ একটা ভালো পানীয়, যদিও এলকোহোল আছে ওখানে, স্বাস্থ্যের জন্য ভালো এটা।
এলকোহোল তো অনেক অষুধেও আছে, কাশির অষুধেও নাকি আছে, ওসব বোঝাবি কাকে?
নন-এলকোহোলিক মদও আছে অনেক।
ঘিমা শাক নিয়ে আসে দু’বাটি, এক চামচ মুখে দেই, ভাবতেও পারি নি এতো স্বাদ, পানীয়ের সঙ্গে যখন আস্ত মাছ ও সব ঘিমা শাক শেষ হয়ে যায়, জিজ্ঞেস করে সোয়ে_
কম্বিনেশানটা ঠিক ছিল?
বিশ্বাসও করতে পারি না সোয়ে! আসল জহুরী তুই।
আমার কোনোটাই নকল নেই রে দাউদ। বছর চারেক আগে একটা দাঁত ফেলে দেয়ার পর নকল লাগাতে চেয়েছিল, দেই নি।
হো হো হো!
কথা প্রসঙ্গে সোয়ে প্রস্তাব দেয় ময়মনসিংহ গীতিকার পালাগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ করে ইউরোপে অপেরার মতো করে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যায় কিনা। পঞ্চাশ ষাট বছর আগে এগুলোর ইংরেজি অনুবাদ হওয়ার পর ইউরোপের মনীষীরা লোকসাহিত্যের রত্নভাণ্ডার বলে প্রশংসা করেছিল এগুলোর, অথচ এসব রত্ন আমরা চেয়েও দেখি না, রাষ্ট্রীয়ভাবে এসব চিন্তা করার যোগ্যতা পোষা ভৃত্যদের নেই, গবেষণার নামে দরিদ্র জনগণের কোটি কোটি টাকা লোপাটই করবে শুধু এরা।
কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছি অনেক আগে, এখন ভাবতে কষ্ট হয়, একসময় এতো ভালো কবিতা লিখতাম, কতো জায়গায় ছাপা হয়েছে সেসব, এতো এতো প্রশংসা শুনেছি, অথচ এখন শুধু পাঠের মধ্যেই সীমিত সাহিত্য, নির্মাণের প্রশ্ন মাথায়ই আসে না। স্বাধীনতা যুদ্ধে কতজনে কত কিছু হারিয়েছে, কত আপনজন, প্রিয় বস্তু! আমার গেছে সব চেয়ে প্রিয় কবিতার খাতাগুলো, ওসব থাকলে হয়তো আবার প্রেরণা পাওয়া যেতো, সূত্র অনুসরণ করা যেতো।
সোয়ের প্রস্তাবটা মাথার ভেতর খেলা করে, পালাগুলোর ইংরেজি অনুবাদ হয়তো করতে পারবো, কিন্তু সুরগুলোর নোটেশান তো ইউরোপীয় কোনো সঙ্গীতজ্ঞকে দিয়ে করাতে হবে, তারপরে হয়তো ভালো একটা দল দিয়ে উপস্থাপন করতে হবে, নোটেশান তৈরি করাটা বোধ হয় মূল কাজ হবে, মিস কোরবিনের কথা মনে পড়ে, সে কি করবে এটা? বাংলার সুরটা শুনে শুনে যদি কম্পেজিশানটা করতে পারে তাহলে অনুবাদটাকে আবার সেভাবে বদলে নেয়া যাবে। চুপ করে থাকতে দেখে সোয়ে জিজ্ঞেস করে–
ঝামেলায় ফেললাম?
আরে না না, বরং অসাধারণ প্রস্তাব দিয়েছিস একটা, ওটা নিয়েই ভাবছি।
রাত দশটা পেরিয়েছে, প্রায় নীরব হয়ে গেছে শৈল-শহর কক্সবাজার। চমৎকার একটা চাঁদ আকাশে, ইচ্ছে করে সৈকতে যেয়ে একটু ঘুরে বেড়াই, এ সমুদ্রটা এতো আপন, সসাগরা পৃথিবীর সব ক’টা মহাসমুদ্রই দেখা হয়েছে, অসংখ্য সাগর উপসাগর দেখেছি, অথচ এটার স্বরই যেন আলাদা। এটার তাপমাত্রা, শব্দ, ঘ্রাণ, সবই যেন বাংলার। ইউরোপ আমেরিকার সমুদ্রের ধারে হালকা পোশাকে বেশি সময় কাটাতে পারি না, আরবদের সমুদ্র কখনোই আকর্ষণ করে নি আমাকে, অথচ এখানে মনে হয় সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারি। সোয়ে জিজ্ঞেস করে, এসব মিস করি কিনা! মনে মনে ভাবি, মিস করি না কোনটা? ঘর থেকে বাইরে বেরোলে মিস করি ঘর, বিশ্বাবিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এলে ওখানটা, এখন বিলেতের সবকিছু, বিলেতে থাকলে দেশের সবকিছু, এভাবে ভাবলে তো অসুস্থ হয়ে যেতে হবে। এভাবেই জীবন চলে, সবকিছুই হারাই আমরা, কোনোটা ক্ষণিকের জন্য, কোনোটা চিরতরে। যা ফিরে ফিরে পাই অনেকবার, অন্তরে গেঁথে যায় ওটার স্মৃতি, সেজন্য অনুভবটাও অনেক বেশি তার।
ঘণ্টাখানেক সাগরপাড়ে থেকে ক্ষুধা লেগে যায়, জিজ্ঞেস করি–
নিরিবিলি খোলা?
হ্যাঁ, অনেক দেরিতে বন্ধ করে ওরা। আর বন্ধ করে দিলেই বা কি, আমার জন্য সারা রাত খোলা রাখবে ওরা।
খুব জনপ্রিয় তুই!
জনপ্রিয়তা না, ভালোবাসা।
নিরিবিলিতে তখনো বেশ কাস্টমার। কোনার একটা টেবিল খালি হলে বসি ওখানে যেয়ে। আমার প্রিয় খাবারগুলো আনাতে বলে সোয়ে। বলি_
একবারে সব আনতে নিষেধ কর, এক দু’টা আইটেম করে যেনো আনে। দারুণ স্বাদের করলাভাজি করেছে একটা, ওটা দিয়েই পেট ভরে খেয়ে ওঠা যায়। খেতে বসে আমার সজনির কথা মনে পড়ে।
ওকে একটা টেলিফোন করা যায়? জিজ্ঞেস করি সোয়েকে। একটু একলা কথা বলতে চাই, কেউ কান পেতে রাখুক, এটা চাই না।
তাহলে তো বাসায় যেতে হবে।
তাই সই।
খাওয়া-দাওয়া সেরে গেলে হয় না?
আবার এসে খাবো, ক্ষতি কি?
পাগলামো পেয়ে বসেছে। বেয়ারাকে বুঝিয়ে বলে সোয়ে। খুশি মনে সম্মতি জানায়। রিক্সা নিয়ে চলে আসি সোয়ের বাসায়।
সজনি?
কোথায়?
খুব কাছে তোমার।
হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, একেবারে কোলের কাছে।
খেয়েছো?
না।
খাবার নিয়ে আসবো?
না, আসতে হবে না। সত্যিই ঘুমাবো আমি।
তাহলে খাবার পাঠিয়ে দেই?
দিতে পারো।
ঠিক আছে, পঠিয়ে দিচ্ছি।
ইচ্ছে করলে পুরোনো বান্ধবীদের সঙ্গেও কাটাতে পারো আজ।
না সজনি, ঐ বয়সটা নেই। বলেছি তো তোমাকে এলিনার কথা, ঐ উত্তাল সময় আর কখনো আসবে না এ জীবনে।
দু’এক রাতের জন্য এলে ক্ষতি কি?
না সজনি, সোয়ের সঙ্গে আড্ডায় মেতেছি।
ঠিক আছে, অসুবিধা নেই।
সজনির সঙ্গে আমার বোঝাপড়াটা এতো ভালো যে পারস্পরিক শারীরিক প্রয়োজনের বাইরে তৃতীয়জন যে কারো জন্যই এসে যেতে পারে, দু’জনের কেউই এতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করি না। হোটেলে ফিরে এসে আবার খেতে বসি, সজনির জন্য খাবার পাঠিয়ে ওর হোটেলে ফোন করে দেয় সোয়ে, যেনো রুমে পৌঁছে দেয়। খেয়ে-দেয়ে ফিরে আসি সোয়ের বাসায়, মাথার ভেতর ময়মনসিংহ গীতিকা, অনেকগুলো পালা-গান বাজিয়ে শোনায় সোয়ে। এতো বাজে রেকর্ডিং! যন্ত্র বাজানো একেবারে যা-তা, অথচ সুর ও বাণী হৃদয় স্পর্শ করে গভীরভাবে, এসব যদি আধুনিক যন্ত্রে উপস্থাপন করে অপেরা নির্মাণ করা যায়, আমার ধারণা, বিশ্বে আলোড়ন তুলবে, সখিনা বিবির পালা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি।
১০
এতো নিরুচ্ছ্বাস ফেরা কখনো হয় নি আর, ফেলে আসা দেশের জন্য বুকের ভেতর চাপা ব্যথা, সেই সঙ্গে মুক্ত-বিশ্বের জাগতিক সব প্রাপ্তিগুলোর প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ থাকে, কোনো কিছুই নেই এসবের, এক ধরনের নির্লিপ্তির ভেতর ডুবে আছি। ফেরার কথা জানাইও নি কাউকে, বাসায় ঢুকে জানালা খুলে ঘরের গুমোট বের করে দেই, রল্ফ যে প্রায়ই এসে ঘরদোর পরিষ্কার করে রেখে গেছে বোঝা যায়। শাওয়ার নিয়ে শুয়ে পড়ি, খেতে ইচ্ছে করে না কিছু, ঘুম আসে না। পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি, কাজের মধ্য দিয়ে ভুলে থাকতে চাই সব।
কোনো কোনো বিকেলে আইসিস নদী বরাবর হাঁটি একা একা, খুঁজে বের করার চেষ্টা করি নদীর ঐ অংশটা, যেখান দিয়ে গরুগুলো পিঠে বোঝা নিয়ে পেরিয়ে যেতো নদীটা। আমার পিঠে এখন আমারই জীবনের বোঝা, কোথাও পেরোতে হবে এ নদীটা, নামাতে হবে বোঝা, ক্লান্ত আমি, ভীষণ ক্লান্ত এখন। মনে মনে ভাবি গরুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অক্সফোর্ডের নাম, যারা রেখেছিল তারা কি জানতো একদিন জ্ঞানীদের রাজ্য হবে এটা! গরু ও জ্ঞানী, পার্থক্য কত এ দু’জনের? ইংরেজরা একসময় গর্ব করে বলতো অঙ্ফোর্ডের চেয়ে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পৃথিবীতে নেই, ইউরোপের অন্য অংশ কখনোই এটা মেনে নিতো না। ইংরেজদের খেলাধুলা প্রীতির সঙ্গে মিলিয়ে অক্সফোর্ডকে কটাক্ষ করতে ছাড়তো না। অক্সফোর্ড থেকে পাশ করেছো? কি বিষয়ে, ক্রিকেট না ফুটবল? এরকম অনেক কৌতুক আছে অক্সফোর্ডকে ঘিরে।
নিজেকে নিয়ে ভাবতে ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে। এগিয়ে আসছে সন্ধ্যা, কেরোলকে সঙ্গে নিয়ে এমন অনেক সন্ধ্যা কাটিয়েছি এই নদীটার তীরে, সূর্যের সোনালি রং এখনো পাহাড়ের চূড়ায় আলো ছড়ায়, নদীর কাছাকাছি গাছপালায় ধূসর ছায়া, পুরোনো ঔক গাছের ছায়াগুলো মিলিয়ে যাওয়ার আগে নিজেদের প্রসারিত করে যত দূরে সম্ভব, সন্ধ্যার অনালোকিত অনুভব বুকের ভেতর প্রবেশ করে, মনে হয় নিজের ভেতরও নেমে আসছে অনাগত রাতের অন্ধকার, কেরোল মারা যাওয়ার পর লেইডি মালকিনের ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দেই নি, কোনো কোনো দিন ওখানে কাটিয়ে আসি কিছু সময়, সব কিছুতেই এতো বেশি প্রাণবন্ত ওর উপস্থিতি! অথচ মানুষটা নেই, এখন বুঝি, শুধু কেরোলকেই ভালোবেসেছিলাম আমি, লেইডি মালকিনের সঙ্গে প্রতি মাসে দেখা হয় ভাড়া দেয়ার সময়, প্রায়ই বলে বাসাটা ছেড়ে দিতে, এ পাগলামীর অর্থ হয় না, পারি না, ছেড়ে দিতে পারি না ওটা।
রল্ফের সঙ্গে ব্যবহার প্রায় ঝগড়ার পর্যায়ে চলে যায় কখনো কখনো, বোঝাপড়াটা এতো ভালো আমাদের যে দু’জনেই সামলে নেই। একদিন রেগে যেয়ে বলি, ইউ আর দ্য ওনলি অক্স ইন অক্সফোর্ড সিটি হু ডাজ নট ইট গ্রাস। হেসে বলে, বিকজ আই লিভ দেম ফর ইউ। আমি হলে হয়তো আর কথাই বলতাম না ওর সঙ্গে।
এমন একটা জীবনই কি চেয়েছিলাম আমি? অথবা কিছুই চাই নি, কোনো স্বপ্ন ছিল না আমার, যেভাবে এগিয়ে গেছে জীবন, ভেসে গেছি সেভাবে, প্রতিকূল স্রোতে এখন চরায় আটকে গেছি, ক্লান্ত মানুষ যেমন খরকুটো ধরে বাঁচতে চায়, তেমনি হাত বাড়াই কোরবিনের দিকে। ফোন করি এক দিন_
হ্যাঁ, মিস কোরবিন, আমি . . .
কে তিনি?
আমি …, আপনার উপর তলায় ভাড়া ছিলাম।
বিশ্বাস করতে পারি না কোরবিন চিনে নি আমাকে, না চেনার ভান করতে পারে এটা ভাবাও কষ্টকর। বলে_
বলুন, কীভাবে সাহায্য করতে পারি।
তাৎক্ষণিকভাবে কোনো কথা না পেয়ে জিজ্ঞেস করি_
আপনার উপর তলাটা খালি আছে?
না, এখন ভাড়া দেই না ওটা, ছোট্টো একটা মিউজিক স্কুল দেয়া হয়েছে ওখানে।
ও আচ্ছা। একটু থেমে বলি, আপনার সঙ্গে কি সাক্ষাতে একটু কথা বলতে পারি মিস কোরবিন?
কি বিষয়ে বলুন তো?
সাক্ষাতে বলতে চাই।
এড়িয়ে যেতে চায়। বলে–
দুঃখিত মি. এব্রাম, আমার হাতে তো সময় নেই। সময় হলে জানাবো, বাই।
ফোন রেখে দেয়। ভাবতেও পারি না এভাবে প্রত্যাখ্যাত হবো, কি আছে ওর, নিজেকে কেন এতো নামিয়ে নিলাম! অবশেষে মেনে নেই বিষয়টা, প্রত্যেকেরই তো নিজের ইচ্ছের স্বাধীনতা রয়েছে। মরিয়া হয়ে আরেকদিন ফোন করি–
মিস কোরবিন, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম সংগীত বিষয়ে, আমাদের কিছু লোক-সংগীত আছে, ইচ্ছে হয়েছিল আপনাকে শোনাতে, আপনাদের পিয়ানোয় যদি ওগুলোর নোটেশান করে দিতে পারেন, এটার জন্য যথাযোগ্য সম্মানী আপনাকে দেবো।
কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে_
ঠিক আছে, নিয়ে আসুন এক দিন।
পরের রোববারই যাই ওখানে, সখিনা বিবির পালা নিয়ে, ওসব শুনে বলে কিছুই বুঝতে পারছি না, আমার মনে হয় না কিছু করতে পারবো আমি।
ওয়ার্ডিংগুলো না বুঝলে কিছু করা সত্যি মুস্কিল, ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেবো আমি, আপনি শুধু সুরটা তুলে দিন।
আচ্ছা দেখবো চেষ্টা করে।
সামান্য আন্তরিকতাও নেই কোরবিনের ব্যবহারে, পুরোপুরি আনুষ্ঠানিক।
আমি কি পরের হপ্তায় আসবো?
না, আরো একটু সময় দিন।
দু’হপ্তা পরের রোববার যাই আবার, কিছুটা কাছাকাছি সুর তুলেছে পিয়ানোয়, শব্দগুলোকে বসিয়ে ঐ সুরে গেয়ে শোনাই, কিছু শব্দ বদলে দেয় কোরবিন, কয়েক হপ্তা চেষ্টার পর একটা অবস্থায় পৌঁছে ওটা। জিজ্ঞেস করে, কি করবো এটা নিয়ে। বলি, যদি সঠিক মানে এটাকে পৌঁছে দেয়া যায়, উপস্থাপন করবো। এখনো অনেক দূর যেতে হবে, তবে যেটুকু হয়েছে, ভালো কোনো কোম্পোজারকে বোঝানো যাবে অন্তত যে বিষয়টা কি।
কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে কোরবিন, সংগীতের জগত নিয়ে জীবন পার করে দিচ্ছে, কিছুটা সুর মেশানোর চেষ্টা করি আমিও। কোনোভাবেই খোলসের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে না, মনে হয় প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে। পালাটার একটা অংশে ওকেও গলা মেলাতে বলি, সুরের সঙ্গে ভালোভাবেই মিশে যায়, আবেগের জায়গাগুলো বুঝিয়ে বলি, চেষ্টা করে সেসব সুরে ধরার জন্য। একদিন কিছুটা আবেগাকুল মুহূর্তে জিজ্ঞেস করি, আরেকবার তোমার হাতটা ধরার অনুমতি দেবে কোরবিন?
স্পষ্ট বলে: না।
এর পর আর এগোনো যায় না, জীবন থেকে কোরবিনের পৃষ্ঠাটা ভাঁজ করে রাখি।
এখন কষ্ট হয় বাবার জন্য, আমাকে নিয়ে একটা স্বপ্ন ছিল ওর। কৌতুক করে দেয়া রল্ফের পরামর্শটাই আদর্শ মনে হয়, ও বলে, একটা দেশি মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে আসো, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। হয়তো ওর অনুমানটাই ঠিক, কিন্তু এ বয়সে বিয়ের উপযোগী কাউকে পাওয়া অসম্ভবের কাছাকাছি। জীবনের শুরুতে, যাকে হয়তো ভালো লেগেছিল, আমার আদর্শ ছাত্রী, এখন নিশ্চয় নানি-দাদি সে! চাচার মেয়ে আয়েশাও তাই। এলিনার কোনো খোঁজ জানি না, শুনেছিলাম দেশে যেয়ে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিল, বিয়েশাদী কোরে ভালোই নাকি আছে।
মাথা থেকে এলিনাকে নামাতে পারছি না ক’দিন থেকে। বিশ্ববিদ্যালয় দু’দিন বন্ধ থাকায় উইকেন্ডের সঙ্গে ঐ দুদিন যোগ করে মাঝখানে একদিন ছুটি নিয়ে ইসলামাবাদের বিমানে উড়াল দেই। তৃতীয় বিশ্বের একজন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা যে কত বড় এ্যাডভেঞ্চার বুঝতে পারি। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে, বিলেতের একজন বিজনেস ডেলিগেট দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখা করার সুযোগ পাওয়া যায়। অনেক বছর পর আবেগ সামলানো একটু কঠিন হয়, প্রায় একই রকম আছে এলিনা, কালো ফ্রেমের একটা চশমা উঠেছে চোখে, মাথায় হিজাব, আচরণে গাম্ভীর্য।
কেমন আছেন?
ভালো, আপনি?
কোনো কাজে এসেছেন?
না, আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য শুধু, এটারও কোনো কারণ জানি না।
চা খাবেন?
আপনার কোনো সমস্যা না থাকলে।
চা দিয়ে বেয়ারা বেরিয়ে যাওয়ার পর বলে_
এটা তো আমার কাজের জায়গা, কথা বলার জায়গা না, বলুন কি জন্য এসেছেন।
কোনো কিছুর জন্যই আসি নি এলি, তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যই শুধু।
কণ্ঠে আমার আকুলতা ছিল কিনা জানি না, চুপ করে থাকে এলিনা। আবার বলি_
মনের সঙ্গে পেরে উঠি নি এলি, মন চাইছিল, তোমাকে একবার দেখি। দেখেছি, খুব খুশি হয়েছি, দেখা করার অনুমতি দিয়েছো তুমি। এজন্য অনেক ধন্যবাদ। যদি চাও, চলে যেতে পারি এখন।
না, বসো।
চুপচাপ বসে থাকি। নোট বই ঘেঁটে জিজ্ঞেস করে–
পরশু পর্যন্ত আছো?
শুক্রবার… হ্যাঁ। তুমি চাইলে সারা জীবনও থেকে যেতে পারি।
কথার যাদু এখনও তেমনি আছে তোমার!
শুধুই কথার?
দুপুরে একটা জায়গায় দেখা করতে বললে পারবে?
আশা করি, যদি তোমার দপ্তরের মতো না হয়।
একটা রেস্টুরেন্টের ঠিকানা দিয়ে বলে, বারোটার মধ্যে পৌঁছে যেও, কোনো কারণে আমার একটু দেরি হলেও মনে কিছু করো না।
না না, ঠিক আছে।
দুটো দিন ইসলামাবাদ শহর দেখে কাটিয়ে দেই। রেস্টুরেন্টের যেখানে বসতে বলেছিল একটু আগে থেকেই বসে থাকি ওখানে যেয়ে। ফ্রেশ ম্যাঙ্গো জ্যুস পান করি, সাড়ে বারোটায় আসে এলিনা। এসেই বলে_
আমার তো একটু সমস্যা আছে, বোঝোই। ফ্যামিলি রুম আছে এখানে, চল একটায় ঢুকে পড়ি। উঠে যাই, ম্যানু দেখে খাবারের অর্ডার দেয় এলিনা।
এবার বলো, কেন এসেছো।
কেন বিশ্বাস করছো না এলি!
একটু কঠিন। তা ছাড়া এতো বছর পর!
কথায় কথায় অনেক কথা বলা হয়ে যায়, খুব তাড়াতাড়ি বরাদ্দ সময় শেষ হয়ে যেতে থাকে। খুব ব্যস্তভাবে নাকি জীবন পার করে দিচ্ছে। বাইরে থেকে ওকে মনে হয় খুব ক্ষমতাবান! প্রতিরাতে স্বামীর পাশবিক অত্যাচার, বছর বছর বাচ্চা, শরীর ক্ষয় করে শেষ পর্যন্ত অস্ত্রোপচার করে ওটা ফেলেই দিয়েছে। গত বছর থেকে স্বাস্থ্য একটু ভালো যাচ্ছে। এই রাজনীতিটা হচ্ছে বেঁচে থাকার একটা অবলম্বন, দ্রুত জীবনটাকে শেষ করে দেয়ার ভালো একটা পথ, কারো প্রতিই কোনো আকর্ষণ নেই, দায় বা ভালোবাসাও নেই, এমনকি ছেলেমেয়েদের প্রতিও না, বড় মেয়েটা সংসারের সবকিছু দেখে, রাজনীতি চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে রেখেছে স্বামী, ওর ব্যবসায় দারুণ সুবিধে হচ্ছে এতে, ব্যবসাটাই ওর কাছে মুখ্য, আমি অথবা পরিবার কোনো কিছুই না ওর কাছে। যাদের জন্য রাজনীতি করে ওদেরকেও ভালোবাসে না, ওরাও ভালোবাসে না ওকে। দু’বার গুলি করেছে গাড়িতে, বাসায় বোমা মেরেছে, নিরাপত্তা-রক্ষী ছাড়া চলা ফেরা করতে পারে না। একটা মার্কেটে সপিংএর জন্য যেয়ে, টয়লেটে ঢুকে বোরখা বদলে অন্য মানুষের বেশে এখানে এসেছে। ঐ সপিং সেন্টারের বাইরে ড্রাইভার এখনো অপেক্ষায় আছে, ট্যাক্সিভাড়া করে এসেছে এখানে।
খুব ঝামেলায় ফেলেছি তোমাকে এলি।
না ঝামেলা না, অনেকদিন পর একটু মন খুলে কথা বলতে পারছি, আর কিছু না।
যদ্দুর শুনেছি, জেনেছি সুখে আছো তুমি!
সুখ দুঃখ বুঝি না, জীবনটা যাপন করে যাচ্ছি।
ওটা করতে পারাই বোধ হয় অনেক বড় এলিনা।
খুশি হলাম, আমার খোঁজ খবর তুমি নিয়েছো জেনে। তোমার খবর বল।
কোনো খবর নেই এলি।
বিয়ে শাদী, ঘর সংসার?
হো হো হো করে হাসতে যেয়েও হাত চাপা দেই মুখে। এটা তো আবার রামগরুড়ের ছানাদের দেশ!
কেন?
কোনো কারণ নেই।
চুপচাপ কিছু সময় কাটে। ওরা এত ভালো কাবাব বানায় কীভাবে? এটা সেটা খাই, বোরহানিটায় ঝাল একটু বেশি যেন, নীরবতা ভেঙ্গে বলে এলিনা_
ভেবেছিলাম বড় মেয়েটাকে বিলেতে পাঠাবো পড়াশোনার জন্য, নিজের জীবনের কথা ভেবে ক্ষান্ত দিয়েছি।
সবার জীবন একই পথে এগোয় না। কারোই না।
তা ঠিক, তারপরেও মনে হয়েছে, যে সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত এদেশের মানুষ, তা মেনে নিয়েই জীবন যাপন করুক, ওখানে যেয়েও যে অন্য রকম কিছু একটা হবে তার নিশ্চয়তা কি?
অনেকেরই তো হচ্ছে।
আমার তো হয় নি, ভয়টা এজন্য।
তোমার বাবা-মা, বোন কেমন আছে?
ভালোই, বোনের বিয়ে হয়েছে, ব্যবসাটা ওরাই চালায়, বেশির ভাগ সময় বাবা-মা এখানে কাটায়।
চলে আসো না আবার?
কেন?
জীবনটাকে আরেকটা মোচড় দিয়ে দেখতে দোষ কি?
লোভ দেখাচ্ছো?
তোমাকে দেখানোর মতো লোভনীয় কোনো কিছুই নেই আমার এলিনা, নিজের জন্যই আসো।
আর কোনো কিছু চাওয়া পাওয়ার নেই আমার!
কত বিচিত্র আনন্দ আছে পৃথিবীতে, সংসার যাপনটাই তো সব না।
প্রাচ্য দেশের নারীদের জন্য এটাই প্রধান।
জীবনে অপ্রধানের গুরুত্বও কম না। ছুটি কাটাতে আসো, বেড়াতে আসো, এমনিতেই আসো, আমার জন্য আসো।
আশ্চর্য সুন্দর ওর চোখ দুটো তুলে তাকায়, মুক্তোর মতো জলের বিন্দু যেন জমতে শুরু করেছে ওখানে। বলে_
আমার শীত লাগছে। শরীরে জড়ানো ওড়না খুলে পাতলা করে ছড়িয়ে দেয় শরীরের একপাশে। বলি_
জানালা দিয়ে একবার বাইরে তাকাও। তুষার ঝরছে, কি দারুণ তুষার, তোমার গাড়িটা কত পুরু তুষারের নিচে চাপা পড়েছে দেখেছো!
মুহূর্তে যেনো বিদ্যুৎ খেলে যায় ওর ভেতর, অকস্মাৎ স্মৃতির সুখে ভেসে যেয়ে হেসে উঠতে চায়, সেই পুরোনো অপ্সরা হাসি, যাদুর রঙিন হাসি, সঙ্গে সঙ্গে ওড়না চাপা দেয় মুখে, চোখে কিশোরীর লজ্জানম্র চপলতা।
ভুলেই গেছিলাম যে আমি বিলেতে নই এ মুহূর্তে!
আমারও তাই মনে হয়েছে এলিনা।
অতীত সুখের উল্কাপিণ্ডটা নেড়েচেড়ে দেখছে যেনো এলিনা, ওর চোখেমুখে খুশির লাবণ্য।
তোমার হাতটা একটু ধরি এলি?
চুপ করে থাকে। করতলের ভেতর দেবীর আরতির জন্য নেয়া অর্ঘ্যের ফুলের মতো কোমল হাতের স্পর্শ নিয়ে বসে থাকি অনেকক্ষণ, পা থেকে জুতো খুলে ওর দু’পায়ের পাতার উপর চেপে রাখি। আবেগ আর ধরে রাখতে পারে না এলিনা, চোখের জল হয়ে বেরিয়ে আসে ছাই-চাপা দুঃখ, হালকা হতে দেই ওকে। অনেকখন পর বলে_
তুমি যদি বলো আসবো।
আসো এলিনা।
স্বামী, সংসার, দেশ, সব ছেড়ে-ছুঁড়ে আসবো।
না, সব রেখেই আসো।
কি বলছো তুমি? দ্বিচারিণী হতে পারবো না আমি।
একটু যেনো রুক্ষ ওর কণ্ঠ।
দ্বিচারিণী হতে বলছি না এলিনা, নিজের জন্য আসো, অন্তরের জন্য আসো, আবারও বলছি আমার জন্য আসো।
একটু থেমে বলি–
শরীরের ঐ চাহিদা আমার আর নেই।
একটু যেন লজ্জা পায়, বলে–
আমার আছে, পুরোপুরি।
আবারও হাসি দু’জনে।
ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, মাই গড, আমার ড্রাইভার বোধ হয় দুশ্চিন্তা শুরু করেছে।
ওঠার আগে বলি_
তাহলে এই কথাই রইলো এলি, তুমি আসছো, আগামী তুষারের আগেই।
জানি না, হয়তো শুধু তুষারই আসবে।
তুমি না এলে বিলেতে এবার তুষার আসবে না এলিনা!
না আসুক।
না এলি, দুটোই চাই আমি, তুষার ও তোমাকে।
একটা চুমো দেবে আমাকে, দাউদ?
ওর ঠোঁটে ঠোঁট রাখি, এতো বিদ্যুৎ! এতো প্রবল আকর্ষণ, কোথাও পাই নি এ জীবনে!
বিলেতে ফিরে আসি, মনের ভেতর সুখের প্রজাপতিটা ওড়াউড়ি শুরু করে আবার। পুরোনো প্রেমিকারা নতুন করে উদ্দীপনা ছড়াতে শুরু করে, আইসিস নদী দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া জল দেখি। সব কিছুই সুন্দর, প্রকৃতির নিয়মে স্বাভাবিক। অথচ আশ্চর্য, এবারের শীতে তুষার ও এলিনা, কেউই আসে না! অনেক বছর পর একটা ব্যতিক্রমী শীত এসে আবার ফিরে যায় উত্তরে।
রাজনীতি করে প্রাজ্ঞ হয়ে ওঠেছে এলিনা, জীবনের হিসাবটায় ভুল করে নি এবার, আবেগে ভেসে যায় নি, দ্বিতীয়বার ঝুঁকি নেয় নি, ভালোই করেছে।
আমি এ জীবন লইয়া কি করি?
জন্মগতভাবে পাশ্চাত্যের হলে এমন একটা জীবন মেনে নেয়া খুব কঠিন ছিল না, কিন্তু বাবার মুখের দিকে তাকাতে পারি না, বাবাকে সুখী দেখতে চাই, বাবার একটা স্বপ্ন ছিল, ওটা সফল দেখতে চাই। আমাদের ভাষায়, বা আমার, ছেলেকে মানুষ করার জন্য বিলেতে পাঠিয়েছিলেন বাবা, কীভাবে আর মানুষ হবো, উচ্চশিক্ষা যতটুকু সাধ্য গ্রহণ করেছি। ডক্টরেট, পোস্ট-ডক্টরেট সবই করেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছি। অর্থ, বিত্ত, সুখ, নারীসঙ্গ সবই উপভোগ করছি। শুধু একটা সংসারের অভাব, আমার দিক থেকে, খুব যে অসুবিধায় বা না পাওয়ার মধ্যে আছি, তা তো না।
বাবা তাহলে ঐ সব জাগতিক সুখের সঙ্গে ঘরভরা নাতি-পুতি চেয়েছেন, আমার অন্য ভাইয়েরা সেসব খুব যত্ন নিয়ে উৎপাদন করে চলেছে। বাবার নামে প্রচুর জমিজমা কিনি, ভাইয়েরা মহাখুশি, বাবা মারা যাওয়ার পর এসব সম্পত্তি ওদেরই হবে।
বাবাকে খুশি করা, ও রাখার জন্য বলি–
একটা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে দেই, আপনি পরিচালনা করেন ওটা।
বেশ খুশি হয়ে ওঠেন। একটা ভালো প্রস্তাব যেন দিয়েছি। একটা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জন্য দশ একরের মতো বড় এক খণ্ড জমি গ্রামে পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত পাকা রাস্তা থেকে কিছুটা দূরে সব মিলিয়ে সাড়ে পাঁচ একরের কয়েক টুকরো জমি একসঙ্গে করা যায়। সামনের রাস্তা পর্যন্ত জমির ছোট ছোট খণ্ডগুলো দ্বিগুণ-আড়াইগুণ দামে কিনে চওড়া রাস্তা বানিয়ে দুপাশে গাছ লাগিয়ে জমি প্রস্তুত করি। বছর খানেকের মধ্যেই ভবন তৈরি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাজকর্ম শেষ করি। ওটার নাম রাখতে চাই বাবার নামে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে ওঠেন বাবা, ‘না, ওটা তোমাদের মায়ের নামে’ মুহূর্তের জন্য বাবার চোখে প্রেমের স্ফুলিঙ্গ দেখি, থ হয়ে যাই, মায়ের কথা কোনো প্রসঙ্গে কখনোই শুনি নি বাবার মুখে! জীবনের এই শেষ কালে এক নতুন রূপে আবিষ্কার করি বাবাকে। ওখানেই কি প্রেম, ভালোবাসা! গভীর গোপনে? প্রকাশ্য সবই মেকি!
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নাম রাখেন বাবা, রোজিনা আশ্রম। এখানে শুধু স্বাস্থ্য-সেবাই না, স্বামী-পরিত্যক্তা অথবা পুনর্বিবাহ করতে অনিচ্ছুক দুস্থ বিধবাদের পুনর্বাসন কেন্দ্র, ও শিশুকিশোরদের জন্য একটা লাইব্রেরিসহ বেশ বড় একটা কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়। মন প্রাণ দিয়ে খাটছেন এটাতে বাবা, একটা ট্রাস্ট গঠন করে বাবাকে আজীবন চেয়ারম্যান, স্কুলের প্রধান শিক্ষক, থানা কমপ্লেক্সে ডাক্তার, মহকুমা সদরের একজন ম্যাজিস্ট্রেট, গ্রামের মেম্বার, আমাদের পরিবারের তিনজন সদস্য, এরকম এগারো জনের ট্রাস্ট কমিটি গঠন করে দেই এটা পরিচালনার জন্য। আমাদের অনুপস্থিতিতে এটা যেন বন্ধ না হয়ে যায়, এজন্য এটার খরচ নির্বাহের ব্যবস্থা করি, বাবার নামে আমার অর্থে কেনা সকল সম্পত্তি ট্রাস্টের নামে লিখে দেয়ায় আমার ভাইয়েরা মহা খেপা। গ্রামের হাটের সঙ্গে লাগানো তিন একর জমি কিনে একটা খোলা চত্বর পাকা করে উপরে ছাদ দিয়ে দেই, ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় থাকবে ওটা। একসারিতে মাছের দোকান, যা দিনে দু’বার, সকাল আটটা থেকে এগারোটা, ও বিকাল তিনটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত চালু থাকবে। অন্যান্য দোকান ন’টা-পাঁচটা। বাজার বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার রাখার জন্য ক্লিনার ও দারোয়ান রাখি দু’জন। সব মিলিয়ে গ্রামের মানুষজন খুশি, বাবাও খুশি।
খুশি না হয়ে আর উপায় আছে আমার?
প্রতিষ্ঠানটা চালু করে একদিক দিয়ে খুব ভালো হয়েছে, বাবা ব্যস্ত হয়ে ওঠেছে, শরীর স্বাস্থ্য বেশ ভালো যাচ্ছে, আমাকেও ঘন ঘন দেশে আসতে হচ্ছে। যন্ত্রণাগুলো দূরে রাখা যাচ্ছে।
তুষার-ঝরা এক রাতে মালকিনের ফ্ল্যাটে যাই, এতো বেশি কেরোলময় সব কিছু, মনে হয়, এই তো টয়লেটে গেছে, নয়তো উপরতলায় পরিপাটি হতে গেছে, এক্ষুণি বেরিয়ে আসবে, অথবা নেমে আসবে, ওর কেনা আমার প্রিয় পানীয়ের বোতলগুলো এখনো পূর্ণ, ইচ্ছে হয় না ওগুলো পান করি। আমার ভালোবাসার, ভালোলাগার প্রতিটা জিনিসের প্রতি এতো সূক্ষ্ম দরদ ছিল ওর! ফ্রীজের ভেতর এখনো পুরোনো জল জমে বরফ হয়ে আছে, ব্যবহার করা হয় নি কত দিন! অথচ, কত কী যে হতো আরো! কাঁদতে ইচ্ছে করে, ভগবান, এই কি জীবন!
হঠাৎ দরোজায় টোকা, অবাক হই, কারোই তো আসার কথা না। ভুল শুনি নি তো? আহা ভুল করেও যদি শুনে থাকি, আর দরোজা খুলে দেখি কেরোল!
দ্বিতীয়বার টোকা শুনে ভুলটা ভেঙ্গে যায়, সেই সঙ্গে স্বপ্নটাও।
দরোজা খুলে তো আরোও অবাক, মিটিমিটি হাসছে আওয়ার লেইডি মালকিন!
তোর ঘরে আলো দেখে আসলাম।
এই তুষার ভেঙ্গে?
না, পিটার পৌঁছে দিয়ে গেছে।
ওকে নিয়ে আসো নি কেন, যাবে কিভাবে এখন?
যাবো কেন?
হেসে উঠি গলা ফাটিয়ে, মনটা ভালো হয়ে যায় হঠাৎ।
ও রে মজার বুড়ি!
আধ ঘণ্টা পর আবার আসবে পিটার।
তাই বলো। বুঝলে কিভাবে, ঘরে আছি?
ওকে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে বলেছি, এ সময়ের মধ্যে না নামলে চলে যাবে ও।
অনেক বুদ্ধি তোমার! কি খাবে, চা কফি?
ব্র্যান্ডি।
বা বা।
অনেকদিন পরে এলি মনে হয়।
হ্যাঁ, দেশে দৌড়াদৌড়ি করতে হয় আজকাল।
চা দে এক কাপ।
দু’কাপ চা নিয়ে বসি, মনে হয় একটু দুর্বল হয়ে গেছে মজার বুড়ি।
তোমার শরীর স্বাস্থ্য ভালো আছে তো মালকিন?
নারে, ভালো নেই। বুড়োটা যে কেন পালালো আমাকে রেখে!
তুমি একা নও মালকিন।
হ্যাঁ। ফিরবি কখন?
আজ ফিরবো না মালকিন।
এখানে কাটাবি!
হ্যাঁ, মালকিন, কোরোলের রেখে যাওয়া সুধাগুলো এখনো রয়েছে সেলারে, ফ্রীজে জমানো ওর হাতে রেখে যাওয়া জল।
বুকের ভেতরটা ছল ছল করে ওঠে। আর কথা আসে না মুখে। মালকিনও বোঝে, চুপচাপ বসে থাকি। চায়ে চুমুক দিয়ে বলে_
কেন যে তোদের একসঙ্গে শুতে বারণ করেছিলাম, এখন দুঃখ হয়।
হঠাৎ বদলে যায় পরিবেশটা। আবার হেসে উঠি গলা ছেড়ে।
এখন আর দুঃখ করে কি হবে মালকিন?
কি আর করতে পারি, প্রায়শ্চিত্ত করি এখন, আয় আমার সঙ্গেই শুবি।
হাসতে হাসতে চায়ের কাপ উল্টে ফেলি, ধুলো তো নেই যে লুটোপুটি খাবো।
আহা রে, মজার বুড়ি, পৃথিবী এতো বদলে গেছে, অথচ তুমি সেই মজার বুড়িই রয়ে গেছো!
আধ ঘণ্টা হয়ে গেছে রে, উঠতে হবে। যাওয়ার সময় বলে_
খুব বেশি ভাবিস না, তুইও এক দিন মজার বুড়ো হয়ে উঠবি।
দরোজা খুলে দিয়ে বলি–
মজার হবো কিনা জানি না, বুড়ো তো প্রায় হয়েই গেছি।
ওটাও হবি, শুভরাত্রি।
শুভরাত্রি, আওয়ার লেইডি মালকিন।
কেরোলের চেইঞ্জারটায় আমার প্রিয় রবীন্দ্রসংগীতের ছ’টা রেকর্ড চাপিয়ে ওর রকিং চেয়ারটায় বসি, সুরা ও সংগীতের ভেতর ভুলে যাই জীবনের অন্য সব কিছু।
অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উপলব্ধি করতে পারি কী অসীম বেদনা, কত গভীর যাতনা নিয়ে কবিগুরু রচনা করেছিলেন:
এসো এসো ফিরে এসো, বঁধু হে ফিরে এসো
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত, নাথ হে, ফিরে এসো।
ওহে নিষ্ঠুর, ফিরে এসো,
আমার করুণকোমল এসো.
. . . . . . . . .
আমার ধরম-করম-সোহাগ-শরম-জনম-মরণে এসো।।
ওখান থেকে কেউ ফিরে আসে না হে কবি! বৃথাই এ কামনা, এই প্রার্থনা। কাঁদতে ইচ্ছে করে আমার।
জীবনের মধ্য বয়সে পৌঁছে এখন পেছনে ফিরে দেখতে ইচ্ছে হয় যাপিত জীবনটুকু, এখানটায় পৌঁছে গৃহী পুরুষদের নিজের বলে খুব বেশি কিছু থাকে না, পুত্র-কন্যা-পরিবার-পরিজনের জীবনের স্বপ্ন আশা আকাংখার যোগান দিতে যেয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায় অবশিষ্ট দিনগুলো।
মাত্র কিছুদিন আগে এলাম দেশ থেকে, আবার বাবার তলব, আশ্রম পরিচালনায় কিছুটা সমস্যা হচ্ছে, একা সামলাতে পারছেন না। আরো একটা যন্ত্রণা সৃষ্টি করলাম নাকি! কি দুঃখে নিরোদ বাবু ‘আত্মঘাতী’ হয়েছেন বুঝতে পারি, এদের জন্য ভালো কিছু করাও বোধ হয় বোকামী, মাদ্রাসার মতো প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে পরকালের আফিমের ভেতর এদের ডুবিয়ে রাখাই ভালো। মাসখানেক পর দেশে যেয়ে কিছুটা সামাল দিয়ে আসি। ওসব ঠিকঠাক করার সময় একদিন আমার এক আওয়ামী ভাগ্নে এসে জিজ্ঞেস করে, এসব করছি কেন, আগামী নির্বাচনে দাঁড়ানোর কোনো ইচ্ছে আছে কিনা। আমি তো আকাশ থেকে পড়ি, স্বপ্নেও ভাবি নি এরকম কিছু, এরা তাহলে এই ভেবেছে! মনের কথা চেপে যেয়ে ওকে বলি, ইচ্ছে তো আছে, তবে তোদের দল থেকে না, তোরা তো ক্ষমতায় নেই, ধানের শিষ থেকে নমিনেশান ঠিক করে ফেলেছি। আঁতকে ওঠে ও। বলে, আগে কেন বলি নি, মন্ত্রী বানিয়ে ছাড়তো আমাকে। মনে মনে বলি, বিলেতে কিং মেইকার আছে, বাংলাদেশে যে এ সময়ের মধ্যে মিনিস্টার মেইকার জন্ম নিয়েছে জানতে পারি নি, ভালোই অগ্রগতি হচ্ছে তাহলে দেশের, খুব শীঘ্র ফিরে আসি।
রল্ফের মতো একটা জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। নিজেও যখন কোনো এক ঘূর্ণাবর্তের ভেতর রয়েছি, তখন সমস্যা কি আর, ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে চলে জীবন। মাঝে মাঝে আমার স্বভাবজাত বিষণ্নতা লুকাতে পারি না। ঝড়ের মতো একদিন এসে আবার বলে রল্ফ_
এক কাজ করো ডাউ, একটা দেশি মেয়ে বিয়ে করে আনো, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, আগেও বলেছিলাম মনে হয়।
বাহ্, এতো সহজ সমাধানটা আমার মাথায় আসে নি কেন? তুমি একটা ব্রিলিয়্যান্ট!
ঠিক আছে, তাহলে আর একটা বলি। একটা জার্মান মেয়ে ব্যবস্থা করে দেই, ওদের মতো ভালো বউ এই পৃথিবীতেই হয় না, হাজব্যান্ডের জন্য সবই করে ওরা।
আরো ভালো বলেছো রল্ফ, অনেক ধন্যবাদ। দু’টোতেই রাজি আমি, ব্যবস্থা করো। কিছু মনে না করো যদি, জিজ্ঞেস করতে পারি কেন এত বছরেও একটা জার্মান মেয়ে নিজের জন্য ব্যবস্থা করতে পারো নি তুমি?
কিছুটা তো বলেছি তোমাকে ডাউ, কীভাবে ওরা মেয়েগুলোকে সরিয়ে নেয় আমার কাছ থেকে।
হ্যাঁ হ্যাঁ রল্ফ, অনেকবার বলেছো, আর দরকার নেই।
ঠিক আছে, আর বলবো না, তবে একটা জিনিস কি জানো, একজন মানুষের বিয়ে করতেই হবে এমন কোনো দিব্যি তো নেই।
নিশ্চয় নেই, জীবনের কোনো কিছুই তো থেমে নেই।
তাহলে আর এটা নিয়ে ভেবে লাভ কি?
না ভেবেও লাভ কি? যাহোক, আমি ভাবছি না। কি আনবো বলো?
জানোই তো।
একটু চেইঞ্জ করো না কেন আজ?
তাহলে যা খুশি তোমার।
জার্মান ভোদকা মনে হয় জার্মান মেয়েদের মতো, যদিও খুব জানি না ওদের সম্পর্কে।
কেন বল তো?
এখনো ওটার মাত্রা ঠিক করতে পারি নি আমি, কখনো দেখি দু’পেগেই বেশ ভালো আছি, কখনো চার পেগেও ধরা দেয় না।
ঠিকই বলেছো, শরীর ও মনের উপর কিছুটা নির্ভর করে ওটা। যাহোক, বুঝে যাবে ধীরে ধীরে। কোনো জার্মান মেয়ের সঙ্গে যদি সখ্য গড়ে ওঠে তোমার, বুঝে যাবে আশা করি।
একটু থেমে আবার বলে–
ধীরে ধীরে।
হ্যাঁ, ধীরে ধীরে।
অনেক রাতে ফিরে যায় রল্ফ, ওর সকল রহস্য নিয়ে উধাও হয়ে যায়। আমি খুঁজে পাবো কি আর, বৃটিশ পুলিশ, কিংবা গোয়েন্দা সংস্থাও কোনো কিছু জানতে পারে নি, অথবা প্রকাশ করতে পারে নি!
জানি না ঐ সরল, অথবা আবর্তিক পথে কীভাবে এগিয়ে গেছে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো, অন্তরে এখন অন্য আলো, অচেনা অন্ধকার, কোনো কিছু হয় না আর, হচ্ছে না, হবেও না, এরকম একটা বোধের ভেতর থেকেও অবশেষে কিছু না কিছু তো হয়েছিল অবশ্যই, রল্ফের দেয়া দুটো পরামর্শের একটার সূত্র ধরে, না-হলে আগামী দিনগুলোয় আমার নাতি-পুতিরা পৃথিবীর বৃহত্তম ঐ বদ্বীপটায় যেয়ে গবেষণা করবে কীভাবে?

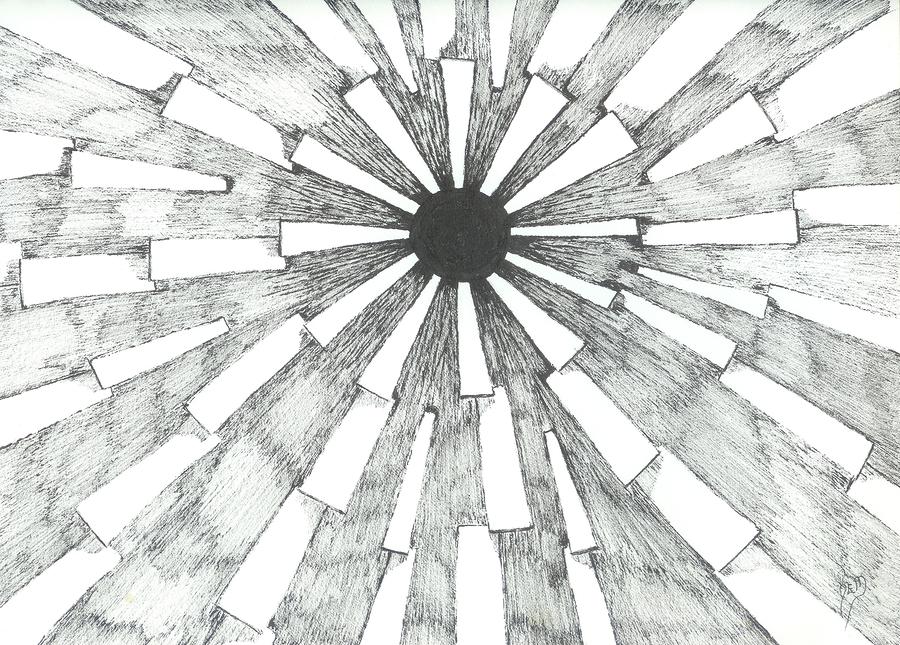
opurbo!!!
ki samasya, kalyani !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1